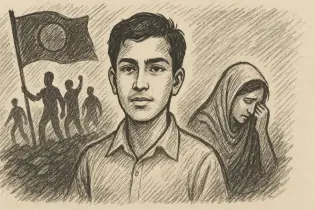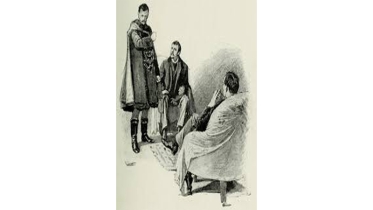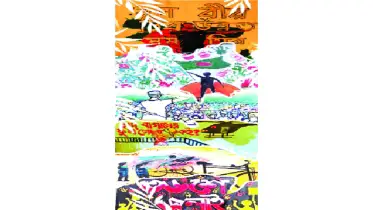রিভলবার
কলকাতায়
রিভলবারটা দেখার খুব ইচ্ছা ছিল আমার। সৌম্য বলল, ‘এখানেই আছে সেই রিভলবার- এই মিউজিয়ামে।’ একটা বিল্ডিংয়ের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা। ট্যাক্সি থেকে নামলাম আমি আর সৌম্য।
সৌম্যর বয়স তিরিশের মতো, সে পর্বতারোহী। বছর কয়েক আগে পাহাড়ে উঠেছিল সৌম্য আর তার টিম। চূড়া ছোঁয়ার পর নিচে নামছিল তারা। চারজনের দল। নামার পথে কঠিন একটা চড়াই পার হচ্ছিল দলটা, তখন ঘটল দুর্ঘটনা। পা পিছলে গেল সৌম্যর, দড়িতে ঝুলছিল সে- তার শরীরের ভারে টান খেয়ে ব্যালান্স হারাল আরও একজন- সামলে নেওয়ার সময়ই পেল না। অবস্থা এমন হলো একটু পরে সবাই একে একে ঝুলতে থাকবে- পুরো দলটাই পড়ে যাবে ভয়ানক বিপর্যয়ে। সৌম্যর ভুলের জন্য মারা যাবে তিনজন মানুষ।
দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল সৌম্য এবং হার্নেস থেকে নিজেকে খুলে নিল। এই সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। ধপ করে উঁচু থেকে পড়লো সৌম্যর শরীর, তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে প্রায় শ’খানেক মিটার নেমে স্থির হয়ে গেল। এরপর ও আর কিছুই জানে না। নৈনিতাল হাসপাতালে যখন চোখ খুললো সৌম্য, ওর দেহের বাঁ পাশটা অসার হয়ে গেছে। ভাঙা হাত-পা কোনমতে জোড়া দিলেন ডাক্তার, কিন্তু বাঁ চোখটা আর বাঁচাতে পারলেন না- নষ্ট চোখটা সরিয়ে পাথরের চোখ বসিয়ে দিলেন তিনি।
পুলিশ মিউজিয়ামটা মানিকতলায়। ভেতরে ঢুকে বাঁ দিক দিয়ে এগোতেই দেয়ালে বিপ্লবীদের ছবি। বিপ্লবী কানাইলালের চোখে চশমা। জ্বলজ্বল করছে তার চোখ। দু’পাশে দুটো পুলিশ, মাঝখানে বন্দী কানাই। কে বলবে ক্ষীণদেহী, নিরীহ দেখতে এই বিপ্লবীর শরীরে আর মনে এত তেজ, এত শক্তি ছিল। জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি যেন।
ছবি তোলা নিষেধ লেখা আছে দেয়ালে। ভেতরে ঢোকার সময় গার্ডও মনে করিয়ে দিয়েছে। কী আর করা। মিউজিয়ামের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখলাম বিল্পবীদের অস্ত্রশস্ত্র আর বোমা। এসবের মধ্যে একটা বই-বোমাও আছে। মোটা বইয়ের পৃষ্ঠা কেটে, চারকোনা খোপ বানিয়ে তার মধ্যে বোম বসিয়ে বিপ্লবীরা পাঠিয়ে দিয়েছিল বড়লাটের কাছে। বড়লাটের ভাগ্য ভাল বইটা তিনি খোলেননি। খুললে খবর ছিল। এইসব দেখলাম ঘুরে ঘুরে।
লড়াই ও সশস্ত্র সংগ্রামের দীর্ঘ ইতিহাস আছে এই ভূখ-ের। অগ্নিযুগের বিপ্লবী খুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকি অত্যাচারী বড়লাট কিংসফোর্ডকে মারতে গিয়েছিল ১৯০৮ সালে। ভুল করে তারা বড়লাটের গাড়ির মতো দেখতে আরেকটা গাড়িতে বোমা মারে। বোমার আঘাতে মারা যায় অন্য দুজন মানুষ। খুদিরামের বিখ্যাত সেই গানেই আছে এই কাহিনী-
‘বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম
আরেক ইংল্যান্ডবাসী
একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি...।’
অগ্নিযুগ
অনুশীলন সমিতি গড়ে ওঠে কলকাতায় ১৯০২ সালে। অল্প কিছুকাল পরেই ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল থেকে শুরু করে সুদূর চট্টগ্রামেও ছড়িয়ে পড়ে এর শাখা-উপশাখা। প্রথমে তরুণ ছেলেদের ব্যায়াম, লাঠিখেলা, শরীরচর্চার কেন্দ্র ছিল এসব সমিতি- অনেকটা পাড়ার ক্লাবের মতো। তিন-চার বছরের মধ্যেই তা গোপন বিপ্লবী সংস্থায় পরিণত হলো।
সারা বাংলার তরুণরা তখন টগবগ করে ফুটছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। এদের মুখপত্র ছিল ‘যুগান্তর’ পত্রিকা। এছাড়াও ‘সন্ধ্যা’, ‘সোনার বাংলা’, ‘বন্দে মাতরম’ নামে পত্রিকাগুলো ব্রিটিশ সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল এবং অনলবর্ষী লেখালেখির মধ্যে দিয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল বিপ্লবের মন্ত্র।
ব্রিটিশরাজ নড়েচড়ে বসলো। তারা প্রথমে নিষেধাজ্ঞা দিল পত্রিকার ওপর, তারপর লেখক ও সম্পাদকদের গ্রেফতার করতে শুরু করলো। বিচার বসে কলকাতা চিফ ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস কিংসফোর্ডের আদালতে। বিচারক কিংসফোর্ড শাস্তি দেন লেখক ও সম্পাদকদের। যেদিন বিচার হচ্ছিল ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকার সম্পাদক অরবিন্দ ঘোষের, সেদিন আদালতের বাইরে ছাত্র-জনতার ভিড়। জরিমানা হয় সম্পাদকের। ততদিনে অরবিন্দ ক্ষুব্ধ তারুণ্যের প্রতীক। পরিণত হয়েছেন তিনি বিপ্লবীদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায়। এই অরবিন্দকে নিয়েই ১৯০৭ সালে ‘নমস্কার’ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-
এ উদাত্ত সঙ্গীতের তরঙ্গ মাঝার
অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার।
অরবিন্দ ঘোষের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষ ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের উঁচু পদে আসীন ডাক্তার এবং আপাদমস্তক সাহেবি মেজাজের মানুষ। অরবিন্দর শৈশব ও কৈশোর কেটেছে ইংল্যান্ডে। সেখানেই তার লেখাপড়া ও বেড়ে ওঠা। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে আইসিএস পরীক্ষা দিয়ে সরকারী চাকরি করবে উঁচু পদে। ছেলের তা ইচ্ছা ছিল না। বাবার ইচ্ছায় অরবিন্দ আইসিএস পরীক্ষা দিলেন ঠিকই, কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণও হলেন। কিন্তু যেদিন ঘোড়ায় চড়া ও অশ্বচালনার পরীক্ষা ছিল, সেদিন তিনি ইচ্ছা করে দেরিতে গেলেন এবং পরীক্ষা থেকে বাদ পড়লেন। পিতার ইচ্ছা আর পূরণ হলো না। ছেলে তার নিজের পথে এগিয়ে চললো।
বরোদা স্টেট সাভির্সে যোগ দিয়ে অরবিন্দ ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে এলেন। এখানে বরোদা কলেজে ইংরেজী পড়ানো থেকে শুরু করে বরোদার মহারাজের বক্তৃতা লিখে দেওয়া সবরকম কাজই তিনি করতে থাকেন। পরে কলেজের অধ্যক্ষ হন। ফাঁকে ফাঁকে চলছিল পত্রিকায় লেখালেখি। দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে ধীরে ধীরে স্বদেশী আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন যুবক অরবিন্দ। বরোদায় একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হলো সিস্টার নিবেদিতার।
নিবেদিতা আইরিশ নারী- আয়ারল্যান্ড তাঁর দেশ। দেশে থাকতে তিনি শিক্ষকতা করতেন, ছিলেন সামাজিক এ্যাকটিভিস্ট। সেখানে তাঁর নাম ছিল মার্গারেট নোবেল। একদিন সব ছেড়েছুড়ে এদেশে চলে এলেন স্বামী বিবেকানন্দর শিষ্য হয়ে। বাংলাকে ভালবেসে তাঁর নবজন্ম হলো- মার্গারেট নতুন নাম নিলেন নিবেদিতা। কলকাতার পিছিয়ে পড়া মেয়েদের জন্য স্কুল খুললেন।
কলকাতায় প্লেগ মহামারী দেখা দিলে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন নিবেদিতা। হতদরিদ্র, অসহায়, অসুস্থ মানুষের নার্সিং শুরু করলেন, হলেন সিস্টার নিবেদিতা। ধীরে ধীরে বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জগতে ছড়িয়ে পড়লো এই মহিয়সীর নাম। জগদীশচন্দ্র বসুর বিজ্ঞান চর্চা ও বসু বিজ্ঞান মন্দির গড়ে তোলার পিছনে নিবেদিতার অবদান এখন সবার জানা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশপ্রেমে মুগ্ধ হয়ে নাম দিলেন ‘লোকমাতা’।
এসবের আড়ালে তাঁর আরেকটি পরিচয় চাপা পড়ে গেছে। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে আগে থেকেই তিনি লেখালেখি করছিলেন, বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। একসময় অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও যোগাযোগ ঘটে এবং তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সক্রিয় সমর্থকে পরিণত হন। বিবেকানন্দর মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মকা- থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন নিবেদিতা।
বরোদায় গিয়ে তিনি অরবিন্দর সঙ্গে দেখা করলেন। নিবেদিতার দেশ আয়ারল্যান্ডে তখন সশস্ত্র সংগ্রাম চলছে। আইরিশ রিপাবলিকানরা সেখানে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবের সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে দু’জনের মধ্যে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হয়।
নিবেদিতার কাছ থেকে আইরিশ বিপ্লবের তথ্য, বই, লিফলেট পেলেন অরবিন্দ। নিবেদিতার লেখা ‘কধষর ঃযব গড়ঃযবৎ’ বইটি তাঁকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। ভাই বারিন ঘোষকে আগেই তিনি কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন, এবার অনুপ্রাণিত অরবিন্দ নিজেও কলকাতায় চলে এলেন এবং বিপ্লবের কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করলেন।
চন্দননগরে
‘এটা আমার কলেজ।’ সুলগ্না চক্রবর্তী বললেন। ‘এখানে আমি দু’বছর পড়েছি।’ সুলগ্না একজন শিক্ষক, গবেষক ও চন্দননগরের আদি বাসিন্দা। এই শহরের অলিগলি রাজপথ তার আশৈশবের চেনা।
আমি এসেছি কলকাতা বইমেলা দেখতে। ইচ্ছা ছিল এবার আন্দামান ঘুরে আসব। দেখে আসব সেই জেলখানা, যেখানে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বন্দী করে রাখা হতো। এত অল্প নোটিসে প্ল্যান অনুযায়ী আন্দামানের টিকিট পেলাম না। সুলগ্না বললেন, ‘তাহলে চন্দননগর ঘুরে যান। একসময় বিপ্লবীদের অভয়াশ্রম ছিল এই চন্দননগর- অগ্নিযুগের অনেক ইতিহাস এখানে ছড়িয়ে আছে।’
অটো নিয়ে ঘুরছি আমি আর সুলগ্না চন্দননগরে। ঘুরতে ঘুরতে শহরের গোন্দলপাড়া নামে একটা জায়গায় চলে এলো অটো, থামলো পুকুরপাড়ে গাছের ছায়ায়। সাদামাটা ছোট্ট পুকুর, এপাশটায় কচুরিপানা দিয়ে ঢাকা। ওপাশে ভাঙা, পুরনো শতবর্ষী একটা বাড়ি। বাড়িটা দেখিয়ে সুলগ্না বললেন- ‘ঐ বাড়িতে থাকতো বিপ্লবী মাখনলাল ঘোষাল আর পুঁটিদি।’
সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল করার মিশন শুরু হয় ১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল রাতে। মাখনলাল ছিল ছয়জনের একটি দলে। ছয়জনের আরেকটি দল শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত টেলিগ্রাফ-টেলিফোন অফিস দখল করে ধ্বংস করে দেয়। ট্রেনলাইন উপড়ে ফেলে। এভাবে বাইরের জগত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন চট্টগ্রামকে স্বাধীন ঘোষণা করেন সূর্য সেন। ব্রিটিশের দম্ভ চূর্ণ হয়, যদিও চট্টগ্রাম স্বাধীন ছিল মাত্র চারদিনের জন্য। ২২ এপ্রিল বিকেলের দিকে ব্রিটিশ সৈন্যরা আক্রমণ করে বিপ্লবীদের ঘাঁটি। জালালাবাদ পাহাড়ে শুরু হয় সন্মুখযুদ্ধ।
একদিকে প্রশিক্ষিত বিশাল ব্রিটিশ বাহিনী, অন্যদিকে সূর্য সেনের নেতৃত্বে কয়েকজন মাত্র বিপ্লবী। বারো জন বিপ্লবী শহীদ হলেন। টিকতে না পেরে পিছিয়ে গেলেন বাকিরা। দলছুট হয়ে মাখনলাল, আনন্দ, লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ আর অনন্ত সিংহ চলে আসেন চন্দননগরে।
তারা আশ্রয় পেলেন সুহাসিনী গাঙ্গুলি ও শশধর আচার্যর গোন্দলপাড়ার এই বাড়িতে। সুহাসিনীই বিপ্লবীদের পুঁটিদি। তাঁর জন্ম খুলনায়, লেখাপড়া ঢাকা শহরে। ইডেন কলেজে পড়ার সময় কলকাতায় মূক ও বধিরদের স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি পেয়ে তিনি কলকাতায় চলে আসেন। এখানে যুগান্তর দলে যোগ দেন সুহাসিনী- বিপ্লবের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে থাকেন। পুলিশের কাছে তার কর্মকা-ের খবর পৌঁছে যায়।
পুলিশের নজর এড়াতে তিনি চন্দননগরে এসে একটা পাঠশালায় পড়াতে থাকেন। এমন সময় সুহাসিনী জানতে পারলেন পলাতক বিপ্লবীদের একটা আশ্রয় দরকার। সেজন্য তাঁকে শশধর আচার্য নামে একজনের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী সেজে এক বাড়িতে থাকতে হবে। সেই বাড়িতে আশ্রয় নেবে বিপ্লবীরা।
স্বামী-স্ত্রী সেজে অভিনয় করে যাওয়া! প্রস্তাবটা পেয়ে অবাক হলেন সুহাসিনী। সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপটে এমন প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া একুশ বছরের যে কোন যুবতীর পক্ষে প্রায় অসম্ভব কাজ। কিন্তু সুহাসিনী বিপ্লবী নারী, নির্দ্বিধায় রাজি হলেন তিনি- এও তো দেশেরই কাজ। তাদের বাড়িতে গোপনে আশ্রয় নিলেন বিপ্লবীরা। এদের মধ্যে অনন্ত সিংহ সবাইকে অবাক করে দিয়ে একদিন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। বাকিরা থেকে গেলেন সুহাসিনীর আশ্রয়ে আত্মগোপন করে।
বাড়িতে ছয়জন মানুষ। আশপাশের প্রতিবেশীরা যেন বুঝতে না পারে, সেজন্য সুহাসিনী মুদি দোকান থেকে জিনিস কিনতেন খুব সাবধানে। সতর্ক থাকতে হতো বাজার-সওদা করার সময়। ছদ্মনাম নিয়েছিলেন বিপ্লবীরা সবাই। তারপরও শেষ রক্ষা হলো না। খবর পেয়ে যায় পুলিশ। একদিন গভীর রাতে কমিশনার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বে বাড়ি ঘিরে ফেলে পুলিশ বাহিনী। ফরাসী পুলিশের অনুমতি না নিয়ে গোপনে এসেছিল তারা।
টের পেয়ে অস্ত্র হাতে অন্ধকারে বেরিয়ে এলেন বিপ্লবীরা। সবার সামনে মাখন। দেয়াল টপকে সে ঝুপ করে নামলো পুকুর পাড়ে। নামতেই জ্বলে উঠলো সার্চলাইট। ছুটে এলো গুলির ঝাঁক। শত্রুর সব গুলি যেন তাকেই খুঁজে নিল। লুটিয়ে পড়ল মাখন। এখানে এই পুকুর পাড়ে এভাবেই প্রাণ দিয়েছেন অগ্নিযুগের মহান বিপ্লবী মাখনলাল ঘোষাল।
তখন তাঁর বয়স মাত্র আঠারো বছর। জন্ম চট্টগ্রামে, শহীদ হলেন দূরের শহর চন্দননগরে এসে। তরুণ এই বীরের শবযাত্রায় মানুষের ঢল নেমেছিল। তাঁর স্মরণে এখানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ আছে। নদীর ধারে শ্মশানঘাটেও তাঁর স্মারক আছে। মাখন মারা যাওয়ার পর সেদিন ধরা পড়েছিলেন বাকি তিনজন বিপ্লবী- গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্ত।
সবাই অক্ষত ছিলেন, শুধু আনন্দের পায়ে গুলি লেগেছিল। তার বয়স চৌদ্দ বছর, সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। শশধর আর সুুহাসিনীকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ভয়াবহ পুলিশি নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন সুহাসিনী- নারী বলে তাঁকে রেহাই দেয়নি তারা। পরে তাঁকে আন্দামানে পাঠিয়ে দেয়। ছয় বছর দ্বীপান্তরে বন্দী ছিলেন এই সাহসিনী নারী।
সুলগ্নার মুখে ইতিহাসের রক্তক্ষরা এইসব কাহিনী শুনে নীরবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম পুকুর পাড়ে। এপার থেকে দেখলাম মাখন আর তার পুঁটিদির স্মৃতিঘেরা ভগ্নপ্রায় বাড়িটিকে। চৈত্রের মাঝামাঝি, গাছের ছায়ায় চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। পুঁটিদির কথা ভাবছিলাম- কী দারুণ সাহস নিয়ে প্রায় শতবর্ষ আগে এই মহীয়সী নারী বিপ্লবের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন-
সুলগ্নার ডাকে চমক ভাঙলো। ‘চলুন, এবার আমরা যাব হেরিটেজ মিউজিয়ামে।’ সুলগ্না বললেন। ‘অরুণদা অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য।’
চশমা চোখে, পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা সৌম্য চেহারার অরুণ চক্রবর্তী দাঁড়িয়ে আছেন মিউজিয়ামের সামনে। তিনি আমাদের ভেতরে নিয়ে গেলেন। একতলায় রবীন্দ্রনাথের ছবি। কবির সঙ্গে চন্দননগরের বিশেষ সম্পর্কের কথা আর এই শহরের ইতিহাস বললেন তিনি। বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন এখানে। অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবীও তখন ছিলেন চন্দননগরে মোরাণ সাহেবের বাড়ি ভাড়া নিয়ে। সেই বাড়ির প্রসঙ্গ আছে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথায়- এখানে বসেই তিনি রচনা করেছেন ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ আর ‘বৌঠাকুরাণীর হাট’। বাড়িটি এখন আর নেই, গঙ্গা গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।
চন্দননগরে ছিল ফরাসীদের কুঠি। ডাচ, ওলন্দাজ, ব্রিটিশদের মতো ফরাসীরাও এসেছিল এদেশে বাণিজ্য করতে। এদের মধ্যে ব্রিটিশরা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী। ১৬৯৬ সালের দিকে দুর্গ তৈরি করে চন্দননগরে উপনিবেশ গড়ে তোলে ফরাসীরা। তারাও বাংলার গ্রামে গ্রামে চাষীদের দিয়ে জোর করে নীলের চাষ করাতো। ফ্রেঞ্চ উপনিবেশ হওয়ায় ফরাসীদের অনুমতি না নিয়ে হুট করে চন্দননগরে ঢুকে পড়তে পারতো না ব্রিটিশ পুলিশ। এ কারণেই বিপ্লবীদের অভয়াশ্রমে পরিণত হয়েছিল শহরটা।
ব্রিটিশ পুলিশের তাড়া খেলে কিংবা ধরপাকড় ও গ্রেফতার শুরু হলে গঙ্গা পার হয়ে বিপ্লবীরা ঢুকে পড়তো এই শহরে। দুই সা¤্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে রেষারেষি আর যুদ্ধ-বিগ্রহ তখন লেগেই ছিল। যে কারণে চন্দননগর অনেকবার হাতবদল হয়েছে ব্রিটিশ আর ফরাসীদের মধ্যে। বন্দুকের দোকান ছিল চন্দননগরে। এই শহরের ধনী বাসিন্দারা লাইসেন্স করা অস্ত্রশস্ত্র কিনতে পারতেন। তা আবার হাতবদল হয়ে চলে যেত বিপ্লবীদের কাছে। তাদের অস্ত্রের বড় জোগান আসতো এই চন্দননগর থেকে। কলকতার বিখ্যাত অস্ত্র ব্যবসায়ী ‘রডা কোম্পানি’র দোকান লুট করেও প্রচুর অস্ত্র পেয়েছিল বিপ্লবীরা।
এসব ইতিহাস শেষে আমরা গেলাম পাশের ঘরে। এই ঘরে রাধানাথ শিকদারের ব্যবহার করা যন্ত্রপাতি, ক্যামেরা, পাহাড়ে চড়ার গিয়ার এসব রাখা আছে প্রদর্শনীর জন্য। রাধানাথ শিকদার ছিলেন হিন্দু কলেজের গণিত বিভাগের মেধাবী ছাত্র। পরে তিনি সারভেয়ার হিসেবে তাঁর পেশাজীবন শুরু করেন। এভারেস্ট চূড়ার উচ্চতা তিনিই নির্ণয় করেছিলেন জরিপের জটিল সূত্র ব্যবহার করে, যদিও চূড়ার নাম রাখা হয় তার প্রাক্তন বস জর্জ এভারেস্টের নামে।
‘এ হচ্ছে কৃতিত্ব ছিনতাইয়ের ঘটনা।’ অরুণ চক্রবর্তী বলেন। ‘রাধানাথের কৃতিত্ব নিয়ে নিলেন প্রাক্তন সারভেয়ার-জেনারেল জর্জ এভারেস্ট। হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়ার উচ্চতা যখন জানা গেল, মিস্টার এভারেস্ট তখন চাকরি ছেড়ে অবসরে চলে গেছেন। অথচ তার নামেই এখন সবাই চেনে পৃথিবীর সর্বোচ্চ চূড়া। রাধানাথ শিকদারকে কে চেনে? কেউ না। আমরা তাঁর স্মৃতি ধরে রেখেছি এখানে।’ রাধানাথ যখন কলেজে পড়তেন তখন সেই কলেজের শিক্ষক ছিলেন হেনরি ডিরোজিও। তাঁর নেতৃত্বে চলছিল ‘ইয়াং বেঙ্গল’ আন্দোলন। রাধানাথ ছিলেন ডিরোজিওর শিষ্য।
ব্রিটিশদের অন্যায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন রাধানাথ সবসময়। ব্রিটিশ অফিসাররা শ্রমিকদের বিনা পারিশ্রমিকে খাটাতো। এর প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে অফিসারদের সঙ্গে তাঁর বাদ-প্রতিবাদের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা আদালত পর্যন্ত গড়ায়। বিচারক রাধানাথকে দুশো রুপি অন্যায়ভাবে জরিমানা করেছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে অরুণ চক্রবর্তী বলেন, ‘এই হচ্ছে ব্রিটিশ বিচারকের পক্ষপাতিত্বের ছোট্ট একটি নমুনা। যাক, আসুন আমি আপনাদের নিয়ে যাই আমার উপাসনালয়ে।’ সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে একটা ঘরের সামনে দাঁড়ান তিনি। জুতো খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন। আমরাও তাঁর দেখাদেখি জুতো খুলি।
আমি ভেবেছি বোধহয় ভেতরে আছে কোনো বিগ্রহ কিংবা মূর্তি। দেখি ঘরের দেয়াল জুড়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বড় একটা ছবি। টেবিলে বসুর লেখা অনেক বই। চারপাশে তাঁর ব্যবহার করা স্মারক আর জাপানের স্মৃতি। চারপাশটা দেখিয়ে অরুণ চক্রবর্তী বললেন, ‘এই আমার উপাসনালয়।’
রাসবিহারী বসুর পরিকল্পনায় লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা হামলা হয়েছিল- ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর। তখন কেবলি কলকাতা থেকে রাজধানী নিয়ে যাওয়া হয়েছে দিল্লীতে। সেই উপলক্ষে অনুষ্ঠান হচ্ছে জাঁকজমকের সঙ্গে। অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ হাতির পিঠে চড়ে। সুদৃশ্য হাওদায় সস্ত্রীক বসে আছেন হার্ডিঞ্জ, পিছনে ছাতা ধরে আছে চামরবাহক। সামনে মাহুত। প্রচ- শব্দে বোমা ফাটলো হাওদার ওপর। বোমাটা ছুড়েছিল নদীয়ার বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস। অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন হার্ডিঞ্জ।
হামলার পরিকল্পনাকারী রাসবিহারী বসুকে খুঁজতে থাকে পুলিশ। পালিয়ে বেড়ান বসু। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় যান তিনি। গোপনে বিপ্লবীদের সংগঠিত করতে থাকেন। অসাধারণ সংগঠন ক্ষমতা ছিল তাঁর। পুলিশের চোখ ফাঁকি দেওয়ার দক্ষতাও ছিল অতুলনীয়। বারবার পুলিশ তাঁর আস্তানা আক্রমণ করেছে, বারবার তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি নির্বিঘ্নে সরে পড়েছেন- ঠিক যেন ডিটেকটিভ গল্প, থ্রিলার মুভি।
অথচ গল্প নয় এই কাহিনী, বানানো মুভিও নয়- ইতিহাসের সত্য। সারা উপমহাদেশ জুড়ে তখন ব্রিটিশের জাল বিছানো। তার ভেতর দিয়ে তিন বছর ধরে চলেছিল পুলিশের সঙ্গে দুঃসাহসী এই বিপ্লবীর লুকোচুরি খেলা। ধরা পড়লে পরিণতি হতো প্রাণঘাতী- এমন খেলা সবাই খেলতে পারে না। কেউ কেউ পারে। রাসবিহারি ছিলেন তেমনি একজন বিপ্লবী।
স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রবাসী পাঞ্জাবীরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ‘গদর পার্টি’। এই পার্টির সঙ্গে যুক্ত হন রাসবিহারী- নেতৃত্বের আসনে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। সিপাহী বিদ্রোহের আদলে একটি অভ্যুত্থানের প্ল্যান করেছিলেন গদর বিপ্লবীরা। অভ্যুত্থানের দিন ঠিক হয় ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৫। ভারতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামে অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করতে সম্মত হয়েছিল জার্মান সরকার।
অস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগটা শুরু হয়েছিল বহুদিন আগে বাংলার আরেক বিপ্লবী বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) মাধ্যমে। ১৯১২ সালে জার্মানির যুবরাজ কলকাতায় এলে যতীন তার সঙ্গে দেখা করে অস্ত্র সাহায্য চেয়েছিলেন। তারপর এই উপলক্ষে বহুবার বহু সূত্রে জার্মান সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন প্রবাসী বিপ্লবীরা, সহায়তা চেয়েছেন। শেষ পর্যন্ত অস্ত্র ভর্তি জাহাজ পাঠাতে রাজি হয়েছিল জার্মান সরকার।
কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, গদর পার্টির প্ল্যানটা জেনে যায় ব্রিটিশ পুলিশ। ব্যর্থ হয় অভ্যুত্থানের চেষ্টা। ধরা পড়তে থাকেন নেতারা। রাসবিহারীর আস্তানায়ও হানা দেয় পুলিশ- টের পেয়ে পুলিশকে বোকা বানিয়ে আবার পালালেন বসু। জাহাজ ভর্তি অস্ত্র পাঠানোর তথ্যও পেয়ে যায় ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স। একটি জাহাজ আসবার কথা ছিল উড়িষ্যার উপকণ্ঠে।
সেই অস্ত্রের চালান সংগ্রহ করার জন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ উড়িষ্যার বালেশ্বরে আত্মগোপন করে ছিলেন বাঘা যতীন। সেই খবরও পেয়ে যায় পুলিশ। তাদের তাড়া খেয়ে বুড়িবালাম নদীর তীরে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হলেন যতীন ও তাঁর চারজন সঙ্গী। তাঁদের হাতে রডা কোম্পানি থেকে লুট করা মাউজার পিস্তল। অন্যদিকে প্রতিপক্ষ ব্রিটিশ বাহিনী।
নেতৃত্ব দিচ্ছে লেফটেন্যান্ট রাদারফোর্ড। বিপ্লবীদের গুলি ফুরিয়ে গেলে যুদ্ধ শেষ হলো। পাঁচজন বিপ্লবীর সবাই আহত অথবা নিহত। পরদিন বালেশ্বর হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস নিলেন বাঘা যতীন। দিনটা ছিল ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ সাল।
এরপর রাসবিহারী বসুকে আবার দেখা গেল জাপানে। ছদ্মনামে পাসপোর্ট তৈরি করে পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে কলকাতা বন্দর থেকে জাহাজে চেপে তিনি চলে যান জাপান। ভাষা জানা নেই, নতুন এক দেশ। ধীরে ধীরে সেখানে কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করলেন তিনি, বিয়ে করে সংসার পাতলেন, তারপর ইন্ডিয়ান কারির রেস্টুরেন্ট খুললেন টোকিওতে- সেসব আরেক কাহিনী, দীর্ঘ ইতিহাস- যেমন বিস্ময়ের তেমনি রোমাঞ্চকর। ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি চলতে থাকলো দেশের কাজ। ধীরে ধীরে বসুর এই রেস্টুরেন্ট হয়ে উঠলো প্রবাসী বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় ও শক্তিশালী ঘাঁটি।
জাপানে এসেছিলেন বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম এন রায়)। অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ফিলিপিন্স, জাপান, চীন, আমেরিকা ঘুরে তিনি চলে যান মেক্সিকোতে। সেখানে পৌঁছে তাঁর জীবনের গতিপথ যায় পাল্টে। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের (কমিন্টার্ন) একজন গুরুত্বপূর্ণ তাত্ত্বিক নেতা। ১৯২০ সালে এম এন রায় মস্কো গিয়েছিলেন কমিন্টার্নের ওয়ার্ল্ড কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য।
ভ্লাাদিমির লেনিন তাঁকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানিয়েছিলেন। লেনিনের নির্দেশে তাসখন্দ যান এম এন রায়। সেখানে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিলে দেশে ফিরে আসেন এম এন রায়। এভাবে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন অদম্য সাহসী বাঙালী বিপ্লবীরা।
প্রবাসীদের নিয়ে জাপানে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি গড়ে তুলেছিলেন রাসবিহারী বসু। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজির আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে যোগ দেয় বসুর ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি। যে স্বাধীনতার জন্য এত আত্মত্যাগ, তা দেখে যেতে পারেননি বসু। তিনি প্রয়াত হয়েছেন জাপানে ১৯৪৫ সালে, সেখানেই সমাহিত তিনি। মৃত্যুর সময় বিপ্লবীর শেষ ইচ্ছা ছিল তাঁর দেহাবশেষ যেন চন্দননগরে নিয়ে আসা হয়। সেই ইচ্ছা পূরণ হয়েছে। তাঁর দেহভস্ম এনে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে যথাযোগ্য মর্যাদায়।
অরুণ চক্রবর্তী বললেন, ‘আমরা এখানে রাসবিহারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট গড়েছি, তাঁর স্মরণে। আজও তিনি জাপানে অত্যন্ত সম্মানিত। জাপানী তরুণ-তরুণীরা আসে এখানে- এই মহান বিপ্লবীর জীবন সম্পর্কে জানার জন্য। এখানে থাকে তারা যতদিন খুশি- গবেষণার রসদ জোগাড় করে নিয়ে যায়।’
বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত
অরুণ চক্রবর্তীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি আর সুলগ্না। বাইরে দুপুরের রোদ, তার ভেতর দিয়ে এগোই আমরা। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য প্রবর্তক সংঘের আশ্রম। সেখানে দেখা পাবো শর্বরী বোসের। তিনি বিপ্লবী কানাইলালের নাতনি। অটোতে উঠতে উঠতে সুলগ্না বলেন, ‘চলুন, এবার নাতনির মুখে শুনবেন বিপ্লবী দাদুর জীবন কাহিনী।’ (চলবে...)