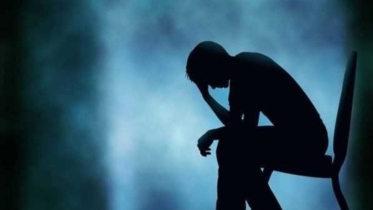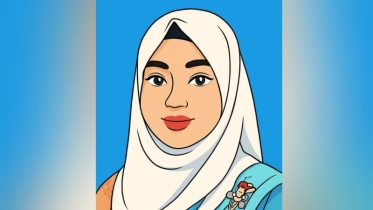সিলেটি নাগরীলিপি সাহিত্যে ‘প্রণয়োপাখ্যান’ মোস্তফা সেলিমের এক অনন্য উদ্যোগ। অনিন্দ্য প্রকাশের প্রকাশনায় ড. ভীষ্মদেব চৌধুরীকে উৎসর্গীকৃত ঝকঝকে প্রিন্ট্রের বইখানি আমাদের উৎসাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নাগরীলিপিতে রচিত চার শ’ বছরের রচিত বাংলা সাহিত্য দু’শ’ মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সমন্বয়ে ছিল বিচিত্র ও ব্যাপক। কিন্তু গ্রন্থের চেয়ে পা-ুলিপির সংখ্যা ছিল বেশি, যা পুঁথি হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে হাতে লেখা সে সব পুঁথি লেখকের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায়। সেগুলো সংরক্ষণের জন্য যতটুকু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, তাও লেখকের মৃত্যুর পরে। নানা কারণে নাগরীলিপির সাহিত্য বিলুপ্ত হতে দেখা যায়, যেমন: এক. সংগ্রাহকের মৃত্যু, দুই. দেশভাগ এবং তিন. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ অন্যতম।
সিলেটের পাশাপাশি নাগরীলিপির চর্চা হতো ভারতের অসম এবং ত্রিপুরায়। দেশভাগের ফলে সে চর্চায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। ফলে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যেতে থাকে বহু মূল্যবান পুঁথি। নাগরীলিপিতে ধর্মীয় বিষয়ের আধিক্য থাকলেও, রয়েছে নানা বিচিত্রতা, যেমন : এক. সামাজিক উপাখ্যান, দুই. যুদ্ধকাহিনী, তিন. প্রেম-প্রণয়কাহিনী এবং চার. সমাজচেতনতামূলক গ্রন্থ ইত্যাদি। এই গ্রন্থটিতে নাগরীরিপির প্রেম-প্রণয়নমূলক তিনটি পুঁথি নিয়েই এ গ্রন্থের আয়োজন।
চন্দ্রমুখী : অনন্য এক প্রণয়গাথা গ্রন্থে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য, হারিকেল রাজ্য হয়ে প্রাচীন শ্রীহট্টতেই চতুর্দশ শতকে ভাষালিপির বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। পৃথিবীতে প্রচলিত কয়েক হাজার ভাষার যেখানে কোন লিপিই নেই, সেখানে একটি ভাসার একাধিক লিপির যে প্রচলন বাংলাদেশের সিলেটে হয় ভাষালিপির ইতিহাসে এটি এক বিরল অধ্যায়। বাংলালিপির পাশাপাশি সিলেটি নাগরীলিপি পাঁচ শ’ বছর দাপটের সঙ্গে টিকে ছিল বঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলজুড়ে। এ লিপির সাহিত্যজগত মোটেও ছোট নয়। এ লিপির জনপ্রিয় একটি পুঁথি চন্দ্রমুখী ছিল ভীষণ জনপ্রিয়। শুধু কাহিনীতে নয়, কাব্যরচনার মুন্সিয়ানার জন্যও। চন্দ্রমুখীর পুঁথিকা মুহম্মদ খলিল সম্পর্কে আমাদের কাছে কোন তথ্য ছিল না কিন্তু গবেষক এসএম গোলাম কাদির (১৯৩৩-২০১১) চন্দ্রমুখীর ভাষা, শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদি বিবেচনায় তাঁকে লাউড়ের অধিবাসী বলে মত দিয়েছেন। লাউড় বর্তমান সুনামগঞ্জ জেলার একটি অঞ্চল। চন্দ্রমুখী ছাড়াও মুহম্মদ খলিল আরও দুটি পুঁথি রচনা করেছেন। এগুলো হলো : ফুলকুমারী এবং হাসিনা। চন্দ্রমুখী পুঁথিকে আঠারো শতকের (১৯২১-১৯৯৯) রচনা বলে উল্লেখ করা হয়। তবে লাল বিহারী দে (১৮২৪-১৮৯২) সালে চন্দ্রমুখী নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু বিষয়বস্তুর কোন মিল ছিল না গ্রন্থ দুটোতে। তবে গ্রন্থ-দুটো রচনা হয়েছে সমকালে, প্রায় কাছাকাছি সময়ে। যদিও গ্রন্থ দুটির একটি চন্দ্রমুখী এবং অন্যটি চন্দরমুখী। যদিও নাগরীলিপি প্রকাশনার রীতি অনুযায়ী শিরোনামটি চন্দ্রমুখী হওয়াই সংযত ছিল। পুঁথিটি ২৩টি অঙ্ক বা অধ্যায়ে বিভক্ত। পুঁথিটির বেশিরভাগ অধ্যায় পয়ার ছন্দে লেখা। তবে কয়েকটি রাগ তাল-ছন্দেও লেখা হয়েছে। চন্দ্রমুখী মূলত একটি মর্মস্পর্শী প্রেমকাহিনী। রূপকথার মতো এর ঘটনাপ্রবাহ বিস্তৃত। পুঁথির সূচনাতেই তিনি লিখেছেন : আগেতে আল্লাহর নাম মনিতে রাখিয়া/ চন্দরমুখীর কথা শুন মন দিয়া */ মিছিল নগরের রাজা নামে পুরবেশ^র/ তান ঘরে হইয়া পুতরু গুল শুনাহর*’। চন্দ্রমুখী পুঁথিটিএক নিটোল প্রেমকাহিনী। গল্পের বুনন চমৎকার। কাহিনীপরম্পরা সাবলীল। তাই পুঁথিটি পাঠককে টেনে রাখে শেষ পর্যন্ত। সিলেটি নাগরীলিপির এ পুথিটি প্রায় দু’শ’ বছর পাঠকের পছন্দের তালিকায় তুমুল জনপ্রিয় ছিল। মহব্বত নামা গ্রন্থটি নাগরীলিপির পুঁথি সাহিত্য আকারে যেমন বড়, প্রকারে, বিষয়-প্রকরণেও তার বৈভব বৈচিত্র্যপূর্ণ। এই গ্রন্থটির পরিসর চার শতাব্দীজুড়ে বিস্তৃত ছিল বঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং নাগরিক জীবনের ওপর প্রভাব, সময়ের ভাঁজে ভাঁজে ও স্তরে স্তরে এবং সাহিত্যজমিনে ফলেছে বিচিত্র সব আখ্যান। মধ্যযুগের পুঁথিসাহিত্যের জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল মহব্ব নামা। এই গ্রন্থটির রচয়িতা মুন্সি সাদেক আলী (১৮০১-১৮৬২) ছিলেন নাগরী-সাহিত্যের ব্যাপক প্রিয়তম কবি। তাঁর কেতাব হালতুন্নবী ছিল বিপুল জনপ্রিয়, ঘরে ঘরে সমাদৃত। তিনি নাগরীলিপি সাহিত্যের সর্বাাধিক পুথিপ্রণেতাও। তাঁর রচিত পুঁথিগুলো হচ্ছে : কেতাব হালতুন্নবী, রদ্দুল হিন্দ, কাশফুল বেদাত, পান্দেনামা, দফেউল হুজত, হুঁশিয়ারনামা, রদ্দে কুফুর, মহব্বত নামা, হাশর মিছিল এবং রাহাসতুল ইসলাম ইত্যাদি। তিনি মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নাগরীলিপির গবেষক এসএম গোলাম কাদিরের মতে, ১৮৬২ থেকে ১৮৬৫-এর মধ্যে কোনো একসময় রচিত হয়। সিলেটি নাগরীতে বিশ শতকে মহব্বতনামা কেতাব নামে অন্য আরেকটি পুঁথি রচিত হয়েছে। এর রচয়িতা হাতেম আলী। মুন্সি সাদেক আলী বাংলার পাশাপাশি ইউসুফ-জুলেখার আখ্যান নিয়ে মহব্বতনামা পুঁথিটি রচনা করেন। কিন্তু এতে রয়েছে ধর্মীয় সম্পৃক্ততা। কাহিনীর ভাষায় সিলেটের উপভাষাকে গ্রহণ করা হয়েছে। পুঁথির কাহিনী মৌলিক নয় আবার কেবল অনুসরণও নয়। পুঁথিটিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য সাদেক আলী শিল্পীমনে এঁকেছেন মহব্বতনামার কল্পকথা। মধ্যযুগে যখন বিনোদনের সুযোগ এত অবারিত ছিল না, তখন পুঁথিই ছিল আশ্রয়। আর এই পুঁথিটিকে ঘিরে জমে উঠত মানুষের আড্ডা আর জয়জয়কার। মহব্বতনামাও শত বছর ছিল এমনই এক জনপ্রিয় পুঁথি। যার কাব্যরসে সিক্ত হয়েছে গ্রামবাংলার সহজ-সরল মানুষের রোমান্টিক মন। এই আখ্যানকাব্যটি মুন্সি সাদেক আলীর এক অবিনশ^র সৃষ্টি।
বারাম জহুরা গ্রন্থটি একটি রোমাঞ্চকর প্রেমাখ্যান।সিলেট অন্তত আড়াইহাজার বছরের প্রাচীন জনপদ। এর পক্ষে প্রমাণ মেলে পানিণি রচিত অষ্ট্যাধ্যায়ী গ্রন্থে। বানারস হিন্দু বিশ^বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বিদ্যাপ্রসাদ আগরওয়ালা (ভিপি আগারওয়ালা), তাঁর ইন্ডিয়া ইন দ্য এজ অব পানিণি (১৯৪৩) গ্রন্থে ‘সুররমাস’ অঞ্চলকে সুরমা নদীর তীরবর্তী জনপদ শনাক্ত করেছেন তিনি। পানিণির মন্তব্য, ‘এখানকার রমণীরা সুন্দরী।’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সিলেট ভ্রমণ করেন ৪ নবেম্বর, ১৯১৯ সালে। ইতিহাসের প্রাচীন জনপদ এই সিলেটে বাংলাভাষার এক নাটকীয় অধ্যায় হচ্ছে সিলেটি নাগরীলিপির আত্মপ্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সূচনাকালে চতুর্দশ শতকে বাংলাসাহিত্য চর্চায় যুক্ত হয় বাংলাভাষার ভিন্ন আরেকটি লিপি, যা সিলেটি নাগরীলিপি নামেই অভিহিত। বারাম জহুরা কাব্যের ভাষা সাদামাটা হলেও রয়েছে প্রাণস্পর্শ। এই পুঁথিতে আরবী-ফারসি শব্দেরও বিপুল সমাহার চোখে পড়ে। ইসলামী শব্দের ব্যবহার অহরহ এই কারণে যে, এসব পুঁতির পাঠক ছিলেন মূলত সাধারণ মুসলমান সমাজ। পুঁথিটি আটটি আখ্যানে বিভক্ত বাহরাম জহুরা। এর মধ্যে ৪টি পয়ার ছন্দে লেখা, বাকিগুলোর তিনটি ত্রিপদী ছন্দে, একটি চৌপদী ছন্দে লিখিত। পুঁথিটির ভাষা বিশ্লেষণে অনুমিত হয় যে, এ পুঁথিটি বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচনা করা হয়েছে। মোস্তফা সেলিম লুপ্ত বর্ণমালা সিলেটি নাগরীলিপি ও সাহিত্য গবেষণা, প্রকাশনা এবং তার নবজাগরণে অনন্য ভূমিকা রেখে দেশে-বিদেশে নন্দিত একজন গবেষক। সিলেটি নাগরীলিপি সাহিত্যে তিনি তিনটি আখ্যান রচনার মাধ্যমে যে প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন তা আমাদের সত্যিই বিমোহিত করে। আখ্যান-চয়ন, বিশ্লেষণ, ভাষাশৈলী ও উপস্থাপনা আমাদের বিমোহিত করে। আমরা বইটির সাফল্য কামনা করি।