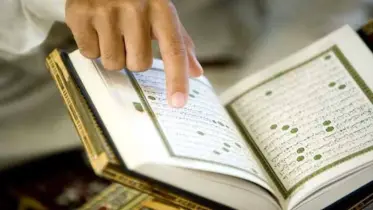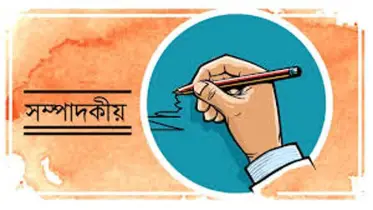শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় পার্বণ। হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়ে বিশ^বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই দিনটিকে পালন করেন। বাংলাদেশের বৌদ্ধরাও যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদা ও ভাবচেতনায় দিনটি পালন করেন। এ পূর্ণিমা তিথিতে মহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্ম, সম্বোধিলাভ (মহাজ্ঞান লাভ) ও মহাপরিনির্বাণ (দেহত্যাগ) সাধিত হয়। তথাগত বুদ্ধের জীবনের ত্রি-স্মৃতিতে সমুজ্জ্বল। এ তিথিই ‘বুদ্ধ পূর্ণিমা’ নামে খ্যাত।
খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় রাজকুমার সিদ্ধার্থ কপিলাবস্তুর লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, পিতা-মাতা, প্রজা, আত্মীয়-স্বজন সকলের সর্বার্থ সিদ্ধ হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। দুঃখের বিষয় যে, সিদ্ধার্থের জন্মের সাত দিনের মাতায় রানী মহামায়া মৃত্যুবরণ করেন। সিদ্ধার্থের লালন পালনের ভার গ্রহণ করেন তাঁর বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। মহাপ্রজাপতি গৌতমীর অসমান্য যত্ন ও ভালোবাসায় সিদ্ধার্থ বড় হয়েছেন। তাই তাঁর আরেক নাম হলো গৌতম। ইতিহাসে তিনি গৌতম বুদ্ধ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। সাংসারিক জীবনের কোনো অভাববোধ থেকে তিনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হননি। উপরন্তু তিনি অত্যন্ত প্রাচুর্যের মধ্যে থেকেই জীবনের সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন। মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব ইতিহাসে তা একটি অনুপম ও বিরল দৃষ্টান্ত। সিদ্ধার্থ গৌতম সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য এবং দুঃখ মুক্তির পথ অন্বেষণের জন্য পরিবার-পরিজন, রাজ প্রাসাদের বিলাসী জীবন, স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা এবং রাজ সিংহাসনের মায়া ত্যাগ করে নেমেছিলেন পথে। সন্ন্যাস জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি বহু ধর্মীয় আচার্য এবং সাধুজনের শরণাপন্ন হন, কিন্তু কারো কাছ থেকে দুঃখের রহস্য উদঘাটনের পথের সন্ধান পেলেন না। অবশেষে তিনি তাঁর আত্মশক্তির ওপর বিশ্বাস রেখে ধ্যান মগ্ন হলেন। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষতলে বহুবৎসর কঠোর তপস্যা করে বৈশাখী পূর্ণিমার এক শুভ তিথিতে গৌতম জগতে দুঃখের রহস্য ও স্বরূপ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেন। জগতের সকল তথ্য লাভ করে তিনি হলেন সম্যক সম্বুদ্ধ, খ্যাত হন বুদ্ধ নামে। মানুষকে সঠিক পথ বা দুঃখমুক্তির পথ দেখাবার জন্য তিনি পয়ঁতাল্লিশ বছর ধর্মপ্রচার করেছিলেন। বুদ্ধ দীর্ঘকাল সকল প্রাণীর হিতসাধন করে আশি বছর বয়সে কুশীনগরের মল্লদের শালবনে আরেক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতে পরিনির্বাণ লাভ করেন। জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ (মৃত্যু)- বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবনে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সংঘটিত হয়েছিল। তাই বৈশাখী পূর্ণিমাকে বুদ্ধ পূর্ণিমাও বলা হয়। বিশ্ব বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর নিকট দিনটির আবেদন অনন্য সাধারণ এবং পবিত্র।
অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজ ব্যবস্থায় প্রজ্ঞালোক হয়ে জন্ম নিলেন জ্যোতির্ময় মহাকারুণিক বুদ্ধ এবং প্রচার করলেন সর্বজীবের কল্যাণকর বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধধর্ম বিশ্বশান্তির ধর্ম তথা বিশ্বমানবের ধর্ম। কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এ ধর্ম প্রচারিত হয়নি। বিশ্বমানবতাই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। শুধু মানুষ নয়, বিশ্বের সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী ও অশেষ করুণা হতে এ ধর্মের উৎপত্তি এবং জীবের দুঃখ বিনাশে এ ধর্মের আত্মপ্রকাশ। বুদ্ধ এমন এক সময় তাঁর দর্শন প্রচার করেছিলেন যখন প্রাচীন ভারতের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী জাতিভেদ প্রথার নিগড়ে আবদ্ধ, অসাম্য-অনাচার সর্বস্বতার দ্বারা দারুণভাবে বিপর্যস্ত, ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত এবং বিশ্বাসরূপী সংস্কারের বেড়াজালে শৃঙ্খলিত ছিল। তিনি মানুষকে কোনো প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ করেননি, বিশ্বাসরূপী শৃঙ্খল দ্বারাও বাঁধেননি। অধিকন্তু দিয়েছিলেন বুদ্ধি ও বিবেকের স্বাধীনতা। তাই তিনি নিজেকে ত্রাণকর্তা হিসেবে উপস্থাপন করেননি। বরং উপস্থাপিত হয়েছেন পথ প্রদর্শক হিসেবে। তাঁর উপদেশ ছিল ‘নিজের দ্বীপ প্রজ্বলিত করে নিজেই নিজের মুক্তির পথ পরিষ্কার কর, অন্যের ওপর নির্ভর করো না।’ বৌদ্ধ দর্শনে ভক্তির পরিবর্তে আত্মগত ধর্মনিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। ‘আত্মদীপো’, ‘আত্মশরণো’ অর্থাৎ আত্ম প্রত্যয়েই সম্বোধির পথে এগিয়ে যাওয়া, বুদ্ধের নির্দেশ।
বুদ্ধের চিন্তা চেতনার কেন্দ্রে ছিল মানুষ। অধিবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি নির্লিপ্ত থাকতেন। জগৎ শাশ্বত কি অশাশ্বত, ধ্রুব কি অধ্রুব এসব অধিবিদ্যা সংক্রান্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, ‘কোন ব্যক্তি শরাহত হলে আগে সেবা দিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলা উচিত, না কি কে শরটি নিক্ষেপ করল, কোন্ দিক থেকে শরটি এলো প্রভৃতি আগে অনুসন্ধান করা উচিত? জগৎ সংসার দুঃখের ফণায় বিকীর্ণ, জরা তরঙ্গে উদ্বেল এবং মৃত্যুর উগ্রতায় ভয়ংকর। এসব প্রশ্নের চেয়ে দুঃখ হতে মুক্তি লাভের চেষ্টা ও উপায় অনুসন্ধান করাই উত্তম।’ মানুষের দুঃখ মুক্তিই ছিল তাঁর অভীপ্সা। সমাজ যাদের পতিত হিসেবে উপেক্ষা করেছেন, তিনি তাদের উপেক্ষা করেনি। তিনি পতিতাকে টেনে তুলে, পথভ্রান্তকে পথ প্রদর্শন করে সমাজে মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আবাল-বৃদ্ধা-বনিতা সকলকে তাঁর ধর্মে স্থান দিয়ে তিনি মনুষ্যত্বের জয়গান করেছেন। তিনি নিজেকে এবং তাঁর ধর্মকে সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি এবং সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ রাখেননি। তাঁকে বলতে দেখি, ‘গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী প্রভৃতি নদী যেমন সাগরে মিলিত হয়ে নাম হারিয়ে ফেলে তেমনি ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, ক্ষত্রীয়, চণ্ডাল প্রভৃতি আমার ধর্মে প্রবেশ করে নাম হারিয়ে ফেলে, এখানে সকল মানুষ এক।’ বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত সংঘে বিভিন্ন শ্রেণি ও সম্প্রদায়ের লোক ছিল, যারা আপন মহিমা ও কৃতিত্বে সংঘের মধ্যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সর্বজনীন বাণীর সূধারস বারাঙ্গনার জীবনকেও পঙ্কিলতা মুক্ত করেছিল।
বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রদর্শন তাঁর প্রচারিত ধর্মের অনন্য দিক। তাঁর অমৃত বাণী বিশ্বের ক্ষুদ্রতম প্রাণী থেকে বৃহত্তম প্রাণীকে পর্যন্ত রক্ষার প্রেরণা জোগায়। তাঁর হাতে ছিল মানব প্রেমের বাঁশরী, কণ্ঠে ছিল মৈত্রী ও করুণা অমৃত বাণী এবং লক্ষ্য ছিল সত্য ও ন্যায়ের ধর্ম বিতরণে। তাঁকে বলতে দেখি, “সাধক ভিক্ষু! মৈত্রীপূর্ণ চিত্তে সকল প্রাণীর প্রতি অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে। মাতা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে নিজের জীবন দিয়ে রক্ষা করে, সেরূপ সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও ভালোবাসা প্রদর্শন করবে। কাকেও আঘাত করো না। শত্রুকে ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নেবে।’ তাবৎ বিশ্বের সকল প্রাণীর প্রতি বুদ্ধের মমত্ববোধ সর্বকালের মানুষের মনে এক গভীর আবেদন সৃষ্টি করেছে। এই মহামন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সম্রাট অশোক সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন, ‘রাজ্য জয়, যুদ্ধ, নিপীড়ন, যাগ-যজ্ঞ-বলী সত্যিকারের ধর্ম হতে পারে না।’ তাই তিনি হিংসা নীতি পরিহার করে মৈত্রী ভালোবাসার নীতি গ্রহণের মাধ্যমে রাজ্য জয়ের পরিবর্তে ধর্মজয়ের পথ গ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের বিশেষত্ব হলো মৈত্রী ভাবনা, যা বৌদ্ধ মাত্রই অত্যাবশ্যকভাবে পালনীয়। মৈত্রী ভাবনার মূল মন্ত্র হলো : “সকল প্রাণী সুখী হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখে কাল যাপন করুক।” এভাবে স্বীয় জীবনকে মৈত্রীর ফল্গুধারায় প্লাবিত করতে পারলে অপরের প্রতিও স্বাভাবিকভাবে মৈত্রী করুণা এসে যাবে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই মৈত্রী করুণা আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সমঝোতা আনতে সক্ষম। কারণ মৈত্রীকামী ব্যক্তির কোনো শত্রু থাকতে পারে না। মৈত্রী ভাবনার দ্বারা তিনি এমন এক মানসিক অবস্থায় উন্নীত হন, যেখানে তার নিজের এবং অন্যের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-প্রীতি হবে অভিন্ন। বুদ্ধের এই মৈত্রী বাণী সেদিন ভারতবর্ষের মানুষের কাছে এক গভীর আনন্দ সৃষ্টি করেছিল। মহামৈত্রীর এই মহামন্ত্রই সেদিন ভারতবর্ষকে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সেতু বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। এই আদর্শের ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের মর্মকোষ হতে উদগত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই বিস্তার অসুরিক সৈন্যদলের মাধ্যমে নয়, মহাকারুণিক ভিক্ষুদলের মাধ্যমে ঘটেছিল।
নৈতিক চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন, দুঃখ হতে উদ্ধার, সর্বোপরি মানুষকে প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠাই ছিল বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের মূল লক্ষ্য। অথচ মানুষ আজ এই আদর্শকে পাশ কাটিয়ে ধ্বংসাত্মক খেলায় মত্ত। সমগ্র বিশ্বে আজ সংঘাত, সন্ত্রাস, পারস্পরিক অবিশ্বাস, সম্প্রদায় ও জাতিগত ভেদাভেদ এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। পারস্পরিক সমঝোতার অভাবে পাশাপাশি রাষ্ট্রসমমূহের মধ্যে চলছে যুদ্ধের প্রস্তুতি। ইতোপূর্বেও অনেক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। তাতে জাতিগত লাভ হয়নি কিছুই। বরং সভ্যতা ও সংস্কৃতি হয়েছে বিপন্ন। শান্তিকামী মানুষ আর যুদ্ধ চায় না। সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত ভেদাভেদ চায় না। শান্তি চায়। আসুন পরিবাবে-পরিবারে, সমাজে-সমাজে এবং রাষ্ট্রে-রাষ্ট্রের সকল বৈষম্য নিরসনে বুদ্ধের উপদেশ মেনে চলি। সবাই সমস্বরে বলি, ‘সব্বে সত্তা সুখীতা ভবন্ত- জগতের সকল জীব সুখী হোক’।
লেখক : চেয়ারম্যান, পালি অ্যান্ড বুড্ডিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, সহকারী প্রক্টর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল