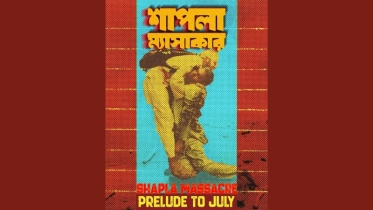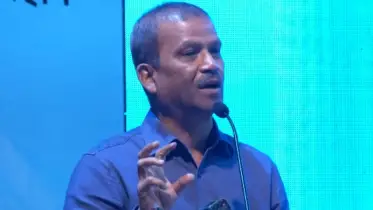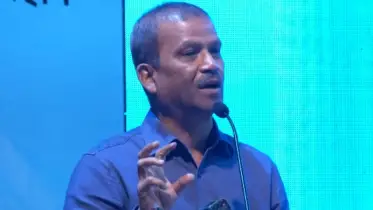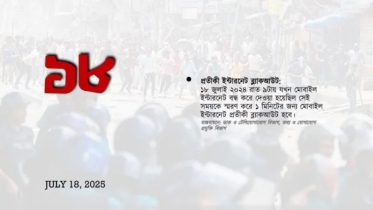জনকণ্ঠ ডেস্ক ॥ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেবল তার দেশের নেুা নন, সম্ভবত তিনি এই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তার অনেক সিদ্ধান্তের প্রভাব বিশ্বের সব মানুষের ওপর পড়ে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময়ও তাই ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে এই বিশ্বকে কতটা বদলে দিয়েছেন ট্রাম্প? তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে বিবিসির এক প্রতিবেদনে।
বিশ্ব দর্পণে আমেরিকা ॥ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বরাবরই যুক্তরাষ্ট্রকে ‘বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম দেশ’ বলে দাবি করে এসেছেন। কিন্তু বিশ্বের মানুষ কী ভাবছে?
সম্প্রতি ১৩ দেশে পিউ রিসার্চ সেন্টারের চালানো এক জরিপে দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে দেশের ভাবমূর্তির খুব বেশি উন্নয়ন ঘটাতে পরেননি ট্রাম্প।
ইউরোপের অধিকাংশ দেশে যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করা মানুষের সংখ্যা এখন ২০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে কম।
যুক্তরাজ্যে জরিপে অংশ নেয়া ব্যক্তিদের ৪১ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্র নিয়ে ইতিবাচক ধারণা পোষণ করার কথা বলেছেন। ফ্রান্সে এই হার ৩১ শতাংশ, যা ২০০৩ সালের পর থেকে সবচেয়ে কম। আর জার্মানিতে এই হার মাত্র ২৬ শতাংশ। বিবিসি লিখেছে, করোনাভাইরাস মহামারী সামাল দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জুলাই-আগস্ট সময়ে ওই জরিপের উত্তরদাতাদের মাত্র ১৫ শতাংশ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র পরিস্থিতি ভালভাবে সামলাতে পেরেছে বলে তারা মনে করেন।
জলবায়ু যুদ্ধে উল্টোরথ ॥ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আসলে কী ভাবেন, তা সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করা সহজ নয়। কখনও তিনি বিষয়টিকে ‘চড়া দামের এক গুজব’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, কখনও আবার বলেছেন ‘সিরিয়াস সাবজেক্ট’, যা নাকি তার কাছে ‘খুবই গুরুত্বপূর্ণ’।
তবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেয়ার ছয় মাসের মধ্যে প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়ে তিনি বিজ্ঞানীদের হতাশ করেছেন।
বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার প্রাক শিল্পায়ন যুগের চেয়ে ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের বেশি যেন না হতে পারে, সেজন্য নিঃসরণের মাত্রা সম্মিলিতভাবে কমিয়ে আনার অঙ্গীকার করা হয়েছে ২০১৫ সালের ওই চুক্তিতে। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৮৯ দেশ ওই চুক্তিতে অনুস্বাক্ষর করেছে।
চীনের পর যুক্তরাষ্ট্রই বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণ করে। গবেষকদের আশঙ্কা, ট্রাম্প পুনর্নির্বাচিত হলে বৈশ্বিক উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।
ট্রাম্পের যুক্তি, প্যারিস চুক্তি মানতে গেলে যেসব বিধিনিষেধ আসবে, তাতে যুক্তরাষ্ট্রের বহু কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে।
তিনি কেবল প্যারিস চুক্তি থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে আনেননি, কয়লা, তেল ও গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনের খরচ কমাতে কিছু নিয়ম শিথিলও করেছেন।
সীমান্ত বন্ধ, কারও কারও জন্য ॥ প্রেসিডেন্ট হিসেবে অভিষিক্ত হওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অভিবাসনের নিয়ম বদলাতে তৎপর হন ট্রাম্প। সে সময় সাত মুসলিম প্রধান দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকার পথ বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে মোট ১৩ দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্র সফরে কড়াকড়ি চলছে।
যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারীদের মধ্যে বিদেশে জন্মগ্রহণকারীর যে সংখ্যা প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার শেষ বছর ২০১৬ সালে ছিল, ২০১৯ সালে এসে তা ৩ শতাংশ বেড়েছে। তবে পরিবর্তন এসেছে তাদের পরিচয়ে।
যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দাদের মধ্যে মেক্সিকো থেকে আসা মানুষের সংখ্যা ট্রাম্পের সময়ে ধারাবাহিকভাবে কমেছে। তবে লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে আসা মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেয়ার হারও এই সময়ে কমে এসেছে, বিশেষ করে যাদের পরিবারের কেউ যুক্তরাষ্ট্রে আছেন, তাদের ক্ষেত্রে কড়াকড়ি বেড়েছে।
ট্রাম্পের অভিবাসন নীতিকে যদি কোন সিলমোহর দিয়ে চিত্রায়িত করতে হয়, তাহলে তা হবে একটি দেয়ালের ছবি, যা তিনি নির্মাণ করছেন মেক্সিকো সীমান্তে।
সরকারী তথ্য অনুযায়ী, গত ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ৩৭১ মাইল দেয়াল নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। অবশ্য মরিয়া অভিবাসীদের আমেরিকামুখী যাত্রা তাতে কমেনি।
‘ফেক নিউজ’ ॥ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যেসব শব্দ বা শব্দবন্ধকে অন্যরকম উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন, তার মধ্যে সবার আগে কোনটির কথা আসবে? ২০১৭ সালে এক সাক্ষাতকারে ট্রাম্প নিজেই বলেছেন- সেটি হবে ‘ফেক নিউজ’।
না, ট্রাম্প নিজে ‘ফেক নিউজ’ শব্দবন্ধটি উদ্ভাবন করেননি, তবে তিনিই যে একে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি দিতে পেরেছেন, তাতে কারও সন্দেহ নেই।
সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ও অডিও ট্রান্সক্রিপ্ট পর্যবেক্ষণ করে ফ্যাক্টবিএ ডট এসই বলছে, ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে প্রথম বার ‘ফেক নিউজ’ টুইট করার পর এ পর্যন্ত অন্তত দুই হাজার বার ওই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন ট্রাম্প।
কেউ যদি ‘ফেক নিউজ’ লিখে গুগলে সার্চ করেন, তাহলে তিনি বিশ্বে ১.১ বিলিয়নের বেশি ভুক্তি পাবেন। গুগল সার্চ ট্রেন্ড দেখলে বোঝা যাবে, ২০১৬-১৭ সালের শীতের দিনগুলোতে ওই শব্দবন্ধটি নিয়ে মানুষের আগ্রহ কীভাবে বেড়ে গিয়েছিল, আর তা তুঙ্গে উঠেছিল যখন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ‘ফেক নিউজ এ্যাওয়ার্ড’ দেয়ার কথা বলেছিলেন।
অন্তঃহীন যুদ্ধ ॥ ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্টেট অব দ্য ইউনিয়ন ভাষণে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দিলেন, সিরিয়া থেকে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবেন, কারণ ‘কোন মহৎ রাষ্ট্র অন্তঃহীন যুদ্ধকে সমর্থন করে না।’ তবে কয়েক মাস বাদে তিনি সিদ্ধান্ত দিলেন, শ’ পাঁচেক মার্কিন সৈন্য সিরিয়ায় থাকবে, কারণ তেলকুপগুলোতে নিরাপত্তা তো দিতে হবে! তিনি দায়িত্ব নেয়ার সময় আফগানিস্তানে যত মার্কিন সেনা ছিল, সেই সংখ্যাও তিনি কমিয়ে আনার ঘোষণা দেন, একই সিদ্ধান্ত হয় ইরাকের ক্ষেত্রেও। কিন্তু সব জায়গাতেই এখনও মার্কিন সেনারা আছে।
সৈন্য না রেখেও মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব জারি রাখার উপায় নিশ্চয় আছে। ২০১৮ সালে ট্রাম্প যখন জর্দান নদীর পশ্চিম তীরসহ জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানীর স্বীকৃতি দিলেন এবং তেল আবিব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নিলেন, সাবেক প্রেসিডেন্টরা তাতে আপত্তি করেছিলেন। তবে ট্রাম্প তা কানে তোলেননি।
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাত সম্প্রতি যখন ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চুক্তি করল, ট্রাম্প তাকে বর্ণনা করলেন এক ‘নতুন মধ্যপ্রাচ্যের সূচনালগ্ন’ হিসেবে।
মনের মতো চুক্তি ॥ যে চুক্তিতে নিজে ছিলেন না, তা মানতে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রবল আপত্তি আছে। ওভাল অফিসে বসার প্রথম দিনই তিনি ১২ দেশের ‘ট্রান্স প্যাসিফিক পার্টনারশিপ’ চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দেন, যা অনুমোদন করে গিয়েছিলেন তার পূর্বসূরী প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ট্রাম্পের ভাষায় ওই চুক্তি ছিল ‘জঘন্য’।
যুক্তরাষ্ট্র ওই চুক্তি থেকে সরে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশি লাভ হয়েছে চীনের। কারণ ওই চুক্তি করাই হয়েছিল এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে চীনের প্রভাব খর্ব করার লক্ষ্য নিয়ে।
কানাডা আর মেক্সিকোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি ছিল, ট্রাম্পের আমলে তা করা হলো নতুন করে। ট্রাম্পের ভাষায় আগের করা চুক্তিগুলো ছিল ‘ইতিহাসের সবচেয়ে বাজে চুক্তি’। নতুন চুক্তিতে শ্রমিক নিয়োগ আর গাড়ির যন্ত্রাংশ আমদানির নিয়মে কিছু কড়াকড়ি বাড়লেও বাকি নিয়মকানুন মোটামুটি আগের মতোই থাকল।
অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্র কতটা লাভবান হচ্ছে, তা নিশ্চিত করাই ছিল ট্রাম্পের লক্ষ্য। আর তার ফলে চীনের সঙ্গে তিক্ত এক বাণিজ্য যুদ্ধের সূচনা হলো, বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির এ দুই দেশ পরস্পরের পণ্যের ওপর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের করের বোঝা চাপিয়ে দিতে লাগল।
তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন চাষীদের পাশাপাশি মোটরগাড়ি ও প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের মাথায় হাত পড়ল। ক্ষতি গুনতে হলো চীনকেও, কারণ বহু কোম্পানি করের খরচ থেকে বাঁচতে সেখান থেকে সরে যেতে লাগল ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়ার মতো দেশে।
সবকিছুর পর ২০১৯ সালে চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতির যে অংক দাঁড়াল, তা ২০১৬ সালের তুলনায় সামান্যই কম।
ট্রাম্পের ট্যারিফ এড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলো চীন থেকে আমদানি করার প্রবণতা কিছুটা কমিয়েছে। কিন্তু এখনও চীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের আমদানির পরিমাণ রফদানির চেয়ে বেশি।
চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ॥ ২০১৬ সালের ৩ ডিসেম্বর একটি টুইট করলেন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই টুইটের বিষয়বস্তু যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির এতটাই বিপরীত ছিল যে উইকিপিডিয়াকে ওই ঘটনা নিয়ে নতুন একটি পৃষ্ঠা খুলতে হয়েছে।
২ ডিসেম্বর ট্রাম্প টেলিফোনে সরাসরি কথা বলেন তাইওয়ানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে, যে কাজটি ১৯৭৯ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের আর কোন প্রেসিডেন্ট কখনও করেননি। ওই বছরই তাইওয়ানের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল যুক্তরাষ্ট্র।
পরদিন নিজেই টুইট করে সেই ফোনালাপের কথা বিশ্বকে জানালেন ট্রাম্প; বললেন, তাইওয়ানের প্রেসিডেন্ট তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।
অনেকেই ধারণা করেছিলেন, চীন বিষয়টি ভালভাবে নেবে না, কারণ তাইওয়ানকে নিজেদের একটি প্রদেশ বলেই দাবি করে বেজিং।
বর্তমান বিশ্বের ভূ-রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী চীনের সঙ্গে বহুমুখী খোঁচাখুঁচি প্রতিযোগিতার সেটা ছিল ট্রাম্পীয় সূচনা। এর জেরে পরের দিনগুলোতে দুই দেশের সম্পর্ক নামল তলানিতে।
বেজিংকে খেপিয়ে তুলতে ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা দিল, দক্ষিণ চীন সাগরের সীমানার অধিকার নিয়ে চীনের দাবি ‘অবৈধ’। চীনা পণ্যের ওপর দফায় দফায় শুল্ক আরোপ করা হলো। টিকটক আর উইচ্যাটের মতো জনপ্রিয় চীনা এ্যাপ যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ করা হলো। টেলিকম জায়ান্ট হুয়াওয়েকে কালো তালিকাভুক্ত করা হলো, কারণ ট্রাম্পের ভাষায়, ওই চীনা কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।
বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়া কোভিড-১৯ কে ট্রাম্প নাম দিলেন ‘চীনা ভাইরাস’, কারণ চীনেই এর প্রাদুর্ভাবের সূচনা হয়েছিল।
তিনি হয়ত যুক্তরাষ্ট্রে মহামরীর প্রকোপ সামলাতে ব্যর্থতা থেকে দৃষ্টি সরাতে চেয়েছিলেন, তবে আগামী নির্বাচনে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব বদলালেই যে চীনের সঙ্গে দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে, তা নাও হতে পারে। কারণ ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী বাইডেনও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে ‘ঠগ’ আখ্যায়িত করেছেন; তার ভাষায় চীনা নেতার শরীরে গণতন্ত্র বলে কিছু নেই।
যুদ্ধের দুয়ারে ॥ ‘আমাদের কোন স্থাপনা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কোন প্রাণহানি যদি ঘটে, ইরান তার জন্য পুরোপুরিভাবে দায়ী থাকবে, আর সেজন্য তাদের অনেক বড় খেসারত দিতে হবে! এটা কোন সতর্কবার্তা নয়, এটা সরাসরি হুমকি।’ এটা ছিল ২০১৯ সালের শেষে মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ টুইট।
কয়েক দিন বাদে পুরো বিশ্ব বিস্ময়ের সঙ্গে জানল, ইরানের সবচেয়ে ক্ষমতাধর জেনারেল কাশেম সুলেমানিকে ইরাকে ড্রোন হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে ইরানের গোপন সামরিক কর্মকা-ের নেতৃত্ব দিয়ে আসছিলেন সুলেমানি। স্বাভাবিকভাবেই প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিল ইরান। ইরাকে যুক্তরাষ্ট্রের দুটি সামরিক ঘাঁটিতে এক ডজনের বেশি ব্যালিস্টিক মিসাইল ছোড়া হলো। তাতে শতাধিক মার্কিন সেনার আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেল। সবাই ভাবলেন, যুদ্ধ বুঝি লেগেই গেল।
সে দফা আর যুদ্ধ হয়নি, কিন্তু নিরীহ মানুষের প্রাণ ঠিকই গেছে। ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলার কয়েক ঘণ্টা বাদে উত্তেজনার মধ্যে ইরানী সামরিক বাহিনী ভুল করে ইউক্রেনের একটি যাত্রীবাহী বিমানকে মিসাইল ছুড়ে ভূপাতিত করে, নিহত হন ১৭৬ আরোহীর সবাই।
বারাক ওবামা প্রশাসন যেখানে ইরানকে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে সরিয়ে আনতে চুক্তি করেছিল, উত্তেজনা প্রশমনে তেহরানের ওপর থেকে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল, সেই চুক্তি বাতিল করে ২০১৮ সালের মে মাসে নতুন করে উত্তেজনা ফিরিয়ে আনেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ইরানের ওপর আরোপ করা হয় হোয়াইট হাউজের ভাষায় ‘কঠোরতম’ নিষেধাজ্ঞা। এর লক্ষ্য ছিল, ইরানকে ট্রাম্পের মর্জিমাফিক নতুন একটি চুক্তিতে আনতে বাধ্য করা।
এরপর এল করোনাভাইরাস মহামারী, তাতে যুক্তরাষ্ট্র আর ইরান- দুই দেশই ক্ষতিগ্রস্ত হলো দারুণভাবে। রাজনীতির টানাপোড়েন তাতে আপাতত চাপা পড়লেও শত্রুতার পুরনো কারণগুলো অক্ষতই থেকে গেল।
ঢাকা, বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার ০৩ জুলাই ২০২৫, ১৯ আষাঢ় ১৪৩২