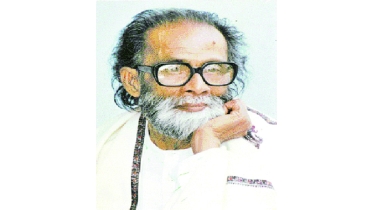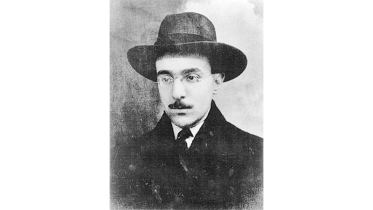‘যখন চারিদিকে মৃত্যু আর মৃত্যু লাশ আর লাশ/যখন দিকে দিকে টগবগে বিক্ষোভ বিস্ময়/প্রতিরোধের উত্তাপে ফুটন্ত বিপ্লব/সেই জুলাই বিপ্লবের আগুন ঝরাদিন!/ হৃদয় নিংড়ানো রঙের আঁচড়ে /তখনই জন্মালো গ্রাফিতি!/ এমন এঁকেছে কি পৃথিবীর কোনো বিপ্লবের তুলি!/ঢাকার প্রতিটি দেয়াল গ্রাফিতির/একেকটি বর্ণিল পৃষ্ঠা/প্রতিবাদ- বিক্ষোভের বিশাল ক্যানভাস/ হৃদয়গ্রাহী স্লোগান, কবিতার বারুদ যেনো/ কোটি কণ্ঠের সমস্বর!/বৈষম্যহীন আন্দোলনের এ এক শিল্পিত রূপ!/শিল্পকর্মে জ্বলে উঠলো একেকটি বাক্য/একেকটি স্লোগান, তীব্র তীক্ষè বুলেট,/ বিঁধে গেলো ফ্যাসিস্ট স্বৈরিণীর বুকের শিরায়/আগ্নেয়াস্ত্র পরাজিত এসব গ্রাফিতির/ রেখার কাছে! /রাজপথের দেয়াল প্রাসাদের পাঁজর এবং পিচপথের কালো দেহে গ্রাফিতির সমগ্রতায় জড়ানো সাহসের প্রাণ!/চোখ উল্টিয়ে জগতবাসী দেখলো-/দুনিয়ার গ্রাফিতির রাজধানী বাংলাদেশ!/ গ্রাফিতির মতো এমন অস্ত্র আমি আর দেখিনি!-’
কবি জাকির আবু জাফরের ‘গ্রাফিতি’ শিল্প, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের সামর্থ্যবান শব্দে উচ্চারিত বিপ্লবী কবিতা। শুধু নির্দিষ্ট সময়ের ঘটনাপ্রবাহ নয়, বরং সকল গণআন্দোলনের পক্ষে শক্তিশালী শব্দাঙ্কিত চিত্র। এই কবিতায় গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করা মানুষের সৃষ্টিশীল প্রকাশ-শক্তির উপস্থিতি লক্ষণীয়। এখানে দেওয়াল হয়েছে শিল্প চিত্রণের ক্যানভাস, শব্দ বিপ্লবের অস্ত্র। গ্রাফিতি মূলত ‘উদ্ভ্রান্ত শিল্প’, যা প্রথাগত নান্দনিক কাঠামোর আওতায় না থেকে প্রকাশ ঘটায় বিদ্রোহের যা গণজাগরণের চূড়ান্ত প্রতীক। এতে রয়েছে সামষ্টিক স্বর যা ব্যস্টির চেতনার প্রতিচিত্র। এখানে শক্তিমানের বিরুদ্ধে দেওয়ালচিত্রে সমবেত জনগণের প্রতিরোধের চিত্র দোলনার মতো দোলায় পাঠকের ভাবচিত্তে চিন্তাসূত্র জন্ম দেয়। এখানে কবি গ্রাফিতিকে কেবল ভিজ্যুয়াল আর্ট বা পথচিত্র হিসেবে চিত্রিত করেননি, রাজনৈতিক অভিব্যক্তি প্রকাশের মাধ্যম করেছেন। গ্রাফিতি মূলত একটি প্রতীকী চিত্র বিবৃত করে ‘শিল্প ও প্রতিরোধের ভাষা হয়ে তীব্রবোধ মানুষের মনে জাগ্রত করতে সক্ষম।
কবিতায় ‘গ্রাফিতি’ শব্দটি একটি কেন্দ্রীয় চিহ্ন, যার অর্থ শুধু চিত্র নয়, বরং তা প্রতিবাদের ভাষা, বিপ্লবের রূপ, শিল্পের অস্ত্র, অর্থাৎ বহুমাত্রিক সংকেত যা বহুমাত্রিক অর্থকে ধারণ করে। ‘রঙের আঁচড়ে’, ‘কবিতার বারুদ’, ‘স্লোগান, তীব্র তীক্ষ্ণ বুলেট’ এসব উপমা এবং রূপকের মাধ্যমে কবিতা দেখায় কিভাবে ভাষা নিজেই বাস্তবতার কাঠামোকে গঠন করে। কবিতায় ক্ষমতার কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করা পুনরবিন্যস্ত করার বহুমাত্রিক অভিব্যক্তি ধারণ করে। দেওয়াল, পিচপথ বা প্রাসাদের পাঁজর প্রতিটি জায়গা নিজস্ব ভাষা নিজের মতো করে অর্থকে দ্যোতিত করছে। অর্থ আর কোনো একক কেন্দ্র [যেমন রাষ্ট্র বা শাসকের ভাষা] থেকে সৃষ্ট নয়, বরং বহুবিধ জায়গা থেকে বিকিরিত। ‘দেরিদার’ ‘ডিফারেন্স’ ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ‘ঢাকার প্রতিটি দেওয়াল গ্রাফিতির/একেকটি বর্ণিল পৃষ্ঠা’ এটি পাঠককে দেওয়ালকে ‘টেক্সট’ হিসেবে পড়তে শেখায়। অর্থাৎ, এখানে গ্রাফিতি নিজেই পাঠযোগ্য এক বয়ান। স্লোগান, চিত্র, রং সবই একত্রে মিলে তৈরি করে সেমিয়োটিক কোড [অর্থ জোগানের পদ্ধতিগত অধ্যয়ন] যা ক্ষমতা, প্রতিরোধ ও জনতার চেতনার কাঠামো নির্মাণ করে। কবিতাটি স্পষ্টভাবে দাঁড় করায় দুটি বিপরীত কাঠামো ‘ফ্যাসিবাদ বনাম গণবিপ্লব’ ‘প্রাসাদ বনাম রাজপথ’ ‘আগ্নেয়াস্ত্র বনাম গ্রাফিতির রেখা’
এসব বিরোধিতা দেরিদার আলোকে ক্রম বিন্যাস ভিত্তিক হায়ারিক্যাল অপজিশন [ সমস্ত প্রতিকূলতা তুচ্ছ করে অর্থ নির্ণয় করে এমন] যেখানে সাধারণত প্রথমটি প্রাধান্য পায়। কিন্তু এই কবিতায় নিচের/দমিত প্রতিচিত্র [যেমন : গ্রাফিতি] এক সময় প্রাধান্যহীন কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করে, কেন্দ্রকে ভেঙে দেয়। দেরিদা মূলত ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য-চিন্তায় বৈপরীত্যগুলো [যেমন : পুরুষ/নারী, আলো/অন্ধকার, বক্তা/লিখিত] ধারণাটি বিশ্লেষণ করেন। দেরিদা বলেন, বিরোধগুলোর কোনোটা এক সময়ে ক্ষমতাশালী বা প্রধান বলে গণ্য হওয়ার সুযোগ পায় এবং অন্যটি অধীনস্ত থাকে। এটাকে লোগোসেন্ট্রিজম বলা হয়। দেরিদার কাছে ভাষা বিন্যাস মূলত দার্শনিক কাঠামোকে ভাঙে। লুই দু্যঁম ফরাসি নৃবিজ্ঞানী তার গবেষণা থেকে প্রকাশ করেন যে, সমাজের ধারণা বা শব্দের কিছু মান যেমন ‘পবিত্র/অপবিত্র’ ক্রমভিত্তিক বিরোধের ভেতর দিয়ে সাংগঠনিক রূপ নেয়। ডুমন্ট মনে করেন, বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতিতে বিপরীত ধারণাগুলো কেবল একে অপরের থেকে আলাদা নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিবিন্যাসের অধীনে সাজানো থাকে। অর্থাৎ- একটি ধারণা অন্যটির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা ব্যাপক হতে পারে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি ধারণা অন্যটিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং একই সঙ্গে তার থেকে আলাদা থাকে। ‘গ্রাফিতি’ কবিতা নিজেই এক ধরনের গ্রাফিতি একটা টেক্সট যা নিজেকে উপস্থাপন করে ‘গ্রাফিতি’র পুনর্নিমাণ/ পুনঃপ্রতিলিপি হিসেবে উপস্থাপন করে। নৃবিজ্ঞানী ডুমন্ট তাঁর গবেষণায় ভারতীয় বর্ণপ্রথাকে এই তত্ত্বের একটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।
‘জুলাই বিপ্লব’, ‘বিপ্লবের আগুন’, ‘ফ্যাসিস্ট স্বৈরিণী’ এগুলো কেবল প্রতীক নয়, বরং ঐতিহাসিক চেতনার উপাদান। এই কবিতায় ইতিহাস অতীত নয়, বরং এক জ্বলন্ত সমসাময়িক বাস্তব, যা দেওয়ালে ভাষায়িত হয়েছে। এইভাবে কবিতা হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক ‘ডিসকোর্স’-এর অংশ, যেখানে ভাষা, চিত্র এবং ইতিহাস পরস্পরকে নির্মাণ করে। কবিতাটি তার কাঠামোর মধ্যেই প্রতিবাদ ও শিল্পচেতনার বিস্ফোরণ। ভাষা ও চিহ্নের খেলা, অর্থের ব্যাখ্যা, কেন্দ্র ও প্রান্তের দ্বন্দ্ব, পাঠযোগ্য দেওয়াল এবং ইতিহাসের দৃশ্যভাষা এই সব মিলিয়ে কবিতাটি কাঠামোবাদী বিশ্লেষণে এক সমৃদ্ধ ক্ষেত্র তৈরি করেছে। ‘রঙের আঁচড়ে’, ‘কবিতার বারুদ’, ‘স্লোগান, তীব্র তীক্ষ্ণ বুলেট’ এসব উপমা এবং রূপকের মাধ্যমে কবিতার ভাষা বাস্তবতার কাঠামোকে গঠন করেছে। ‘গ্রাফিতি’ ক্ষমতার কেন্দ্রকে চ্যালেঞ্জ করা এক পুনরবিন্যস্ত অভিব্যক্তি। দেওয়াল, পিচপথ বা প্রাসাদের পাঁজর প্রতিটি জায়গা নিজস্ব ভাষা ধারণ করছে। শেষে বলা ভুল হবে না, সমকালীন কবিতায় রাজনীতি, প্রতিবাদ এবং জনচেতনাকে চিত্রভাষায় রূপান্তর করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ উদাহরণ হলো ‘গ্রাফিতি’ কবিতাটি। আলবেয়ার কামু বলেন, কবিতাটি নন্দনতাত্ত্বিকভাবে ‘প্রতিবাদের শিল্প’ বা ‘অস্ত্ররূপী কাব্যিক প্রকাশ’ কামুর দর্শনে জীবনের অর্থহীনতা এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তার মতে, ‘এই বিশ্ব এক শূন্যতা, কিন্তু মানুষ নিজের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে তাৎপর্য তৈরি করতে পারে। তিনি আরও বলেন ‘বিদ্রোহ ছাড়া মানুষ কেবলই দাস।’ প্রতিরোধ কেবল অস্ত্রের মাধ্যমে হয় না, বরং শিল্পের মাধ্যমেও হয়। গ্রাফিতি কবিতাটি কবি জাকির আবু জাফরকে বিশেষ করে উপস্থিত করে।
প্যানেল