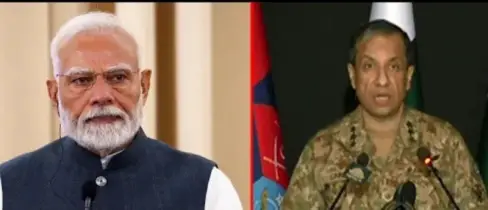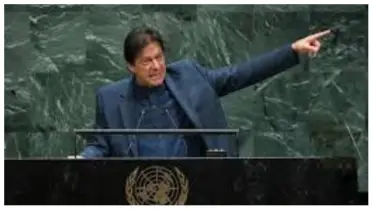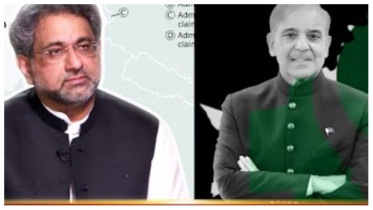ছবি : সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি যুদ্ধবিমান বিশ্বজুড়ে অত্যাধুনিক ডিজাইন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তি এবং পরীক্ষিত অস্ত্রসজ্জার জন্য স্বীকৃত। যুক্তরাষ্ট্র আজকের বিশ্বের এক নম্বর সামরিক শক্তি হিসেবে পরিচিত। ফলে অনেক দেশ এই শক্তির একটি অংশ নিজেদের সামরিক বাহিনীতে যুক্ত করতে চায়, যার ফলে মার্কিন যুদ্ধবিমান কেনার প্রতি তাদের আগ্রহ সর্বদা তুঙ্গে থাকে। অনেকেই মনে করে, যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যুদ্ধবিমান কিনলে কেবল একটি বিমান নয় বরং সেই শক্তির অংশীদারিত্বও পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবতা অনেক ক্ষেত্রেই ভিন্ন।
যখন কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুদ্ধবিমান কিনে, তখন তা শুধু একটি বিমান কেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। এর সাথে যুক্ত হয় একাধিক শর্ত, নিষেধাজ্ঞা এবং জটিল টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস। যা মূলত মনে করিয়ে দেয়, আপনি হয়তো সেই যুদ্ধবিমানের মালিক, কিন্তু আসল নিয়ন্ত্রণ আপনার হাতে নেই। অতীতে পাকিস্তান, ইরান, ভেনেজুয়েলা এবং ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো এ বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছে। তারা যুদ্ধ চলাকালীন নিজেদের কেনা বিমান ব্যবহার করতে পারেনি। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের বিমানগুলো তখন হ্যাঙ্গারে পড়ে ছিল, যেন ধাতব শো পিচে পরিণত হয়েছে।
এই পরিস্থিতির সূচনা হয় ‘এন্ড ইউজার এগ্রিমেন্ট’ (End User Agreement) নামক একটি চুক্তির মাধ্যমে। এতে স্পষ্ট করে বলা থাকে, যুদ্ধবিমান কিভাবে, কোথায় এবং কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যাবে, তা নির্ধারণ করবে যুক্তরাষ্ট্র। প্রতিটি বিমানেই ওয়াশিংটনের থাকবে সরাসরি নজরদারি। ফলে বিমানের ব্যবহার নিয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেয়ার সুযোগ থাকে না। যেমনটি দেখা গেছে ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে। পাকিস্তান তাদের এফ-১৬ ব্যবহার করে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে পারত, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি না থাকায় সেই বিমানগুলো কেবল সীমান্তে চক্কর দিয়েই ফিরে এসেছে। কোনো যুদ্ধমিশনে ব্যবহৃত হয়নি।
এরপর আসে আইটি এআর (International Traffic in Arms Regulation বা ITAR) নামক আরেকটি বিধিনিষেধ, যা শুধু অস্ত্র বিক্রির নিয়ন্ত্রণই করে না, বরং প্রতিটি যন্ত্রাংশ, সফটওয়্যার কোড এবং আপগ্রেড প্রক্রিয়াতেও যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী দখলদারি নিশ্চিত করে। অর্থাৎ, কোনো দেশ চাইলেও তাদের বহরে থাকা মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো রিপেয়ার বা আপগ্রেড করতে পারে না যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া। এমনকি ন্যাটো মিত্র দেশগুলোও পুরোপুরি মুক্ত নয়। ২০১০ সালে যুক্তরাজ্যের বিএই সিস্টেমকে ITAR লঙ্ঘনের জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছিল।
এই নিয়ন্ত্রণ শুধু কাগজে-কলমেই সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবের মাটিতে আরও গভীরভাবে প্রভাব ফেলে। মার্কিন যুদ্ধবিমানগুলো এতটাই জটিল প্রযুক্তিনির্ভর যে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ, যন্ত্রাংশ পরিবর্তন কিংবা সফটওয়্যার আপডেটের জন্যও আমেরিকান ম্যানুফ্যাকচারারদের ওপর নির্ভর করতে হয়। যদি যুক্তরাষ্ট্র কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয় বা কোনো দেশকে শাস্তি দিতে চায়, তখনই স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। যেমনটি ঘটেছে ইরানের ক্ষেত্রে। ১৯৭০ দশকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রিয় মিত্র ইরান প্রায় ৮০টি অত্যাধুনিক এফ-১৪ টমক্যাট যুদ্ধবিমান কিনেছিল। কিন্তু ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র সব ধরনের সাপোর্ট, যন্ত্রাংশ সরবরাহ এবং সফটওয়্যার আপডেট বন্ধ করে দেয়। ফলে এই সেরা যুদ্ধবিমানগুলো একে একে অচল হয়ে পড়ে।
এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে ভেনেজুয়েলাও। তারা ১৯৮০-এর দশকে এফ-১৬ কিনেছিল। কিন্তু হুগো চাভেজের আমেরিকা-বিরোধী অবস্থানের কারণে যুক্তরাষ্ট্র তাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং সমস্ত স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখা যুদ্ধবিমানগুলো তখন আর আকাশে উড়তে পারেনি। একইভাবে ইন্দোনেশিয়া ১৯৮০ সালে এফ-৫ টাইগার টু কিনেছিল। কিন্তু ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরে গণহত্যার অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ার ওপর সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে যুদ্ধবিমানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়।
এর পাশাপাশি মার্কিন যুদ্ধবিমান কেনার সময় চুক্তিতে ছোট হরফে উল্লেখ থাকে, এই বিমানগুলো অন্য কোনো দেশকে বিক্রি করা যাবে না, বিক্রির ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি লাগবে। এসব শর্ত কেবল চুক্তির কাগজেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এগুলো হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের রাজনৈতিক বন্ধক। যুদ্ধবিমান কেনার মাধ্যমে একটি দেশ শুধু প্রযুক্তিই নয়, একটি কূটনৈতিক আনুগত্যও কিনে নেয়, যার দাম দিতে হয় শুধু অর্থ দিয়ে নয়, স্বাধীনতা দিয়েও। সুদের হার অনেক সময় এত বেশি হয়ে যায় যে আকাশে ওড়ার স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয় না।
তবে সব কিছু সত্ত্বেও বিকল্পের অভাব নেই। ফ্রান্সের রাফায়েল, সুইডেনের গ্রিপেন, রাশিয়ার এসইউ-৩৫ কিংবা চীনের জে-১৬ , এসব বিকল্প যুদ্ধবিমান প্রযুক্তিগত সক্ষমতার পাশাপাশি আরও স্বাধীন ব্যবহারের সুযোগ দেয়। তবে প্রতিটি বিকল্পের সাথেও থাকে নিজস্ব শর্ত এবং রাজনৈতিক-সামরিক জটিলতা। স্বাধীনতা বিনা খরচে আসে না, এই সত্যই প্রমাণ করে। প্রশ্ন হলো, আপনি কার কাছে সেই স্বাধীনতাকে বন্ধক রাখতে চান, নাকি নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলবেন? যেমনটা করেছে তুরস্ক। তারা এখন নিজস্ব যুদ্ধবিমান উন্নয়নে কাজ করছে।
সুতরাং, যখন কোনো দেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুদ্ধবিমান কেনে, তখন তারা কেবল একটি যোদ্ধা বিমান কেনে না, তারা কিনে নেয় একগুচ্ছ শর্ত, কিছু অদৃশ্য নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক আনুগত্যের এক অপূর্ব মিশ্রণ। যুদ্ধবিমানের ডানায় অদৃশ্য অক্ষরে লেখা থাকে – Terms & Conditions Applied।
আঁখি