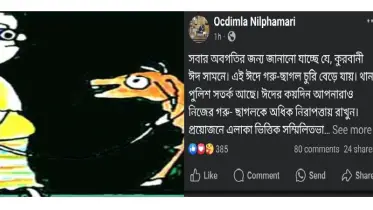‘জীর্ণ বস্ত্র শীর্ণ গাত্র ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ/ডাকিল পান্থ ‘দ্বার খোলো বাবা, খাইনিকো সাত দিন।’/সহসা বন্ধ হলো মন্দির, ভুখারি ফিরিয়া চলে,/তিমির রাত্রি, পথজুড়ে তার ক্ষুধার মানিক জ¦লে।’ এই ক্ষুধার মানিক নিরন্তর জ্বলেছে কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়। সকল দেশের সকল কালের আর্ত মানবতার বেদনার সুর তার কাব্যে ঝঙ্কৃত। এ কাব্য শুধু যুগোত্তীর্ণ নয় - এ কাব্য অন্তহীন-কালের।
তার প্রথম প্রকাশিত কবিতা ‘মুক্তি’ একজন ধুলিমলিন বিকলাঙ্গ ফকিরকে নিয়ে যে গাছতলায় থাকে, পথচারীর দয়ার দানই যার অন্ন। ঈষৎ পর ‘গরিবের ব্যথা’ কবিতায় দরিদ্র পথবাসী শিশুদের চিত্র উন্মোচিত, ‘ক্লিষ্ট শিশুগুলো/ পরণে নেই ছেঁড়া কানি, সারা গায়ে ধুলি/সারাদিনের অনাহারে শুষ্ক বদনখানি, / খিদের জ¦ালায় ক্ষুণœ, তাতে জরের ধুকধুকানি . . / আ-লোনা মাড়-ভাত খেয়ে যে বাচে এসব ছেলে . . / দুঃখ এদের কেউ বোঝে না, ঘেন্না সবাই করে, / ভাবে এসব বালাই কেন পথেই ঘুরে মরে ?’ এসব বালাই আজও পথেই ঘুরে মরে।
প্রত্যন্ত গ্রামের মাটির ঘর, ছনের ছাউনিতে জন্ম নেয়া নজরুল ‘ছেলেবেলা থেকে পথে পথে থাকা মানুষ’- তিনি উন্মুক্ত পথের কবি। ভিতর থেকেই দেখেছেন মানুষের দুঃখ দৈন্য, ‘গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরিয়া দেখিয়াছি পায়ে দলা কাদামাখা কুসুম, / বক্ষে লইয়া কাদিছে মা, চক্ষে পিতার নাহিকো ঘুম !/ শিয়রে দীপে তৈল নাই . .।’ সারা বাংলার এই তো রূপ। কয়লা খনির শ্রমিকদের কঠিন করুণ জীবনের দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন প্রথম জীবনে ‘নবযুগ’ পত্রিকায় । গরিব দুঃখীদের কথা পত্রিকায় পাতায় এমন প্রকাশ, বলতে গেলে, সেই প্রথম। উঁচু বেদীর উপর সোনার সিংহাসনে বসে তিনি কবিতা লেখেননি। দুঃখী বেদনাতুর হতভাগাদের একজন হয়ে বুভুক্ষ, লাঞ্ছিত দুঃখী মানুষের করুণ গাথা তিনি গেয়ে গেছেন সারা জীবন। ছাদ-পেটানি দরিদ্র নারীর আক্ষেপ তার কবিতায় ‘সারাদিন পিটি কার দালানের ছাত গো/পাত ভরে ভাত পাই না ধরে আসে হাত গো।’ কৃষ্ণনগরের চাঁদসড়কের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে নিয়ে রচিত তাঁর উপন্যাস ’মৃত্যুক্ষুধা’- ‘পুরুষেরা জনমজুর-রাজমিস্ত্রি, খানসামা, . . মেয়েরা ধান ভানে, ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্ম করে. . . ছোট ছেলেমেয়ে - . . ধুলিমলিন, ক্ষুধার্ত, গায়ে জামা নেই . . কাঠ কুড়োয়।’ পুরো উপন্যাসটি সর্বহারা মানুষের দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশার এক মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। সাহিত্যে এর তুলনা বিরল। দুটি সন্তান নিয়ে বিধবা মেজ বউ বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য চরিত্র। সে যেমন অর্থকষ্টে নিপীড়িতা, তেমনি ধর্মীয় গোড়ামির নিগড়ে নিষ্পেষিতা। নিরন্ন সন্তান তার মসজিদে যায় শিরনির আশায়, ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে মৃত্যুর প্রহর গুনে। অন্নের অভাবে মানুষ ধর্ম পর্যন্ত বদলায়। নজরুলের সর্বহারা, সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থ দরিদ্র কৃষক, কুলি-মজুর, জেলেদের দুঃখ দুর্দশার চিত্র। সাপুড়েদের নিয়ে রচনা করেছেন নাটক; গৃহহারা ভাসমান বেদেদের দুঃখ নিয়ে লিখেছেন কবিতা গান। লিখেছেন ভাগ্যহত অশুচিদের কথা; ভিক্ষুকদের কথা - ‘তব প্রাসাদের চারদিকে ভিখারীরা/প্রসাদ মেগেছে ক্ষুধার অন্ন, চায়নি তোমার হীরা।. . . তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়/কাঙালের বেশে কাঁদে তব দরজায়-/ তাড়াও তাদেরে, গাল দিয়ে দরওয়ান,/তুমিও মানুষ, কাঁদে না তোমার প্রাণ?’
নিপীড়িত মানুষের কাছে কোন এক দায়বদ্ধতা স্বীকার করেই সাহিত্য জগতে বিচরণ নজরুলের। তার প্রেম, তার মমতা দরিদ্রদের ঘিরেই - ‘দরিদ্র মোর ব্যথার সঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই;/আমি যেন মোর জীবনে নিত্য কাঙালের প্রেম পাই!/তাহাদের সাথে কাঁদিব, তাদেরে বাঁধিব বক্ষে মম ...।’ এ নেহাৎ কাব্য-বিলাস বা চমক সৃষ্টির দ্বারা জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াস নয়। এ তার সহজাত প্রকৃতি। সমাজের অনাবিল উপরিভাগের অদুরে যে বিস্তৃত দুঃখ-ভার তার গভীর কন্দরে প্রবিষ্ট দৃষ্টি নজরুলের। তাকে দেয়া জাতীয় সংবর্ধনার উত্তরে তিনি বলেন, ‘আমি শুধু সুন্দরের হাতের বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তার চোখে চোখভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধা-দীর্ণ মূর্তিতে ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি।’ ইব্রাহিম খাঁকে তিনি লেখেন, ‘সকল ব্যথিতের ব্যথায়, সকল অসহায়ের অশ্রæজলে আমি আমাকে অনুভব করি, এ আমি একটুও বাড়িয়ে বলছিনে, এই ব্যথিতের অশ্রæজলের মুকুরে যেন আমি আমার প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। কিছু করতে যদি নাই পারি, ওদের সঙ্গে প্রাণ ভরে যেন কাঁদতে পাই!’ কবিতায় লেখেন- ‘ওরা যদি আত্মীয় নহে কেন এ আত্মা কাঁদে আমার?/উহাদের তরে কেন এমন বুকে ওঠে রোদনের জোয়ার?/মুক্তি চাহি না, চাহি না যশ, ভিক্ষার ঝুলি চাহি আমি,/এদের লাগিয়া মাগিব ভিক্ষা দ্বারে দ্বারে কেঁদে দিবাযামী !’
কৈশোরে পৈত্রিক সহায়-সম্পদ পরিহার করে যখন পথে নামলেন তখন দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী। কর্মজীবনের প্রথম প্রহরে নজরুলের জীবন-যাত্রা ছিল, ‘খাবার বেলায় প্রায়ই ভাতে, পোড়া ফ্যান নুন; শোবার বেলায় প্রায়ই ছেড়া কম্বল, ছেঁড়াকাঁথা, শ্মশান ঘাটের মতো বালিশ অথবা কাগজের তাড়ার উপাধান (ধুমকেতু ২৭ জানুয়ারি ১৯২৩ )।’ সংসার জীবনে দারিদ্র্যে জর্জরিত কবি লেখেন ‘পারি নাই বাছা মোর, হে প্রিয় আমার,/দুই বিন্দু দুগ্ধ দিতে। -মোর অধিকার/আনন্দের নাহি নাহি! দারিদ্র্য অসহ/পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ/ আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি?/কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?’ এই আনন্দিত সুন্দরের হাসির অন্বেষণে সংগ্রাম করেছেন তিনি-কখনও সবার সঙ্গে, কখনও একা। কখনও কবিতা-গানে কখনও জনসমাগমে। শ্রমিকদের মাঝে যেয়ে তাদের উৎসাহিত করেছেন, জাগরণী গান শুনিয়েছেন। সারা বাংলার গ্রামে গ্রামে সভা করে কৃষক, তাতী, জেলেদের মাঝে নতুন প্রাণ উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন; গেয়েছেন ‘আজ জাগ রে কিষাণ সবতো গেছে, কিসের বা আর ভয়,/এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।’ অভয় দিয়েছেন, ‘জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,/জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,/জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন/ জাগে মজলুম বদ-নসিব !’
সক্রিয় রাজনীতিতেও তিনি অংশ নেন। তাঁর রাজনৈতিক আদর্শ প্রথাগত রাজনীতি থেকে অবশ্যই পৃথক ছিল। সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন যখন ‘স্বরাজ’ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, তখন স্বরাজের চেয়েও অধিক কিছু চেয়েছেন তিনি, ‘ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন?’ এই ক্ষুধাতুর জনগোষ্ঠীর চাহিদা খুব বেশি নয়- ‘একটি ক্ষুদ্র মৃৎপাত্র/-ভরা অভাব তোর,/ চাইলি রে ঘুম শ্রান্তি-হরা, / একটি ছিন্ন মাদুর ভরা, /একটি প্রদীপ-আলো-করা / একটু কুটির দোর।’ এই একটুখানি চাহিদা পূরণের আকুল আগ্রহে তার নিরলস শ্রম- তার স্বাধীনতার সংগ্রাম। রাজনৈতিক ভৌগোলিক স্বাধীনতা নয়, বরং নিরন্ন বুভুক্ষ মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থানই নজরুল-দর্শনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই তিনি লেবার স্বরাজ পাটি ও কৃষক-শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠাতা-কর্মী হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন। ‘লাঙল’, ‘গণবাণী’ পত্রিকায় শ্রম দিয়েছেন। তার মতে এই দুঃখ-বঞ্চনা অবসানের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে তিনিই পারেন, ‘কোটি কোটি নিরন্ন নিরাশ্রয়ের বেদনায় যার ক্ষুধার অন্ন মুখে উঠবে না, ওই ভিক্ষুকদের সঙ্গে পথে পথে করবেন ভিক্ষা- ওই নিরাশ্রয়দের সঙ্গে গাছতলা হবে যার আশ্রয়- ইট-পাথর হবে যার উপাধান-ছিন্ন কন্থা হবে যার একমাত্র আবরণ সেই পরম বৈরাগীই এই বাংলার-ভারতের-মহাভারত বিশ্বের সেনাপতি-নেতা-লিডার-ইমাম।’ এই খানেই নজরুলের সঙ্গে অন্য অনেকের প্রভেদ। নজরুল চান দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের সংগ্রামে নেতৃত্ব দেবেন দরিদ্র মানুষেরাই। এটা তার অলীক কল্পনা নয়, তার স্বপক্ষে তিনি উদাহরণ দিয়েছেন ইসলামের ইতিহাসের খোলাফায়ে রাশেদীনের। তার গঠিত লেবার স্বরাজ পার্টির সম্পর্কেও তার ধারণা তিনি ব্যক্ত করেছেন, ‘বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল’ . . ধনিক নেতার দ্বারা গঠিত নয় . . বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়-চামড়া বের করা . . . চাষা-মজুর। আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রæপ - না আছে চাল না আছে চুলো।’ কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। সমকালীন বিশ্বে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন বিত্ত-বৈভব সম্পন্ন ধনিক শ্রেণী- ভারতেও তাই।
সাধারণ জনমানুষের যা অবলম্বন, সেই ধর্মের দিকেও তিনি প্রত্যাশার হাত বাড়িয়েছেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্তার কাছে আবেদন জানিয়েছেন, ‘আমরা কাঙাল, আমরা গরিব, ভিক্ষুক, মিসকিন,/ভোগীদের দিন অস্ত হোক, আসুক মোদের দিন। . . .কবুল কর এ প্রার্থনা . . উর্ধ হইতে কে বলে ’আমিন।’ সনাতন ধর্মের ভাষায় মা ল²ীর কাছে করুণ মিনতি করেছেন, ‘পান্তা লবণ পায় না ছেলে . . .কার কাছে মা নালিশ করি . . . অমৃত এনে সন্তানে বাঁচা, মা তোর পায় ধরি।’ দুঃখ থেকেই দ্রোহের জন্ম। প্রতিশোধের আগুনও জ¦লে তার কবিতায়, ‘উপবাস যার দিনের সাধনা নিশীথে শয়নসাথী,/যাহারা বাহিরে গাছতলে থাকে, ঘরে জ্বলে না কো বাতি,/তাদের ধৈর্য সহিষ্ণুতা কি পাবে না পুরস্কার?/তারা তিলে তিলে মরে আনিয়াছে এবার খোদার মার।’
নজরুলের বয়স যখন চল্লিশ বৎসর তখন তাঁর অনুভূতির রাজ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে তিনি লেখেন, ‘রস-প্রমত্ত অশান্ত চলিতেছিলাম রাজপথে,/সম্মুখে এলো ভিখারিণী মৃত ছেলে কোলে কোথা হতে ।/ কহিল, ’বিলাসী! পুত্র মোর, দুধ পায় নাই এক ঝিনুক,/শুকায়ে গিয়াছে অন্নহীন দেখো দেখো এ মায়ের বুক ! / . . কাফন কেনার পয়সা নাই, কি পরায়ে গোরে দিব বাছায়?’ . . রূপ দেখিয়াছি কল্পনায় এঁকেছি স্বপ্ন-গুলবাহার,/দেখিনি শ্রীহীন এই মানুষ জীর্ণ হাড্ডি-চামড়া সার!/নগ্ন ক্ষুধিত ছেলেমেয়ে কাঁদায় কাঁদিয়া মায়ের প্রাণ,/শুনিলাম আমি এই প্রথম শিশুর কাঁদনে আল-কুরআান!/মোর বাণী ছিল রস-লোকের, আল্লার বাণী শুনিনু এই,/বিলাসের নেশা গেল টুটে, জেগে দেখি আর সে আমি নেই . . . এই ক্ষুধিত ও ভিক্ষুকের আজীবন পদসেবা করি’/প্রায়শ্চিত্ত মোর ভোগের পূর্ণ করিয়া যেন মরি !’ (কেন আপনারে হানি হেলা? )। কুরআনের সমুত্থিত বাণী সমন্বয়ে তিনি দাবি জানিয়েছিলেন যে, ‘আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদের কাছে,/ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিসসা আছে।’ (কুরআন ৫১.১৯, ৭০.২৪-৫) । ভয়ও দেখালেন, ‘ভিক্ষা দাও না, রাশি রাশি হীরা মণি/তুলে রাখ আর গোনো। /এ টাকা তোমার রবে না, বন্ধু, জানি,/এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি।’ (সুরা হুমাজা)। আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করেই চাইলেন, ‘পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত বঞ্চিতে। / ধরার সকল মানুষ দুবেলা অন্ন পাইবে পাতে, / নগ্ন শরীরে বস্ত্র পাইবে, অস্ত্র পাইবে হাতে।/বিনা ওষুধ-পথ্য না পেয়ে ছেলেমেয়ে মরিবে না,/শিক্ষা পাইবে, দীক্ষা পাইবে, দাসত্ব করিবে না।/ . ..ধনিকের ঘরে বন্দী রয়েছে আল্লার দেয়া দান/লুটিয়া লইবে সকল মানুষ, বাঁচিবে ক্ষুধিত প্রাণ।/আল্লা সেদিন সকলের হবে, সবাই করুণা পাবে; /. . . এই মোর সাধ, সাধনা আমার, প্রার্থনা নিশিদিন,/মানুষ রবে না অন্নবস্ত্রহীন আর পরাধীন।/আল্লা আমার সহায়- আল্লা পুরাবেন মোর আশ;/গরিব ভাইরা, ভয় নাই, আসে আল্লার আশ্বাস।’ (নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমি নবম খণ্ড পৃ ২১৫)
কে-ই বা শুনেছে এসব কথা? আসেনি আল্লার আশ^াস। ধনীর বিত্ত-বৈভব ফুলে ফেপে উঠেছে। পথে পথে কাঙালের পদযাত্রা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ’য়েছে। ক্ষুধাতুর শিশু আজও কাঁদে। জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র ভিখারীর আর্ত চিৎকার আজও ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়, ‘এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান/মাগে প্রতিকার, উত্তর দাও আদি-পিতা ভগবান।’ (ফরিয়াদ)