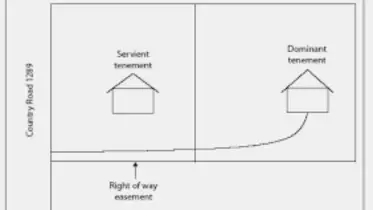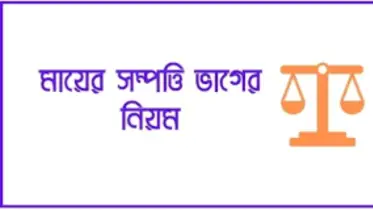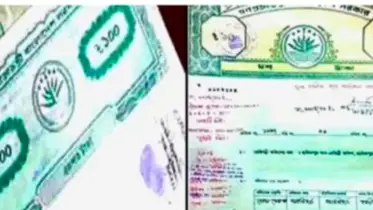ছবি : জনকন্ঠ
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে লঞ্চের একটি কেবিনে সংঘটিত একটি ঘটনা নিয়ে যে আলোচনা চলছে, যেখানে অভিযোগ উঠেছে যে কতিপয় ব্যক্তি কয়েকজন তরুণী ও তাদের সঙ্গীদের প্রতি অনুচিত আচরণ এবং হেনস্থা করেছেন, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আইনের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে এই ঘটনা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত ও চিন্তিত করেছে। এটি কেবল ব্যক্তিগত পরিসরে অনধিকার প্রবেশ ও হয়রানির বিষয় নয়, বরং এর মাধ্যমে প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে পাশ কাটিয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে আইন তুলে নেওয়ার এক বেআইনি প্রবণতা ফুটে উঠেছে, যা 'গণপিটুনি' বা বেআইনি সালিশের সংস্কৃতিরই নামান্তর।
প্রথমত এবং সর্বাগ্রে, বাংলাদেশে গণপিটুনি বা বেআইনি বিচার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তার তদন্ত করা, অপরাধীকে শনাক্ত করা এবং প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেবলমাত্র রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং আদালতের। কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টির আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অর্থ হলো দেশের আইনি কাঠামোকে অস্বীকার করা। অভিযোগ অনুযায়ী এই ঘটনায় যে ধরনের কার্যকলাপের কথা বলা হয়েছে, যেমন কাউকে জোরপূর্বক আটকে রাখা, তা দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (Penal Code, 1860) অনুযায়ী অন্যায় অবরোধ (ধারা ৩৪২) এবং পথ বা গতি রোধ করলে অন্যায় বাধা (ধারা ৩৪১) এর অপরাধ। যদি শারীরিক আঘাত বা বলপ্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তবে তা ফৌজদারি শক্তিপ্রয়োগ (ধারা ৩৫০) বা হামলা (ধারা ৩৫১) এবং ক্ষেত্রবিশেষে গুরুতর আঘাতের অপরাধের আওতায় আসে, যার জন্য দণ্ডবিধিতে কঠোর শাস্তির বিধান রয়েছে। এছাড়াও, ভয়ভীতি প্রদর্শন করা ফৌজদারি ভীতিপ্রদর্শন (ধারা ৫০৩) নামক অপরাধ। যদি পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি বেআইনি উদ্দেশ্য নিয়ে সমবেত হয়ে এই কাজ করে থাকে, তবে সেটি বেআইনি সমাবেশ (ধারা ১৪১) হিসেবে গণ্য এবং বেআইনি সমাবেশের সদস্যরা পরস্পরের কৃত অপরাধের জন্যও দায়ী হতে পারে (ধারা ১৪৯)।
দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যক্তিগত বা নিজস্ব পরিসরে একত্রিত হওয়া কোনো অপরাধ নয়। কারও ব্যক্তিগত জীবন বা সম্পর্ক নিয়ে জনসমক্ষে humiliating করা বা হেয় প্রতিপন্ন করার কোনো আইনি অধিকার কারও নেই। এটি ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকারের পরিপন্থী।
তৃতীয়ত, আইনি প্রক্রিয়ায় কাউকে হেফাজতে নেওয়া বা গ্রেপ্তার করার সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (Code of Criminal Procedure, 1898) এ বিস্তারিত আছে। কেবলমাত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাই আইন অনুযায়ী কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেন। সাধারণ নাগরিকের গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এবং শুধুমাত্র আইনের নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য, সেক্ষেত্রেও আটক ব্যক্তিকে কালবিলম্ব না করে পুলিশের নিকট সোপর্দ করতে হয়। বিশেষত নারী অভিযুক্তদের ক্ষেত্রে গ্রেপ্তার ও দেহ তল্লাশির সময় নারী পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি সংক্রান্ত আইন ও বিধি কঠোরভাবে অনুসরণীয়। কোনো সাধারণ ব্যক্তি বা জনসাধারণের পক্ষে কাউকে আটক বা অবরুদ্ধ করে রাখা সম্পূর্ণ বেআইনি।
এই ঘটনাটি আবারও প্রমাণ করে যে, আইনের শাসনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং প্রতিটি নাগরিকের ব্যক্তিগত অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা কতটা জরুরি। সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আইন অমান্য করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে এবং যে কোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে আইনানুগ পদ্ধতির উপর আস্থা রাখতে হবে। গণপিটুনি বা বেআইনি বিচারের মতো অমানবিক ও বেআইনি কর্মকাণ্ড কোনো সভ্য সমাজের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না।
আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান, এই ধরনের ঘটনাগুলির দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোরতম আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক, যাতে ভবিষ্যতে কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নিজেকে মনে করার স্পর্ধা না দেখায় এবং দেশের সকল নাগরিকের নিরাপত্তা ও সম্মান নিশ্চিত হয়।
আঁখি