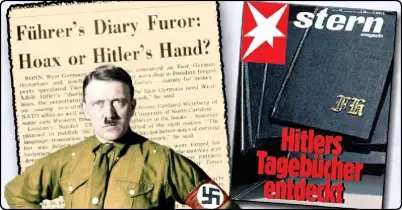১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ ভেঙ্গে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র জন্ম নেয়। পাকিস্তান আবার দুটি অংশে বিভক্ত ছিল, যার একটি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান ও অপরটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বাঙালী (৫৬%), যাদের মাতৃভাষা বাংলা। অপরদিকে পশ্চিমাঞ্চলে ভাষা ছিল সিন্ধি, পশ্তু, বেলুচ, উর্দুসহ আরও কয়েকটি ভাষা। এ অবস্থায় পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নেতৃত্ব সমগ্র পাকিস্তানের আনুমানিক পাঁচ শতাংশের ভাষা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে। ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ অভিমত ব্যক্ত করেন, হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে যেহেতু স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে, উর্দুকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়ার পক্ষে অভিমত দেন। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত ‘পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস’ ১৫ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’ শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন-আদালত ও অফিসাদির ভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর করাচীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করা হয়। পাকিস্তানের তৎকালীন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান, মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহার ও আবদুল হামিদ ওই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এ সংবাদ ৬ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে প্রকাশিত মর্নিং নিউজ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ছাত্রদের প্রতিবাদ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয় বাংলাকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা এবং পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম করা হোক। এটিই রাষ্ট্রভাষার দাবি নিয়ে ছাত্রদের প্রথম সমাবেশ। ওই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন তমদ্দুন মজলিসের সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কাসেম। পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২০ মার্চ রেসকোর্স ময়দান (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এবং ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে উভয় সমাবেশে একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা করেন। এর আগে ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের আইনসভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার দাবি জানানো হয়।
১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এর প্রমাণ। বিশেষ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানীদের গোয়ার্তুমির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটে এবং এদিন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি রুখতে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ। সকল ভয় জয় করে ছাত্ররা নেমে আসে রাজপথে। তখন পুলিশের গুলিতে তৎক্ষণাৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, শফিক, রফিকসহ নাম না জানা অনেকে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষও রাজপথে নেমে আসে। স্বজন হারানোর স্মৃতি অমর করে রাখতে ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহীদদের স্মরণে গড়ে তোলা হয় স্মৃতিস্তম্ভ। ২৬ ফেব্রুয়ারি স্মৃতির মিনার গুঁড়িয়ে দেয় পুলিশ। পঞ্চাশের দশকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই শরিক হয়। গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষাকে অন্যতম দাফতরিক ভাষা করার দাবি তোলেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ জনগণের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ব বাংলার) ৪ কোটি ৪০ লাখ লোকের ভাষা বাংলা। কাজেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের ভাষাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী তীব্র ভাষায় এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয়, মুসলিম লীগের কোন বাঙালী সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে সমর্থন করে কিছু বলেননি। পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনও উর্দুর পক্ষ অবলম্বন করেন। ১১ মার্চ গণপরিষদে প্রস্তাব পাস হয় উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তান গণপরিষদের আচরণ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘...১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ যখন করাচীতে গণপরিষদে এ মর্মে প্রস্তাব পাস করা হলো যে, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, তখন থেকেই বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত। তখন কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একা এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। আমি অবাক হয়ে যাই, ওই সময় আমাদের বাঙালী মুসলিম নেতারা কি করেছিলেন?’ পশ্চিম পাকিস্তানে সংবিধান সভার বৈঠক চলাকালীন পূর্ব বাংলার ছাত্র ও সচেতন মহল বুঝতে পারল যে, বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। গণপরিষদে বাংলা ভাষাবিরোধী সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ঢাকায় ছাত্রসমাজ ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালন করে। বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২ মার্চ ফজলুল হক হলে বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীদের একটি সভা আহ্বান করা হয়। কমরুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ১১ মার্চ পূর্ব বাংলায় ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং দিনটিকে ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ ঘোষণা করা হয়। এ সভাতেই ‘রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ’কে সর্বদলীয় রূপ দেয়া হয়। ১১ মার্চের কর্মসূচী সফল করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতারা জেলায় জেলায় সফরে বেরিয়ে পড়েন। তৎকালীন ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমান ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করেন। ১১ মার্চ ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ উপলক্ষে পূর্ব বাংলায় পালিত হয় সাধারণ ধর্মঘট। ওইদিন ভোরে শত শত ছাত্র ইডেন বিল্ডিং, জিপিও ও অন্যান্য জায়গায় পিকেটিং শুরু করে। পুরো ঢাকা শহর পোস্টারে ছেয়ে যায়। ছাত্রদের আন্দোলনে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। নানা জায়গায় অনেক ছাত্র আহত হয়। শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদসহ ৭০-৭৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। স্বাধীন পাকিস্তানে এটিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম গ্রেফতার।
তখন পূর্ব পাকিস্তান আইনসভার অধিবেশন চলছিল। এ সময় শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, তোফাজ্জল আলী, ডাঃ মালেক, খান এ সবুর, খয়রাত হোসেন, আনোয়ারা খাতুন এবং আরও অনেক সদস্য ছাত্রদের পুলিশ কর্তৃক মারধর ও জেলে পাঠানোর প্রতিবাদ করেন। নাজিমুদ্দিন সাহেব ঘাবড়ে গেলেন এবং সংগ্রাম পরিষদের সঙ্গে আলাপ করতে রাজি হলেন। ১১ মার্চের আন্দোলন ও ধর্মঘটের প্রস্তুতির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্য নেতারা আগেই ঢাকায় চলে আসেন। ১০ মার্চ রাতে ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক সভা হয়। সভায় কয়েকজন বক্তার আপোসকামী মনোভাব দেখে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ‘সরকার কি আপোস প্রস্তাব দিয়েছে? নাজিমুদ্দিন সরকার কি বাংলা ভাষার দাবি মেনে নিয়েছে? যদি তা না হয়ে থাকে তবে আগামীকাল ধর্মঘট হবে, সেক্রেটারিয়েটের সামনে পিকেটিং হবে।’ শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন করেন অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, মোগলটুলীর শওকত আলি ও শামসুল হক। অলি আহাদ তার ‘জাতীয় রাজনীতি-’৪৫ থেকে ’৭৫ গ্রন্থে’ উল্লেখ করেন, ‘সেদিন (১০ মার্চ) সন্ধ্যায় যদি মুজিবুর রহমান ভাই ঢাকায় না পৌঁছতেন তাহলে ১১ মার্চের হরতাল, পিকেটিং কিছুই হতো না।’ ১৯৪৮-এ সূচিত ছাত্র-জনতার আন্দোলন ’৫২তে বেগবান হয়ে ওঠে। একুশে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পর তা পরিণত হয় গণঅভ্যুত্থানে। পাকিস্তান সরকার বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। সেইসঙ্গে রাজপথের সংগ্রামও নতুন মাত্রায় উন্নীত হয়। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আবহমানকালের বাংলা জেগে ওঠে।
১৯৫২ থেকে ১৯৭১ এই ১৯টি বছর দেশের মানুষ কাটিয়েছে অনেক সংগ্রামের মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে। এর সফল বাস্তবায়ন হয় ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয়, যা জাতির ইতিহাসে এক অনন্য অধ্যায় হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে পৃষ্ঠা ৯২-এ লিখেছেন- ‘সভায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চকে ‘বাংলা ভাষা দাবি দিবস’ ঘোষণা করা হলো। জেলায় জেলায় আমরা বের হয়ে পড়লাম। আমি ফরিদপুর, যশোর হয়ে দৌলতপুর, খুলনা ও বরিশালে ছাত্রসভা করে ওই তারিখের তিনদিন পূর্বে ঢাকায় ফিরে এলাম।’
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সেই ১৯৫২ সালেই বাংলাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিয়ে যান। ওই বছর তিনি চীনের পিকিংয়ে (২-১২ অক্টোবর) অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতা করেন। কেন তিনি চীনের বিশ্বশান্তি সম্মেলনে বাংলায় ভাষণ দেন তার উল্লেখ রয়েছে ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’তে (পৃষ্ঠা ২২৮)। তিনি বলেছেন, ‘পূর্ব বাংলার ছাত্ররা জীবন দিয়েছে মাতৃভাষার জন্য। বাংলা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু লোকের ভাষা। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকে না জানে এমন শিক্ষিত লোক চীন কেন দুনিয়ার অন্যান্য দেশেও আমি খুব কম দেখেছি। আমি ইংরেজীতে কথা বলতে পারি। তবু মাতৃভাষায় কথা বলা আমার কর্তব্য।’ এরপর স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় বক্তৃতা করেন তিনি। বাংলায় বক্তৃতা করে বঙ্গবন্ধু শুধু বাংলা ভাষাকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে পরিচয় করানো নয়, বাঙালীর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বার্তাও পৌঁছে দেন। বর্তমান বিশ্বে ৭০০ কোটি মানুষ ৬০০০ ভাষায় কথা বলে। বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বুকের রক্ত দিয়ে গেছেন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরও অনেকে, যাদের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি বাংলা ভাষা। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত এই ভাষা। ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি দেয়। ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্রে প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে, যা বাংলার বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় এটি একটি বড় ধাপ। আমাদের বড় পরিচয় আমরা বাঙালী, আমাদের ভাষা বাংলা। আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্যচিন্তা ও বোধ এক। বাঙালী হিসেবে অহঙ্কার করার মতো আমাদের রয়েছে হাজার বছরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। আজ আমাদের গর্বিত পরিচয়- মাতৃভাষার জন্য আমরা রক্ত দিয়েছি বিধায় আমরা একুশের উত্তরাধিকার। কিন্তু এত আত্মত্যাগ পরিপুষ্ট সেই ভাষা আজ কতটা টেকসই? শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের অনেক দেশেই মাতৃভাষা ভুলে যাওয়া মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। কাজেই আমাদের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার বিচার-বিশ্লেষণের এটাই আসল সময়। কারণ ১৯৫২ থেকে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি- এই ৭ দশকের পথপরিক্রমায় জাতি কি পেয়েছে? জাতি পেয়েছে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র, একটি ভাষা, ভাষা নিয়ে গর্বের অধিকার, আত্মোপলব্ধির সুযোগ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি, শহীদ মিনার তৈরির সুযোগ, সংস্কৃতি বিকাশের সুযোগ- কি গানে, কি কবিতায়, কি নাটকে, কি চলচ্চিত্রে, কি একুশের বইমেলায়, একুশেকেন্দ্রিক ব্যবসা-বাণিজ্য, যেমন- ফুল, মুদ্রণ শিল্প, বইমেলা, চিত্রকর, নির্মাণ শিল্পী, কলাকুশলী ইত্যাদি। ভাষা আন্দোলনই স্বাধীন বাংলাদেশকে জন্ম দিয়েছে মূলত দুটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে- প্রথমত রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ও দ্বিতীয়ত সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার চাই। প্রথমটি অর্জিত হলেও দ্বিতীয়টি অনেকাংশে অপূর্ণ রয়ে গেছে, যা অনেকটা আশঙ্কার বলে প্রতীয়মান হয়। ১৯৮৭ সালে দেশে আইন করা হয় যে, সর্বস্তরে বাংলা ভাষা ব্যবহার ও প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু তা মানা হচ্ছে কম। আমরা এ ব্যাপারে কতটা কি করতে পেরেছি? আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বটে, কিন্তু সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নেই কেন? এই ব্যর্থতার দায় সবার। কথা ছিল শিক্ষাব্যবস্থা হবে একমুখী, কিন্তু তাও হলো না। আমরা রাষ্ট্র বদল করলাম, কিন্তু সমাজ বিনির্মাণ করতে পারলাম না। যার জন্য প্রয়োজন বৈষম্য দূরীকরণে একমুখী শিক্ষাব্যস্থা নিশ্চিত করা। একুশের শিক্ষা হলো সমষ্টির পক্ষে কোন বিজয়ই অসম্ভব নয়। স্বাধীন বাংলাদেশেও জোটবদ্ধ আন্দোলনের সুফলের নজির রয়েছে। আমরা যেন বায়ান্ন ও একাত্তরের অঙ্গীকার ভুলে না যাই।
২১ ফেব্রুয়ারি স্মরণে আমাদের নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের অন্যতম অনুষঙ্গ অমর একুশে গ্রন্থমেলা, ব্যাপকভাবে যে মেলাটি একুশের বইমেলা হিসেবে পরিচিত। বর্তমান বিশ্বে অন্যতম উপায় হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে মাতৃভাষাকে টেকসই করতে প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের অবস্থানটা কি তা আলোচনার দাবি রাখে অবশ্যই। ভাষাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ভাষাবিদদের পাশাপাশি রাষ্ট্র এবং প্রযুক্তিবিদদেরও সক্রিয় হতে হয়। মায়ের ভাষায় প্রযুক্তি ব্যবহার করেই দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের ইতিবাচক দিক হচ্ছে প্রযুক্তিমনস্ক সরকার ক্ষমতায়। প্রযুক্তির ব্যবহার করে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া ও চর্চা এবং ভাষাকে টেকসই করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চিন্তা এবং তার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উপদেষ্টার বিশেষজ্ঞ জ্ঞান থেকে উৎসারিত সরকারী কিছু উদ্যোগ দেশকে আশাবাদী করছে। প্রধানমন্ত্রী এক দরজা থেকে সেবা প্রদানের প্লাটফর্মের (জেলা তথ্যবাতায়ন) নাম বাংলায় রাখেন। এরই ধারাবাহিকতায় সর্ববৃহৎ প্লাটফর্মটিরও নাম রাখা হয় ‘জাতীয় তথ্যবাতায়ন’। এতে রয়েছে ৫২ হাজার ওয়েবসাইট, যা বাংলা ও ইংরেজীতে। ২০১২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী মোবাইল ফোনে বাংলায় খুদেবার্তা (এসএমএস) চালুর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অন্তর্ভূুক্তিমূলক সমাজ বিনির্মাণের ধারণাকে সামনে রেখে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তবে বাংলাদেশে প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার চর্চা হলেও এ মুহূর্তে বাংলায় ভাল কনটেন্টের অভাব রয়েছে। তাই দেশের ১৭ কোটির বেশি মোবাইল ফোন, ১৩ কোটিরও বেশি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং ৫ কোটির বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীর কথা মাথায় রেখে মাতৃভাষায় ভাল ভাল কনটেন্ট ও মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে হবে। আর তা করা হলে শুধু অর্থনৈতিক কার্যক্রম, মানুষে মানুষে যোগাযোগ বৃদ্ধি, জ্ঞানার্জন এবং তথ্য ও সেবা পাওয়া নিশ্চিত করবে না, মাতৃভাষাকে বাঙালীর মাঝে চিরঞ্জীব করতেও সহায়তা করবে।
কিন্তু সমস্যাটা হলো এক- মাতৃভাষার মাধ্যমে সব স্তরে এবং সব জনপদে শিক্ষাকে যদি কার্যকরভাবে জনপ্রিয় করা না যায় তাহলে শিক্ষার হার বৃদ্ধি এবং এর প্রাসঙ্গিক উন্নয়ন নিয়ামকগুলোর তুলনামূলক প্রবৃদ্ধি কোনভাবেই সম্ভব নয়; দুই- বর্তমান সরকার সম্পদের সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও জাতি গঠন, শিক্ষার মাধ্যম, আধুনিক জ্ঞান ও শক্তিতে বলীয়ান করাসহ বহু উদ্দেশ্য সামনে রেখে শিক্ষার উন্নয়নে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার পর থেকে শিক্ষা সংস্কারের নামে নানা কমিশন জাতির সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার যে ভিত বিশেষত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তা খুবই দুর্বল। যেমন- ভাষা কি? তা হলো মনের ভাব প্রকাশের প্রধান মাধ্যম, তা আমাদের কোমলমতি শিশুদের বোঝানোর মতো শিক্ষক তেমন নেই। এই দুর্বলতা নিয়ে যখন এই শিশুরা বড় হয়ে উচ্চপর্যায়ে যায় তখন ভাষার প্রতি যে জাতীয়তাবোধ তা আর সৃষ্টি হয় না, যা একটি বড় দুর্বলতা বলে প্রতীয়মান; তিন- আকাশ সংস্কৃতির কারণে অনেক ক্ষেত্রেই ইংরেজীর ব্যবহার বাংলা ভাষার মর্যাদা নষ্ট করে দিচ্ছে। বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে তা মোটেও সুখকর নয়। এখনও দেশের বিজ্ঞজনদের অনেকেই সভা-সমিতিতে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করেন। তাদের কথা যে সবাই বুঝতে পারছে না সেটা জেনেও তারা তা করেন। এর মাধ্যমে আমাদের চেতনার মধ্যে ঔপনিবেশিক মানসিকতার ছাপ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়; চার- বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণের কাজ এবং মৌলিক জ্ঞানসম্পন্ন সার্ভিস তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্স, আইওটির মতো প্রাগ্রসরমান (ফ্রন্টিয়ার) প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে। কিন্তু আমাদের ভিত্তিতে যে গলদ রয়ে গেছে তা দিয়ে বাংলা ভাষা অনুশীলনকারীদের কতটুকু ফলপ্রসূ হবে তা গবেষণার বিষয়; পাঁচ- বাংলায় কথা বলা আর শুদ্ধ বাংলা ভাষা চর্চা এক বিষয় নয়। এই বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের দৃষ্টি খুব সীমিত। ব্যাপারটা এরকম যে, একটি বাচ্চাকে শুদ্ধ ভাষা না শিখিয়ে তার হাতে বাবা-মা স্মার্টফোন ধরিয়ে দেন, যা ভয়ঙ্কর হতে বাধ্য। এমনকি বিশ্বায়নের কারণে বাংলা ভাষা কি অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি প্রতিযোগিতায় স্থান করে নিতে পারছে? দেশের রাস্তায় বিলবোর্ডগুলোতে অশুদ্ধ বাংলার পাশাপাশি রুচিবিবর্জিত ছবিগুলো আমাদের অসুস্থতারই লক্ষণ বলে প্রতীয়মান হয়। দেশের ১০৫টি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও বিষয় হিসেবে বাংলা চালু হয়নি। একুশের চিন্তা-চেতনা মানেই দেশকে ভালবাসার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের অঙ্গীকার, যা পূরণ হয়নি। গবেষণায় বাংলাভাষার ব্যবহার সীমিত হয়ে আছে। বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়নি, যা ছিল প্রত্যাশিত। মহান শহীদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দেয়া বাণীতে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেছেন, ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালীর মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। কালের আবর্তে পৃথিবীতে অনেক ভাষাই আজ বিপন্ন। একটা ভাষার বিলুপ্তি মানে একটা সংস্কৃতির বিলোপ, জাতিসত্তার বিলোপ, সভ্যতার অপমৃত্যু। তাই মাতৃভাষা ও নিজস্ব সংস্কৃতির বিকাশসহ সকল জাতিগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় বিশ্ববাসীকে সোচ্চার হওয়ারও তাগিদ জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রীও বলেছেন, ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল এবং এর সফল বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্যের প্রয়োজন।
লেখক : গবেষক, ডিন ও সিন্ডিকেট সদস্য,
সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা