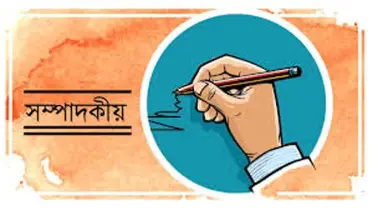বিদেশি ঋণের ওপর ভর করে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ বিলিয়ন ডলারের ঘর অতিক্রম করেছে, যা আপাতদৃষ্টিতে অর্থনীতির জন্য একটি স্বস্তির খবর। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে প্রাপ্ত ঋণ এবং শক্তিশালী রেমিটেন্স প্রবাহ এই বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ২৬ জুন ২০২৫ তারিখে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বাংলাদেশ ব্যাংক ও আইএমএফের বিপিএম৬ হিসাব অনুযায়ী যথাক্রমে ৩০.৫১ বিলিয়ন ও ২৫.৫১ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে, যা গত মাসের তুলনায় প্রায় ৫ বিলিয়ন ডলার বেশি। চলতি মাসের প্রথম ২১ দিনে প্রবাসীরা প্রায় ১.৯৯ বিলিয়ন ডলার দেশে পাঠিয়েছেন এবং আশা করা হচ্ছে, এই মাসে মোট রেমিটেন্সের পরিমাণ ৩.০ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করবে, যা দেশের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ হবে। এই রিজার্ভ বৃদ্ধি বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে একটি ইতিবাচক ইঙ্গিত এবং মুদ্রাবাজার স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক হতে পারে। এটি দেশের বৈদেশিক খাতের, বিশেষ করে পেমেন্ট ব্যালান্সের দ্রুত পুনরুদ্ধারের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে এই রিজার্ভ বৃদ্ধি মূলত ঋণ সহায়তার ওপর নির্ভরশীল, যা অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ কাঠামোগত দুর্বলতা, বিশেষ করে ভোক্তা ব্যয় এবং বিনিয়োগের সংকটকে আড়াল করছে। তাই শুধু রিজার্ভের পরিমাণ দিয়ে অর্থনীতির সামগ্রিক স্বাস্থ্য বিচার করা যুক্তিযুক্ত নয়। স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, অর্থায়নের প্রবাহ সচলকরণ, ভোক্তা আস্থা পুনর্গঠন এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য কার্যকর সহায়তা কাঠামো গড়ে তোলা। অন্যথায়, সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক দুর্বলতা রিজার্ভ বৃদ্ধির এই সুযোগকে টেকসই প্রবৃদ্ধিতে রূপান্তর করতে ব্যর্থ হবে।
দীর্ঘদিন ধরে ৯ শতাংশের ওপরে থাকা উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা মারাত্মকভাবে হ্রাস করেছে, যার ফলে পরিবারগুলো খাদ্যবহির্ভূত এবং জরুরি নয় এমন পণ্যের ব্যয় কমাতে বাধ্য হচ্ছে। এর সরাসরি প্রভাবে খুচরা বিক্রি, পোশাক, ফার্নিচার, রিকন্ডিশন্ড গাড়ি এবং হোটেল-রেস্তোরাঁর মতো খাতগুলোতে তীব্র মন্দা দেখা দিয়েছে। এ বছর দুই ঈদকেন্দ্রিক বাণিজ্যও প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম ছিল, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাসের ভয়াবহতাকে স্পষ্ট করে। প্রাণ-আরএফএলের মতো বড় এফএমসিজি কোম্পানিগুলোও বিক্রিতে পতন লক্ষ্য করেছে, যেখানে ভোক্তারা বড় প্যাকের বদলে ছোট প্যাক বা কমদামি পণ্য কিনছেন- এটি অর্থনৈতিক চাপের একটি সুস্পষ্ট লক্ষণ। দেশের অর্থনীতিতে ২৫ শতাংশ অবদান এবং মোট কর্মসংস্থানের ৪০ শতাংশ সৃষ্টিকারী অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমইএস) খাত প্রায় ২.৮ বিলিয়ন ডলারের অর্থায়ন ঘাটতিতে ভুগছে। যখন উচ্চ খেলাপি ঋণের কারণে ব্যাংকগুলো নতুন ঋণ দিতে পারছে না, তখন কর্মসংস্থানের সবচেয়ে বড় এই খাতটি পুঁজির অভাবে বিকশিত হতে পারছে না। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারকে বাধাগ্রস্ত করছে, তেমনি সামাজিক ন্যায়বিচার ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যকেও ব্যাহত করছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা কমে যাওয়ায় শিল্প-কারখানাগুলো তাদের উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, নির্মাণ খাতের স্থবিরতার কারণে স্টিল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের উৎপাদন প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স (এমসিসিআই) এবং পলিসি এক্সচেঞ্জ অব বাংলাদেশের (পিইবি) পারচেজিং ম্যানেজার্স ইনডেক্স (পিএমআই) অনুযায়ী, অর্থনীতিতে নতুন ব্যবসা এবং কর্মসংস্থান সূচক পুনরায় সংকুচিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক গতিকে সীমিত করার ইঙ্গিত দেয়। বিনিয়োগকারীরা নতুন বিনিয়োগে আস্থা পাচ্ছেন না। ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ৪ লাখ ২০ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের ২৪ শতাংশেরও বেশি। এই বিপুল পরিমাণ খেলাপি ঋণ ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানের সক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে এবং একটি তীব্র তারল্য সংকট তৈরি করেছে। এর ফলে বেসরকারি খাত, বিশেষ করে উৎপাদনশীল খাতের উদ্যোক্তারা প্রয়োজনীয় ঋণ পাচ্ছেন না, যা বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানকে আরও সংকুচিত করছে। অন্যদিকে সরকারের ব্যাংক-নির্ভরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারি খাতের জন্য ঋণের সুযোগ আরও কমে যাওয়ার এবং সুদের হার চড়া থাকার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আবার টাকার মান কমে যাওয়ায় বিদেশি ঋণের সুদের পেছনে অর্থব্যয়ও বাড়ছে।
বিশ্বব্যাংক জানিয়েছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে এসেও বাংলাদেশে সামগ্রিক অর্থনীতির স্থিতিশীলতা ফেরেনি; বরং অর্থনৈতিক সংকট আরও গভীর হয়েছে। রাজস্ব ঘাটতি ১ লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে এবং সরকার সংকট সামাল দিতে ব্যাংক খাত থেকে প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও বেশি ঋণ গ্রহণ করেছে। বিদেশি ঋণের বোঝাও বেড়েছে, যার ফলে ঋণ পরিশোধের দায় বাড়ছে এবং অর্থনীতিতে বাড়তি চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও এর মূল কারণ হলো পুঁজি যন্ত্রাংশ আমদানির ব্যাপক হ্রাস। এই মন্দা পরিস্থিতি দেশীয় ও বিদেশি উভয় বিনিয়োগেই প্রভাব ফেলেছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ছে কর্মসংস্থানের ওপর। চলতি অর্থবছরের শেষে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৩ দশমিক ৫ শতাংশের নিচে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সংকট আরও তীব্র হতে পারে। চলমান ইরান-ইসরাইল সংঘাতের অভিঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকর প্রভাব বয়ে এনেছে। বিশ^ায়নের এই যুগে বিশে^র যে কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ-সংঘাত-অস্থিরতা সব দেশের ওপরই কমবেশি নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এসব কারণে অর্থনীতিবিদদের পাশাপাশি অন্তর্বর্তী সরকারও ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য বেশকিছু বড় চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করেছে এবং সেগুলোকে ২০২৫-২৬ সালের প্রস্তাবিত বাজেটে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে যেমন মন্দাবস্থার কারণে ধীরগতির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা, মূল্যস্ফীতির লাগাম টানা, খাদ্য ও জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দক্ষ জনশক্তি ও কর্মসংস্থান তৈরি, সামাজিক সুরক্ষা জোরদার, রাজস্ব আয় বাড়ানো, ব্যবসা ও বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরি, স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের প্রস্তুতি এবং শিল্প উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ। এই বহুমুখী চ্যালেঞ্জ নিয়েই সরকার ২০২৫-২৬ অর্থবছর শুরু করতে যাচ্ছে, যেখানে অর্থনৈতিক চাপ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। চলমান মন্দাবস্থার প্রভাব রাজস্ব আহরণে ইতোমধ্যেই পড়তে শুরু করেছে, যার ফলে বাজেট বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে উঠছে।
অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক উত্তেজনা তেলের দামকে ১০০ ডলারের ওপরে ঠেলেনি ঠিকই, তবে গত এক মাসে তা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এই মূল্যবৃদ্ধি অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদভিত্তিক পণ্যের দাম, বিশেষ করে অ্যালুমিনিয়ামের মতো ধাতুর দামও বাড়িয়েছে। তেলবাহী ট্যাংকার পরিবহনের ভাড়াও বাড়ছে। এর ফলস্বরূপ ব্যবসাগুলোর জন্য ব্যয় বেড়েছে, যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে। বিশ^ব্যাপী অর্থনীতিবিদ-গবেষক থেকে শুরু করে সাম্রাজবাদী ব্যবস্থার দোসর বিশ^ব্যাংক-আইএমএফ-এডিবি-আইডিবি সবাই বলছে, বৈশ্বিক অর্থনীতি গতি হারাচ্ছে-বিশ্বব্যাংক ২০২৫ সালে বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধি ২ দশমিক ৩ শতাংশে নেমে আসার পূর্বাভাস দিয়েছে, যা পূর্বের পূর্বাভাসের চেয়ে প্রায় অর্ধ শতাংশ পয়েন্ট কম। কিন্তু বাস্তবে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে, যার অন্যতম কারণ সম্প্রতি সমাপ্ত ন্যাটো শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য দেশগুলো তাদের সক্ষমতা বাড়াতে সামরিক জিডিপির ৫ শতাংশ সামরিক খাতে ব্যয় করতে সম্মত হয়েছে, যার প্রভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলোয় মুদ্রাস্ফীতির আশঙ্কা তীব্রতর হয়েছে। আবার যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কের জবাবে চীনও তার অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করছে। ফলে তেল, ধাতু এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের চাহিদা শেষ পর্যন্ত অনেক বেশি শক্তিশালী হচ্ছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতির নতুন ঢেউয়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত। অথচ আমাদের রাজনীতিবিদ-আমলা-ব্যবসায়ীদের দুষ্টচক্র দেশের অর্থনীতিকে চরম ক্ষতিগ্রস্ত করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা ও উদ্ধারে মরিয়া চেষ্টারত। তেলের দাম প্রতি ১০ ডলার বাড়লে ইউরোজোনে মুদ্রাস্ফীতি শূন্য দশমিক ৪ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে এবং বছরের শেষ নাগাদ জিডিপি প্রবৃদ্ধি থেকে ০.২৫ শতাংশ কমে যাবে, যার প্রভাব নিশ্চিতভাবেই বাংলাদেশকে আরও সংকটে ফেলবে। বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে, অক্সফোর্ড ইকোনমিকস তুলনামূলকভাবে নরম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছে-তাদের মতে, ব্রেন্ট যদি ব্যারেলপ্রতি ৭৫ ডলারে স্থির থাকে, তাহলে মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যাশার চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। যেখানে পরিবহন ব্যয়ের কথা, যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিসার্চের (এনআইইএসআর) মতে, শিপিং ব্যয়ে ১০ পয়েন্ট বৃদ্ধিতে ওইসিডি অর্থনীতিগুলোতে প্রায় শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ মুদ্রাস্ফীতি যুক্ত হতে পারে। ভালো খবর হলো, আপাতত ব্যয় এখনো গত বছরের সর্বোচ্চ সীমার নিচে রয়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে তেল ও ধাতুর পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধিই বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ, যা তাদের আরও কঠোর অবস্থানে যেতে বাধ্য করতে পারে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে অস্থিরতা বৈশ্বিক অর্থনীতির জন্য মোটেও ভালো সংবাদ নয়- এ কারণেই বাজারে প্রাথমিক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে। আশা করা যায়, পরিস্থিতি দ্রুত স্থিতিশীল হবে এবং সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি- যেমন হরমুজ প্রণালি বন্ধ হওয়া-এড়িয়ে চলা যাবে। একটি আশাব্যঞ্জক ইঙ্গিত হলো, সোমবারে তেলের দামে ব্যাপক পতন, যা মুদ্রাস্ফীতিজনিত ভয়ের কিছুটা প্রশমন করতে পারে।
সামষ্টিক অর্থনীতির সংকট মোকাবিলায় বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবাই বাংলাদেশের জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে : রাজস্ব আহরণে সংস্কার ও সম্প্রসারণ, রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্যকরণ, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিগুলোর দক্ষতা ও লক্ষ্যভিত্তিকতা উন্নয়ন, অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ। এসব পদক্ষেপ দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে অর্থনীতির ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে। নতুন বাজেটে এসব অগ্রাধিকারের কিছু ইতোমধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে, বিশেষ করে রাজস্ব সংস্কার ও কর আহরণে জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে অতিরিক্ত ১০ হাজার কোটি টাকার বরাদ্দও প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে এখনো কার্যকর কোনো উদ্যোগ দেখা যায়নি। বাংলাদেশের বর্তমান সংকটের পেছনে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক উভয় প্রভাবই রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, বৈদেশিক বাণিজ্য হ্রাস, আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং ঋণ পরিশোধের চাপ। যদিও বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছে, তবে জনজীবনে এর প্রভাব এখনো পুরোপুরি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। মূল্যস্ফীতির চাপ কমতে শুরু করলেও, তা এখনো মানুষের সহ্যসীমার মধ্যে আসেনি। একই সঙ্গে আগামী জুনের মধ্যে ৬.৫ শতাংশে মূল্যস্ফীতি নামিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনের মতো পরিবেশও সৃৃষ্টি হয়নি। রাজস্ব খাতে সংস্কার ও কর আহরণে অগ্রগতি হলে সামষ্টিক অর্থনীতির সংকট দূর করা সহজ হতো। কিন্তু দুর্নীতির সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত রাজস্ব খাত সংকট দূর করার মতো যোগ্যতা দেখাতে পারেনি। উল্টো অন্যায়ভাবে অর্থনীতির জন্য চাপ সৃষ্টি করছে আমলাতান্ত্রিক লোভ-লালসা পূরণ যুক্তি ও কর্মসূচি দিয়ে। অথচ বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের মূল চালিকাশক্তি তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত প্রচণ্ড চাপে আছে ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় অর্থনৈতিক মন্দার কারণে। এসব অঞ্চলের ক্রেতাদের চাহিদা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে, যার ফলে রপ্তানি আয় কমেছে এবং সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে আয়ও হ্রাস পেয়েছে। এটি ভবিষ্যতে খাতটির জটিলতা আরও বাড়াবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অধিকন্তু বাংলাদেশ অচিরেই স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণ করতে যাচ্ছে, যা রপ্তানিযোগ্য পণ্যে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা হারানোর ঝুঁকি তৈরি করবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এখনই প্রস্তুতি হওয়া দরকার। কিন্তু পুঁজিবাদী দুর্বৃত্ত মানসিকতা ও লোভ-লালসায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত পরজীবী গোষ্ঠী অর্থনীতির সামনে একের পর এক চ্যালেঞ্জ খাড়া করছে।
এমন এক অনিশ্চিত প্রেক্ষাপটে রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য আত্মতৃপ্ত না থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা স্থিতিশীল ও নিরবচ্ছিন্ন রাখা জরুরি। সিন্ডিকেট ও বাজার কারসাজি রোধে কার্যকর মনিটরিং এবং আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে খাদ্য মূল্যস্ফীতিকে সহনীয়পর্যায়ে নামিয়ে আনা অপরিহার্য। ব্যাংকিং খাতে জরুরি সংস্কার এবং খেলাপি ঋণ আদায়ে রাজনৈতিক সদিচ্ছাসহ একটি স্বাধীন ও ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করা প্রয়োজন। ইচ্ছাকৃত ঋণখেলাপিদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করে ঋণ বিতরণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমএসএমই খাতের জন্য বিশেষায়িত অর্থায়ন প্যাকেজ হিসেবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিশেষ তহবিল গঠন করা উচিত। অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগ ও চাহিদা বৃদ্ধিতে সরকারকে উন্নয়ন ব্যয় ও প্রকল্পগুলোতে দেশীয় নির্মাণসামগ্রী ও শিল্পের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত। কৃষি ও উৎপাদনশীল খাতে সরাসরি প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষি উৎপাদনে (যেমন: সার, বীজ, জ্বালানি) ভর্তুকি প্রদান করা উচিত। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন কৃষকের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে, তেমনি বাজারে পণ্যের সরবরাহ বাড়বে, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক হবে। একইসঙ্গে কর ও নীতির স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে বেসরকারি ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন, যা নতুন শিল্প স্থাপন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করবে। তবে সবার আগে সরকারের ব্যাংক খাত থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়ার পরিবর্তে করের আওতা বাড়ানো এবং রাজস্ব আদায়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা জরুরি। প্রয়োজনে রাজস্ব খাতের দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ছাঁটাই করে রাজস্ব বিভাগকে কঠোর বার্তা দিতে হবে। কারণ ৫৪ বছর ধরে দেশের প্রাপ্য রাজস্বের সিংহভাগই এই গোষ্ঠীর সহায়তায় ধনিক শ্রেণির করায়ত্ত হয়েছে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল