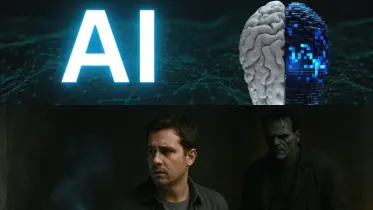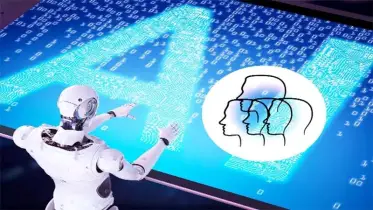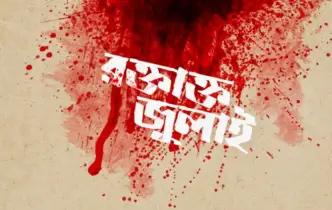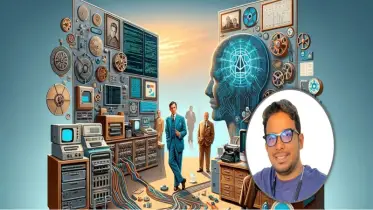প্যালিওলিথিক যুগে মানুষ প্রথম ছবি এঁকেছিল সে কথা ইতিহাস বলে। তার আগে, আজ থেকে প্রায় ত্রিশ হাজার বছর আগের মানুষেরা গুহাচিত্র কেন এঁকেছিল কে জানে। হতে পারে তা নিজেকে প্রকাশের তাগিদ থেকে। হতে পারে প্রকৃতির বিশালতার কাছে নিজের ক্ষুদ্রতার উপলব্ধি থেকে। বিশালতার প্রতিচিত্র এঁকে তাতে নিজেকে সমর্পণ, এতেই হয়ত শান্তি মিলত তাদের।
ওই চিত্রই কি ক্রমে রূপ পেয়েছে মূর্তিতে? নিজের সন্তানদের নিয়ে দেবী দুর্গার যে রূপ তা যেন প্রাচীন সেই জীবনের বাস্তবতাকেই মনে পড়িয়ে দেয়। আদিম যূথবদ্ধ সমাজে মায়েরই অন্যরূপ যেন। বনের ফলমূল সংগ্রহ থেকে পশু শিকার করে জীবন ধারণ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ে মা-ই আগলে রাখতেন পুরো পরিবার। তার নেতৃত্বে চলত সে সময়ের ছোট পরিসরের সমাজ। সমাজ বলতে পরিবারই আসল। একজন মা ও তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ছিল এর বিস্তৃৃতি। ‘সবার আগে রয়েছে একজন স্ত্রীলোক, বলিষ্ঠ তার দেহ। বয়স চল্লিশ পঞ্চাশের মধ্যে। তার নগ্ন বাহুর দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে খুব বলবতী। বাঁ হাতে একটি ছুঁচলো তিন হাত লম্বা ভূর্জ গাছের মোটা কাঠ। ডান হাতে কাঠের হাতলে দড়ি দিয়ে বাঁধা পাথরের কুঠার, শিকারের জন্য ঘষে ঘষে শান দেয়া হয়েছে, তার পেছনে রয়েছে চারজন পুরুষ ও দু’জন স্ত্রীলোক। হাতে কাঠ, হাড় ও পাথরের অস্ত্রাদি এবং তাদের অভিযান দেখে মনে হয়, তারা যেন যুদ্ধে যাচ্ছে। ...পাহাড় থেকে নামার পথে প্রথম স্ত্রী লোকটি হচ্ছে মা। সে বাঁ দিকে ঘুরল, আর সকলে তাকে নীরবে অনুসরণ করল।’ ছ’ হাজার খ্রিস্টপূর্ব সময়ের সমাজচিত্র এভাবেই তুলে ধরেছেন রাহুল সাস্কৃৃত্যায়ন তাঁর ‘ভোল্গা থেকে গঙ্গা’য়।
ওই মা আর্য। দুর্গা ও তার সন্তানদের যে রূপ তাও আর্যেরই। কোল ভিল সাঁওতালদের দেশে আর্য মায়ের এত প্রভাব কি করে হলো সে এক রহস্য। সে কি সুদূর অতীতের উৎসকে জাগ্রত রাখার জন্য? যদিও ধর্মীয় ব্যাখ্যা অন্য রকম এবং বাংলা অঞ্চল ছাড়া দুর্গা অন্য কোথাও এত আড়ম্বরে পূজিত হন না। ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চলে মূল উৎসব দুর্গাপূজা নয়, দেয়ালি বা দীপাবলী, কোনও কোনও রাষ্ট্রে দুর্গার সন্তানেরা আলাদাভাবে মর্যাদা পান। মহারাষ্ট্রে গণেশ সর্বোচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। লক্ষ্মী সরস্বতীর ভক্তও প্রচুর। মগধ উৎকল আর উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের বিশাল এলাকাজুড়ে গড়ে তোলা গৌড় রাজ্যের পরাক্রমশালী রাজা শশাঙ্ক ছিলেন লক্ষ্মীর ভক্ত। অবশ্য তাঁর মূল উপাস্য ছিলেন শিব। দুর্গার স্বামী। তাঁর আমলে চালু মুদ্রার এক পিঠে ছিল শিবের মূর্তি অন্য পিঠে লক্ষ্মীর। সেও সেই ছ’ শ’ খ্রিস্টাব্দের কথা। অত আগে থেকে দুর্গা পরিবারের সদস্যদের পূজা হয়ে এলেও একমাত্র বাঙালীর কল্পনায়ই তিনি পুত্র কন্যা সিংহ বাহিনীসহ পূর্ণরপে ধরা দিয়েছেন।
আশ্বিন মাসের পঞ্চমী তিথিতে আসেন তিনি। তখন শরতকাল। শরতের আকাশ মোটেই ‘মন কেমন করা’ নয়, বরং উজ্জ্বল নীলাকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ ঠিকরানো আলো মনকে নাচিয়ে দেয়। কৈশোরের নির্ভার আনন্দে ভেসে যাওয়া যেন- ‘কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে...।’ এই আকাশ এই প্রকৃতি দেখতে পান যারা, যারা শুনতে পান এই সুর শারদ উৎসব তাঁদেরই। সেখানে ধর্মের গ-ি নেই। আছে বাঁধ ভাঙ্গা আনন্দ আর একে অন্যকে ছুঁয়ে যাওয়া। ছন্নছাড়া স্বামী শিব, তিনি শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান। সারা বছর তাকে আগলে শরতে হিমালয়ের কৈলাস থেকে নেমে আসেন উমা। এই শ্যামল প্রকৃতির বাংলা তার বাপের বাড়ি। সন্তানদের নিয়ে বাপের বাড়ি বেড়াতে আসেন তিনি। ঢাক-শঙ্খ ধান-দুর্বায় উৎসবে মাতান বাপের বাড়ির সবাইকে। শারদ উৎসবের লৌকিক দিক বড় বেশি জীবন ঘেঁষা। চেনা জীবনের গল্পই বলে সে। আর অতি লৌকিক দিক সমৃদ্ধ করেছে পুরাণ সাহিত্য।
সেই প্রাচীন যুগে পৌরাণিক সাহিত্যের এত সমৃদ্ধি কি করে হয়েছিল, সেও এক বিস্ময়। পৃথিবীর পুরাণ সাহিত্যে ভারতীয় পুরাণের সঙ্গে একমাত্র তুলনা চলে গ্রীক পুরাণের। বিস্তৃতি ও ব্যাপকতায় তা গ্রীক পুরাণকে ছাপিয়ে গেছে। এক ক্ল্যাসিক পুরাণ থেকে জন্ম নিয়েছে অসংখ্য অনু পুরাণ। তাকে আশ্রয় করে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাহিত্য।
লৌকিক-পারলৌকিক দু’রকম পাঠই আছে এর। পারলৌকিক পাঠ বেঁচে আছে ধর্মবিশ্বাসে আর লৌকিক পাঠ সাহিত্যের সম্পদ। গ্রীক পুরাণ থেকে ভারতীয় পুরাণ সম্ভবত এখানেই আলাদা। গ্রিক পুরাণের চরিত্ররা সাহিত্যেই বিচরণ করে। ভারতীয় পুরাণ চরিত্ররা জীবিত সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে।
শারদীয় দুর্গাপূজার আচার-অনুষ্ঠানের ভিত্তি ক্ল্যাসিক পুরাণ। দেবতাদের বিচরণ এলাকা স্বর্গরাজ্যে এক সময় হানা দেয় অশুভ শক্তি অসুর। তার তা-বে দেবতারা পালিয়ে প্রাণে বাঁচেন। অনেকে তাকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন। অসুর দম্ভ করে বলে- ‘কোনও পুরুষ আমাকে হত্যা করতে পারবে না’। এক সময় তার তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা তাকে এ বর দিয়েছিলেন। বর পেয়ে ধীরে ধীরে অসুরের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ে। বেপরোয়া হয়ে ওঠে সে। ব্রহ্মা বিব্রত হন। নিজের দেয়া বর ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব নয়। অন্য দেবতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি ঠিক করলেন নারী শক্তি দিয়ে অসুর দমন করবেন। যেহেতু তিনি নিজেই বলেছিলেন, অসুরকে কোন পুরুষ হত্যা করতে পারবে না তাই নারীরূপে দুর্গার আগমন।
রাজা সুরথ প্রথম দেবী দুর্গার আরাধনা শুরু করেন। বসন্তে তিনি এ পূজার আয়োজন করায় দেবীর এ পূজাকে বাসন্তী পূজাও বলে। শারদীয় পূজার প্রচলন রামচন্দ্রের সময় থেকে। রাবণের কাছে বন্দী সীতাকে উদ্ধার করতে যাওয়ার আগে রাম দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। তখন ছিল শরতকাল। শরত থেকে শারদীয়। ধর্মীয় ব্যাখ্যা যা-ই থাক কোথায় যেন এ উৎসব ধর্মকে ছাপিয়ে যায়। যেন প্রকৃতির উৎসব ঋতু মেনে তিথি গুনে আয়োজন। কৃষিনির্ভর বাংলার দিনপঞ্জি চলত গ্রহ-নক্ষত্রের হিসেবে। কৃষকের আনন্দ-বেদনার কাব্য রচিত হয় ঋতুকে কেন্দ্র করে। বারো মাসে তেরো পার্বণের যে প্রবাদ তারও ভিত্তি ওই ঋতু। ফসল বোনার, ফসল কাটার নবান্ন সংক্রান্তি পিঠা-পায়েস ইত্যাদি নানা উপলক্ষে উৎসবের ছলে এক হওয়া, সে উৎসব সাধারণ গ্রামীন বাঙালীর। ধর্মের আবরণটুকু সরিয়ে দিলে ভীষণই প্রাকৃতিক। ভীষণ নিজের। শাব্দিক অর্থেই সর্বজনীন। বাঙালিয়ানার সবটুকু ধারণ করে আছে এ উৎসব।
সনাতন ধর্ম এ মাটির। লৌকিক জীবনকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে এগোতে এগোতে অনেক কিছু আত্মস্থ করেছে। তবে বর্ণপ্রথার কাঠিন্য একে সঙ্কীর্ণও করেছে। গোঁড়ামি সব ধর্মকেই সঙ্কীর্ণ করে, যার অনিবার্য পরিণতি হিংসা আর সন্ত্রাস। তার ওপর রয়েছে রাজনৈতিক ব্যবহার। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার হয়েছে, হচ্ছে। ধর্মকে যখন থেকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু হয়েছে তখন থেকে এতে সন্ত্রাস ঢুকেছে।