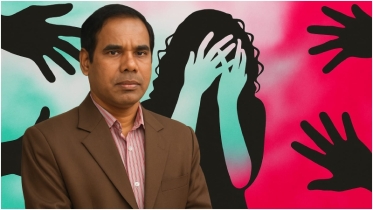প্রাক্তন শিক্ষক, বাংলা বিভাগ
মালিখালী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
নাজিরপুর, পিরোজপুর
পূর্ব প্রকাশের পর...
বিরাম চিহ্নের ব্যবহার
১। কমা (,) : বাক্য সুস্পষ্ট করতে বাক্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে প্রতিটি ভাগের মাঝে কমা বসে। যেমন- সুখ চাও, সুখ পাবে বই পড়ে।
পরস্পর সম্পর্কিত একাধিক বিশেষ্য বা বিশেষণ পদ একসঙ্গে ব্যবহৃত হলে শেষ পদটি ছাড়া প্রতিটির পরে কমা বসে। যেমন- ১৬ ডিসেম্বর আমাদের মন সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, ভালবাসা, আনন্দে ভরে থাকে।
সম্বোধনের পরে কমা বসে। যেমন- রশিদ, এদিকে এসো।
জটিল বাক্যের প্রত্যেকটি খ-বাক্যের পরে কমা বসে। যেমন- যে পরিশ্রম করে, সেই সুখ লাভ করে।
কোন বাক্যে উদ্ধৃতি থাকলে, তার আগের খ-বাক্যের শেষে কমা (,) বসে। যেমন- আহমদ ছফা বলেন, ‘মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।’ তুমি বললে, ‘আমি কালকে আবার আসবো।’
মাসের তারিখ লেখার সময় বার ও মাসের পর কমা বসে। যেমন- ২৫ বৈশাখ, ১৪১৮, বুধবার।
ঠিকানা লেখার সময় বাড়ির নম্বর বা রাস্তার নামের পর কমা বসে। যেমন- ৬৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা- ১০০০।
ডিগ্রী পদবি লেখার সময় কমা ব্যবহৃত হয়। যেমন- ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, এম,এ, পি-এইচ,ডি।
২। সেমিকোলন (;) : কমার চেয়ে বেশি কিন্তু দাঁড়ির চেয়ে কম বিরতি দেয়ার জন্য সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। যেমন-
আমরা সবাই সবাইকে ভালবাসি; আসলেই কি সবাই ভালবাসি?
৩। দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) : প্রতিটি বাক্যের শেষে দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি দিয়ে বাক্যটি শেষ হয়েছে বোঝায়। যেমন-
আমি কাল বাড়ি আসবো।
৪। প্রশ্নবোধক চিহ্ন : প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন-তুমি কেমন আছ?
৫। বিস্ময়সূচক বা আশ্চর্যবোধক চিহ্ন : বিস্মিত হওয়ার অনুভূতি প্রকাশের জন্য কিংবা অন্য কোন হৃদয়ানুভূতি প্রকাশের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন- আহা! কী চমৎকার দৃশ্য। ছি! তুমি এত খারাপ। হুররে! আমরা খেলায় জিতেছি।
৬। কোলন : একটি অপূর্ণ বাক্যের পর অন্য একটি বাক্য লিখতে হলে কোলন ব্যবহার করতে হয়। যেমন- সভায় ঠিক করা হল : এক মাস পর আবার সভা অনুষ্ঠিত হবে।
৭। ড্যাস (-) : যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে দুই বা তারচেয়েও বেশি পৃথক বাক্য লেখার সময় তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে ড্যাস চিহ্ন ব্যবহার করা যায়। যেমন-তোমরা দরিদ্রের উপকার কর- এতে তোমাদের সম্মান যাবে না- বাড়বে।
৮। কোলন ড্যাস (:-) : উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগের জন্য কোলন ড্যাস ব্যবহৃত হয়। যেমন-
পদ পাঁচ প্রকার :- বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, অব্যয় ও ক্রিয়া।
৯। হাইফেন বা সংযোগ চিহ্ন : সমাসবদ্ধ পদের অংশগুলো বিচ্ছিন্ন করে দেখানোর জন্য হাইফেন ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ, দুটি পদ একসঙ্গে লিখতে গেলে হাইফেন দিয়ে লিখতে হয়। যেমন- সুখ-দুঃখ, মা-বাবা।
১০। ইলেক বা লোপ চিহ্ন : কোন বর্ণ লোপ করে বা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ বোঝাতে ইলেক বা লোপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। কবিতা বা অন্যান্য সাহিত্যে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- মাথার ’পরে জ্বলছে রবি। (’পরে=ওপরে)
পাগড়ি বাঁধা যাচ্ছে কা’রা? (কা’রা=কাহারা)
১১। উদ্ধরণ চিহ্ন : বক্তার কথা হুবুহু উদ্ধৃত করলে সেটিকে এই চিহ্নের মধ্যে রাখতে হয়। অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ উক্তিকে এই চিহ্নের মধ্যে রেখে লিখতে হয়। যেমন- ফিদেল ক্যাস্ত্রো বলেছেন, ‘জন্মভূমি অথবা মৃত্যু’।
১২। ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন ( ).{ }. [ ] : গণিতশাস্ত্রে এই তিনটির আলাদা গুরচত্ব থাকলেও ভাষার ক্ষেত্রে এদের আলাদা কোন গুরচত্ব নেই। তবে সাহিত্যে ও রচনায় ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করা হয়। যেমন- ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর রমনার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) পাকিস্তান বাংলাদেশের কাছে পরাজয় মেনে দলিলে স্বাক্ষর করে।
ঢাকা, বাংলাদেশ বৃহস্পতিবার ০৭ আগস্ট ২০২৫, ২৩ শ্রাবণ ১৪৩২