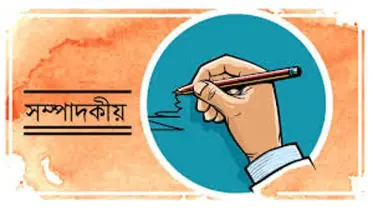পুলিশকে হতে হবে জনবান্ধব
আশাব্যঞ্জক খবর যে, অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্যোগ ও আশ্বাসে নজিরবিহীন অনুপস্থিতির প্রায় এক সপ্তাহ পর অধিকাংশ পুলিশ সদস্য নিজ নিজ কর্মস্থলে (থানায় ও সড়কে) ফিরে এসেছেন। আশা করা যায় অল্প কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশ তার দায়িত্ব পূর্ণোদ্যমে শুরু করতে পারবেন এবং যথাযথ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবেন। তবে দায়িত্ব পালনে পুলিশকে নতুনরূপে আবির্ভূত হতে হবে।
জনবান্ধব হতে হবে শতভাগ। কর্মস্থলে কাজ করার জন্য পুলিশ এখন জনগণের কাছে নিজেদের নিরাপত্তা ও সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন। জনগণের সহযোগিতা অবশ্যই প্রয়োজন। আগে যেখানে জনগণের নিরাপত্তা বিধান তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, এখন তারাও নিরাপত্তা চান। সহযোগিতা প্রদান যেমন প্রয়োজন, তেমনি বিদ্যমান অবস্থার কারণ বিশ্লেষণপূর্বক পুলিশ বাহিনীকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন। কেবল পোশাক বা ওপরের অবয়বে নয়, আইনি সংস্কারসহ পুলিশের মানসকাঠামোর পরিবর্তনও অপরিহার্য।
১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ২৫ মার্চের কালরাতেই রাজারবাগ পুলিশ লাইনস থেকে পাক হানাদারদের বিরুদ্ধে বুলেট ছুড়ে পুলিশের প্রথম প্রতিরোধের কথা আমাদের সবার জানা। জনগণের প্রয়োজনে নিত্য পুলিশের প্রয়োজন। কাগজে-কলমে পুলিশ জনগণের বন্ধু। সেবাই পুলিশের ধর্ম। তথাপি আজ পুলিশের সঙ্গে জনগণের দূরত্ব সুস্পষ্ট। দেশের বেশিরভাগ মানুষ পুলিশকে বিশ্বাস করতে চায় না।
অনেক সময় পুলিশের কাছে প্রত্যাশিত সেবা পায় না বিধায় মানুষ হয়রানির শিকার হয় পুলিশের কাছে। তবে বেশিরভাগ পুলিশই যে খারাপ তা নয়। বন্ধু, আত্মীয় ও পরিচিত এমন বেশকিছু পুলিশকে জানি যারা অত্যন্ত মানবিক এবং জনবান্ধব। তবে যারা খারাপ তাদের কর্মকা- নিন্দনীয় এবং এত ব্যাপক যে, তা জনগণকে বিষিয়ে তুলেছে এবং জনমনে পুলিশ সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
বিশেষ করে অরাজনৈতিক ও ক্ষমতাকেন্দ্রিক না হওয়া সত্ত্বেও নাগরিক আন্দোলন এবং শিক্ষার্থীদের নিরাপদ সড়ক ও বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে পুলিশের মাত্রাতিরিক্ত মারমুখী ভূমিকায় ছাত্র-জনতা প্রায় সবাই পুলিশের ভূমিকায় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। বিরাজমান এই বৈরী পরিস্থিতির মধ্যে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক বেশি বিদ্বেষাত্মক হয়েছে অতি সম্প্রতি– জুলাই-আগস্ট মাসে।
পুলিশের সবাই দায়ী না হলেও জনগণের একটা সামগ্রিক ক্ষোভ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। এই অবস্থার জরুরি অবসান দরকার দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থেই। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখলে জননিরাপত্তা ও আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটবে, যা ইতোমধ্যে আমরা দেশের প্রায় সর্বত্র প্রত্যক্ষ করেছি।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও দেশত্যাগের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। গত ১ জুলাই এবং বিশেষ করে ১৫ জুলাই থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্রতিহত করতে গিয়ে পুলিশের ছাত্র-জনতাবিরোধী যে ভূমিকা জাতি প্রত্যক্ষ করেছে তাতে পুলিশের প্রতি ছাত্র-জনতা চরমভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।
১৬ জুলাই পুলিশের গুলিতে রংপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আবু সাঈদের নির্মম মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুলিশের হিংস্রতা প্রকাশ পায়। পরবর্তীতে আন্দোলন আরও তীব্রতা ধারণ করে এবং বেশকিছু পুলিশের আক্রমণও ব্যাপক হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে ক্ষমতাসীন সরকারদলীয় ছাত্র ও যুবকর্মীরা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মসূচিতে আঘাত হানে। এর ফলে গত ৫ আগস্ট পর্যন্ত প্রায় ৫০০ ছাত্র-জনতা নিহত হয়।
অন্যদিকে পটপরিবর্তনের পর বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার আক্রোশে ৪০০-এর বেশি থানা আক্রমণের শিকার হয় এবং অনেক পুলিশ নিহত হন। এই অবস্থায় প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে বাংলাদেশের সব থানা ছিল পুলিশশূন্য, এমনকি বন্ধও ছিল। ফলে মানুষ প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা সড়কে ও পাড়া-মহল্লা পাহারা দিলেও তা পুলিশের অভাব পূরণে যথেষ্ট ছিল না। পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-জনতার সম্পর্কটা এমনটি হওয়ার কথা ছিল না।
তবে এটা সত্য যে, সব পুলিশ এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী নন। মূলত উচ্চপদস্থ কিছু ক্ষমতালোভী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী কর্মকর্তার কারণে মাঠ পর্যায়ের পুলিশকে জনগণের বিপক্ষে অস্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছে। বিষয়টি অবগত করে ইতোমধ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষ থেকে জনগণের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে। নবনিযুক্ত আইজিপিও দুঃখ প্রকাশের পাশাপাশি অপেশাদার পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অঙ্গীকার করেছেন।
পুলিশকে তার দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। জনগণের এখন ক্ষোভ-আক্রোশ ভুলে গিয়ে, ক্ষমা করে দিয়ে পুলিশকে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করা উচিত। কারণ, পুলিশ ছাড়া জনগণ শান্তিতে, নিরাপদে থাকতে পারবে না। পুলিশের মধ্যে এখন যে হতাশা ও গ্লানি দেখা দিয়েছে তা প্রলম্বিত হলে তারা মানসিক মনোবল হারিয়ে ফেলবে।
জনগণের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই পুলিশের শক্তি ও মনোবল ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন। গুটি কয়েকের আচরণ অপ্রত্যাশিত হলেও ‘পুলিশ জনগণের বন্ধু’ এটা প্রতিষ্ঠা করার সময় এসেছে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কিছু সংখ্যক অত্যুৎসাহী ও নির্দয় পুলিশের জন্য পুরো পুলিশ প্রশাসনকে দায়ী করা ঠিক হবে না। থানা ভাঙচুর ও অস্ত্র লুট করা কোনো সমাধান নয়। অস্ত্র সাধারণ মানুষের মাঝে চলে গেলে তার পরিণত শুভকর হতে পারে না। অন্যায়ের প্রতিবাদে সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে নাÑ এ দিকটি গুরুত্বের সঙ্গে মাথায় রাখতে হবে।
জনগণের বিরুদ্ধে পুলিশের দাঁড়ানোর কারণ কী, কিভাবে জনগণের সঙ্গে পুলিশের দূরত্ব দূর করা যায় সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। ন্যায়-অন্যায় যে কোনো পরিস্থিতিতে পুলিশকে কেন শাসকদের নির্দেশ অনুযায়ী জনগণের বিপক্ষে দাঁড়াতে হবে? পুলিশের নিজস্ব বিচার-বিবেচনা, নিজস্ব বিধি ও আইনশৃঙ্খলা থাকা প্রয়োজন, যাতে করে পুলিশ আইনের আওতায় শাসকের নির্দেশ পালন করবেন, জনগণের বিপক্ষে না গিয়ে।
শাসকশ্রেণি যাই বলবে তা-ই যেন মান্য করতে বাধ্য হতে না হয়। আইন অনুযায়ী জনগণের সঙ্গে আচরণ করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে পুলিশকে। উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নির্দেশ দিলেও অধস্তন পুলিশকে অমানবিক ও দানবিক কর্মকা- থেকে বিরত রাখার জন্য রক্ষামূলক আইনি বিধান থাকতে হবে। পুলিশের কর্মপরিধি ও অন্যায় নির্দেশ পালনের বাধ্যবাধকতার বিষয়টির সংস্কার করতে হবে। জনবান্ধব করে ১৮৬১ সালে প্রণীত পুলিশ আইনসহ পুলিশ প্রবিধান সংস্কারের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে সরকারকে।
কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে পুলিশকে কেউ যেন পেটোয়া বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে না পারে সে ব্যবস্থা করা এখন সময়ের দাবি। পুলিশের প্রশিক্ষণের সময় নীতিনৈতিকতা, মানবাধিকার, সমাজ ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে জনবান্ধব নীতি অনুশীলন করতে হবে। যথাযথ জবাবদিহির আওতায় এনে পুলিশকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপযুক্ত অবস্থানে প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে পুলিশের সঙ্গে জনগণের বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি না হয়।
এজন্য পুলিশ ও জনগণকেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে। পুলিশকে থানাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যাতে মানুষ থানার নাম শুনলে আর ভয় না পায়। থানা যেন তাদের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ের স্থানে পরিণত হয়। বর্তমান বাস্তবতায় অনেক সময় (অবশ্য সব ক্ষেত্রে নয়) মানুষ তার নিরাপত্তার জন্য সামান্য একটা জিডি করার জন্যও থানাকে নিরাপদ বোধ করে না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিডি করতেও টাকা দিতে হয়। কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে মামলা করলেও পুলিশকে টাকা দিতে হয়।
প্রায় সময় মামলা করে বিচারের জন্য থানা পুলিশ ও স্থানীয় সরকারদলীয় নেতা-কর্মীদের টাকা (ঘুষ) দিতে হয়। এসব দুর্বৃত্তায়ন বন্ধ করার জন্য পুলিশকেই এগিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা যেন এমন না হয় যে, বর্তমান দুর্দশা কেটে গেলে পুলিশ আবার আগের চরিত্রে ফিরে যাবে। নিরাপদ সড়কের দাবিতে ২০১৮ সাল থেকে ছাত্রসমাজ যেভাবে জেগেছে আশা করা যায় এখন কোনো অন্যায়কারীর আর রক্ষা নেই। এটি কেবল পুলিশের ক্ষেত্রে নয়, সকল ক্ষেত্রে (শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি অফিস, সচিবালয়, বিমানবন্দর, পাসপোর্ট অফিস ইত্যাদি) যেখানে অন্যায় সেখানে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সৃষ্টি হবে।
সার্বিক বিচারে পুলিশ-জনগণের সম্পর্ক যত দ্রুত সম্ভব স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ করা প্রয়োজন। পুলিশ যদি তার ভূমিকা সঠিকভাবে পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে অপরাধের ব্যাপকতা দ্রুত প্রসারিত হবে। নানা অপরাধীচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে ইতোমধ্যে। এর ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা চরমভাবে বিঘিœত হতে পারে। জনজীবন অনিরাপদ হয়ে পড়তে হবে।
তাই পুলিশের শক্তি ও মনোভাব ফিরিয়ে আনা এবং জনগণের প্রয়োজনীয় সেবা ও নিরাপত্তার জন্য পুলিশ-জনগণের মধ্যে আস্থা ফিরিয়ে আনা আবশ্যক। পুলিশের সঙ্গে ছাত্র-নাগরিকের বর্তমান বিরোধাত্মক পরিস্থিতির তিনটি মূল কারণ– পুলিশের যথাযথ দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও দুর্নীতি, লেজুড়বৃত্তির কারণে সরকারের স্থানীয় আইনি ফোর্সে পরিণত হওয়া এবং আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে ওপরের মহলের নির্দেশক্রমে জনগণের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ। এই তিনটিরই সমাধান সম্ভব। শুধু পোশাক পরিবর্তন যথেষ্ট নয়, দরকার আমূল সংস্কার, কেবল সাজসজ্জা পরিবর্তন নয়, দরকার ঢেলে সাজানো।
জনগণ যদি থানা-পুলিশ থেকে তাদের নিরাপত্তামূলক সেবা সঠিকভাবে পায় তাহলে সৃষ্ট বিরোধপূর্ণ সম্পর্ক রূপ নেবে বন্ধুত্বে। গ্রামে-গঞ্জে, শহরে, রাস্তায় জনগণের যে কোনো বিপদে ও নিরাপত্তার প্রশ্নে পুলিশকে আশ্রয়ের ও সেবকের ভূমিকা পালনে ব্রতী হতে হবে। পুলিশের নাম শুনলে কিংবা পুলিশকে দেখলে যেন জনগণ সহায়বোধ করে, বিশেষ করে দুর্বল, নারী, শিশু যদি পুলিশকে বন্ধু ভাবতে পারে সেটা পুলিশের পরিবর্তিত ভূমিকার মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে জনগণের নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত হবে, তেমনি পুলিশের প্রশ্নে জনমনে যে বিদ্বেষ মনোভাব রয়েছে তা তিরোহিত হবে।
বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন পুলিশ মনোবল প্রায় হারিয়ে ফেলেছে, জনগণের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে, সে অবস্থায় জনগণের উচিত পুলিশকে একটা সুযোগ দেওয়া, যাতে করে পুলিশ তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারে। আর পুলিশকেও জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হতে হবে। আইনি সংস্কার করতে একটু সময় লাগলেও চিহ্নিত পুলিশ কর্মকর্তা, যাদের দানবিক ভূমিকা ইতোমধ্যে জনগণের কাছে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ও দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
তাহলে বিক্ষুব্ধ জনগণ কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে। ইতোমধ্যে লুটকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করা শুরু হয়েছে। আরও কিছু জনগণের কাছে রয়ে গেছে কি না ভালো করে অনুসন্ধান করতে হবে। সাধারণ মানুষের কাছে অস্ত্র থাকা জননিরাপত্তার জন্যই নিরাপদ নয়।
পুলিশের জব ডেসক্রিপশন বা কর্মবণ্টনে জনবান্ধব পরিবর্তন সূচিত করতে হবে। আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে যতটুকু শক্তি দেখাতে হয় তার মধ্যে পুলিশকে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কেউ যেন কারও ক্ষতি করতে না পারে, কারও প্রতি অন্যায় করতে না পারে, সবার অধিকার যেন নিশ্চিত থাকে, সেদিকে পুলিশকে আইন অনুযায়ী কঠোর হতে হবে।
তবে কোনোভাবেই আইন বহির্ভূত পন্থায় জনগণকে শারীরিকভাবে নির্যাতন-নিগ্রহ করে নয়। কোনো কারণে আদালতের নির্দেশক্রমে কোনো আসামিকে রিমান্ডে নিতে হলেও তার সঙ্গে আইনসম্মতভাবে আচরণ করতে হবে। রিমান্ড মানেই অমানবিক ও অবর্ণনীয় শারীরিক নির্যাতন নয়। নারী, শিশু, প্রান্তিক ও দুর্বল শ্রেণির মানুষের জন্য পুলিশকে বিশেষভাবে সহায়ক ও উদার হয়ে উঠতে হবে। পুলিশের পক্ষে সেটা অসম্ভব কিছু নয়।
কারণ, পুলিশও বিবেকসম্পন্ন মানুষ। পুলিশেরও পরিবার-পরিজন রয়েছে। জনগণ ও পুলিশ কেউ কারও শত্রু নয়। অতীত ভুলে, ভুল সংশোধন করে পুলিশ যদি ইতিবাচক ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়, তাহলে পুলিশ অবশ্যই দেশবাসীর সহযোগিতা ও সম্মান পাবেন। পৃথিবীর উন্নত অনেক দেশে এর উদাহরণ আছে, যেখানে পুলিশের সম্মান ও মর্যাদা অনেক ওপরে। বাংলাদেশের মানুষও তা দেখতে চায়– নিজেদের প্রয়োজনে, দেশের স্বার্থে।
লেখক : অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়