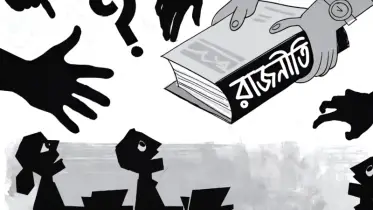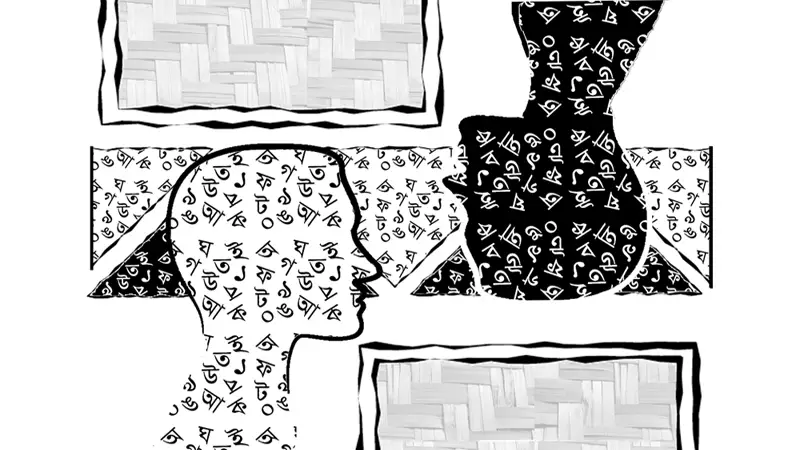
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ কবিতার কয়েকটি চরণ দিয়ে নিবন্ধটি শুরু
আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ কবিতার কয়েকটি চরণ দিয়ে নিবন্ধটি শুরু করতে চাই, “আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি/ ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি/ আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি/ আমি কি ভুলিতে পারি”। ১৯৪৭ সালে মুসলিম লীগ উত্থাপিত সাম্প্রদায়িক দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। পূর্ব বাংলার সিংহভাগ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন তাদের জাতীয় ভাষা সমস্যার সমাধান হয়নি।
আর্যদের ভাষা যেমন বাংলা ছিল না, মধ্যযুগে মুসলমান শাসকদের ভাষাও তেমনি বাংলা ছিল না। তাদের দাপ্তরিক ভাষা ছিল ফারসি। আধুনিক যুগে ব্রিটিশ শাসনামলে দাপ্তরিক ভাষা ছিল ইংরেজি। অর্থাৎ কোনো শাসনামলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, ‘দেশে ব্রিটিশ শাসন জমাট হয়ে উঠার ধাপে ধাপে ক্রমে সংস্কৃত-আরবি-আশ্রিত আবহমান বিদ্যাচর্চার ধারা অবসৃত, তাৎপর্যহীন হয়ে গেল’।
বাংলা ভাষার প্রতি এমন অবহেলা লক্ষ্য করে ষোড়শ শতকের কবি আবদুল হাকিম লিখেছেন, ‘যে সব বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি। দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়, নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়’।
ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এরই ফলস্বরূপ ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভেঙে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র দুটির সৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ অবিবেচনাপ্রসূত। স্বাধীনতা লাভের পূর্ব থেকেই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। নবগঠিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহল প্রথম বিতর্ক শুরু করেন।
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পাকিস্তানের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে করাচিতে পাকিস্তান এডুকেশনাল কনফারেন্স আহ্বান করেন। এ কনফারেন্সে উর্দুকে একমাত্র জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা এর বিরোধিতা করেন। এ সভায় পূর্ব বাংলার পক্ষে আবদুল হামিদ ও হাবিবুল্লাহ বাহার বাংলাকে পূর্ব বাংলার শিক্ষার মাধ্যম করার প্রস্তাব দেন। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন।
এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হকসহ পূর্ব বাংলার কয়েকজন বুদ্ধিজীবী লেখনির মাধ্যমে প্রতিবাদ জানান। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে ‘পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা’ শিরোনামে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় এক নিবন্ধে লিখেন যে, ‘যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নেই। যদি বাংলা ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করতে হয়, তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য’।
তিনি আরও বলেন যে, ‘আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি বাস্তব কথা। যা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারা ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক কিংবা টুপি দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই’।
ড. মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, ‘ইহাতে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সর্বনাশ ঘটিবে।...উর্দু বহিয়া আনিবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মরণÑ রাজনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মৃত্যু। এই রাষ্ট্রীয়ভাষার সূত্র ধরিয়া শাসন, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব-পাকিস্তান হইবে উত্তর ভারতীয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানি উর্দুওয়ালাদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র, যেমন ভারত ছিল ইংরেজি রাষ্ট্রভাষার সূত্রে ইংরেজদের শাসন ও শোষণের ক্ষেত্র’। তিনি আরও বলেন, ‘ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছে, কোন দেশ ইহার নিজের ভাষা দিয়া অপর দেশকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই’।
এর ফলে পূর্ব বাংলার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সপক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টি হয়। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেও বাংলা ভাষার দাবিকে জোরদার করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানিদের অধিকাংশের মাতৃভাষা বাংলার ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের আগ্রাসনের কারণ হিসেবে তারা যদিও ‘এক পাকিস্তানের সংহতি’র দোহাই দিয়েছিলেন, কিন্তু এর নেপথ্যে কাজ করেছিল ঔপনিবেশিক চিন্তাভাবনা।
১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলিতে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা করার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের এ বক্তব্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। খাজা নাজিমুদ্দীনও এর সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেন, পূর্ব বাংলার জনগণ রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুকে চায়। অথচ সমগ্র পাকিস্তানের ৫৪.৬ শতাংশ মানুষ বাংলাভাষী এবং মাত্র ৭.২ শতাংশ মানুষ উর্দুভাষী।
পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চলের মোট সাতটি ভাষার মধ্যে বাংলা ভাষা অর্ধেকেরও বেশি মানুষের মাতৃভাষা এবং অন্য ছয়টি ভাষায় অর্ধেকেরও কম মানুষ কথা বলে। কিন্তু সমাজ ও রাজনীতির মৌলিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকমহল ধর্মের দোহাই দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির ওপর নগ্নভাবে আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ‘উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা’ এ ঘোষণা দিলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এর প্রতিবাদ জানায়।
নুরুল আমিন সরকার ছাত্র আন্দোলনের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টায় ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল প্রকার মিছিল ও জনসমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব ঘোষিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ছাত্র-জনতা মিছিল নিয়ে সেøাগান দিতে দিতে প্রাদেশিক পরিষদের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের বাধা দিতে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ শুরু করে। একপর্যায়ে পুলিশ গুলি চালালে আবুল বরকত, আব্দুল জব্বার, রফিক উদ্দিন আহমদ, আবদুস সালাম, শফিকুর রহমানসহ নাম না জানা কয়েকজন শহিদ হন।
ছাত্রদের ওপর নির্বিচারে গুলির প্রতিবাদে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন প্রমুখ সদস্যগণ পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন কক্ষ থেকে ওয়াকআউট করেন। পরিশেষে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম সংবিধানের ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে উর্দু এবং বাংলা উভয় ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলা ভাষার প্রশ্নে সর্বদাই আপোসহীন ছিলেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে তিনি বলেন, ‘বাংলা পাকিস্তানের শতকরা ছাপ্পান্ন ভাগ লোকের মাতৃভাষা। তাই বাংলাই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। তবুুও আমরা বাংলা এবং উর্দু দুইটা রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করেছিলাম’। তিনি আরও বলেন, ‘দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে। আরব দেশের লোকেরা আরবি বলে। পারস্যের লোকেরা ফার্সি বলে, তুরস্কের লোকেরা তুর্কি ভাষা বলে...। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ধর্মভীরু মুসলমানদের ইসলামের কথা বলে ধোঁকা দেয়া যাবে ভেবেছিল, কিন্তু পারে নাই।
যেকোন জাতি তার মাতৃভাষাকে ভালবাসে। মাতৃভাষার অপমান কোন জাতিই কোনকালে সহ্য করে নাই’। কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দিন বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন, ‘মুজিব, বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হলে বাংলার কৃষ্টি, সভ্যতা সব শেষ হয়ে যাবে। আজ যে গানকে তুমি ভালবাস, এর মাধুর্য ও মর্যাদাও নষ্ট হয়ে যাবে। যা কিছু হোক, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করতেই হবে’। আব্বাসউদ্দিনের সেদিনের কথাগুলো বঙ্গবন্ধু হৃদয়ে ধারণ করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে প্রথম কারাবন্দিদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন।
এ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেওয়ার জন্য পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারে বঙ্গবন্ধুকে দুই বছরের অধিক সময় কারাগারে বন্দি রাখা হয়। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জেলে বন্দি থাকা অবস্থায় বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পূর্ব বাংলায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাই ১৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর জেলে পাঠানো হয়। নারায়ণগঞ্জ স্টিমার ঘাটে শামসুদ্দোহাসহ কয়েকজন ছাত্রনেতার সঙ্গে দেখা হয়।
এ সময় বঙ্গবন্ধু তাদের বলেন যে, ‘যেন একুশে ফেব্রুয়ারীতে হরতাল মিছিল শেষে আইনসভা ঘেরাও করে বাংলা ভাষার সমর্থনে সদস্যদের স্বাক্ষর আদায় করা হয়’। জেলখানায় আমরণ অনশন প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু বলেন, ‘...আমাকে যখন জেল কর্তৃপক্ষ অনুরোধ করল অনশন ধর্মঘট না করতে, তখন আমি বলেছিলাম, ছাব্বিশ-সাতাশ মাস বিনা বিচারে বন্দি রেখেছেন। কোনো অন্যায়ও করি নাই। ঠিক করেছি জেলের বাইরে যাব, হয় আমি জ্যান্ত অবস্থায়, না হয় মৃত অবস্থায় যাব’।
জেলখানায় অনশনে যাওয়ার পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁর মনের অবস্থা এভাবে ব্যক্ত করেন, ‘...একদিন মরতেই হবে। অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি মরতে পারি, সে মরাতেও শান্তি আছে’। বঙ্গবন্ধু যদি সেদিন জেলখানায় না থাকতেন, হয়তো পুলিশের গুলিতে সেদিন তিনিও শহিদ হতেন। তাই বঙ্গবন্ধু শুধু বাঙালি জাতির পিতাই নন, বাংলাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য তিনি বাংলা ভাষারও পিতা।
স্বাধীনতার এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু বাংলাকে যেখানে সাংবিধানিকভাবে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা দিয়েছেন। অথচ এখনও রাষ্ট্রের সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়। যদিও বাংলাদেশের সংবিধানে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে, তবুও সর্বত্র এ ভাষার ব্যবহারে অবহেলা লক্ষণীয়। জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পর বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন, যা বিশ্বসভায় কোনো বাঙালি রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের প্রথম বাংলায় ভাষণ।
১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ নভেম্বর জাতিসংঘের অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কো বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় বাঙালির এ আত্মত্যাগের স্বীকৃতিস্বরূপ ২১ ফেব্রুয়ারিকে ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে ঘোষণা দেয়। জাতিসংঘভুক্ত দেশসমূহ তখন থেকেই প্রতিবছর ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করে আসছে। পৃথিবীর কোথাও ভাষার নামে দেশ নেই। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছে ভাষার নামে। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালিই একমাত্র জাতি, যারা একই সঙ্গে ভাষা ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে।
কিন্ত এখনো উচ্চ আদালত, চিকিৎসা-প্রকৌশলবিদ্যাসহ উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন অফিসে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা অনেক ক্ষেত্রেই অবহেলিত। অথচ এ ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু দুই বছরেরও অধিক সময় জেলে বন্দি ছিলেন, জেলখানায় অনশন করেছেন, ভাষা শহিদরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, অনেকেই পুলিশের গুলিতে আহত হয়েছেন, অনেকেই কারাজীবন ভোগ করেছেন।
বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। এটা শুধু ভাষাগত কিংবা সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না। এটা ছিল সামন্তবাদের তাঁবেদার পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক-শোষক শ্রেণির জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে আপামর জনসাধারণের এক ব্যাপক গণআন্দোলন। ভাষা আন্দোলনের ওপর ভিত্তি করে রচিত পূর্ব বাংলার প্রথম প্রতিবাদী নাটক কবর-এর রচয়িতা মুনীর চৌধুরী, ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানের সুরকার আলতাফ মাহমুদ, ভাষা আন্দোলনের ওপর রচিত উপন্যাস আরেক ফাল্গুন-এর রচয়িতা জহির রায়হান, গণপরিষদের অধিবেশনে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা রাখার দাবি উত্থাপনকারী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখকেও মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিকট জীবন দিতে হয়। তাই বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের সর্বস্তরে এর ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।
হাসান হাফিজুর রহমানের ‘অমর একুশে’ কবিতার কয়েকটি চরণ দিয়ে নিবন্ধটি শেষ করতে চাই। ‘সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার-বি বিষণ্ণ থোকা থোকা নাম; এই এক সারি নাম বর্শার তীক্ষè তীরের মতো এখন হৃদয়কে হানে,...যাঁদের হারালাম তাঁরা আমাদেরকে বিস্তৃত করে দিয়ে গেল দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত, কণা কণা করে ছড়িয়ে দিয়ে গেল দেশের প্রাণের দীপ্তির ভেতর মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতে’।
লেখক : শিক্ষক ও প্রাবন্ধিক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়