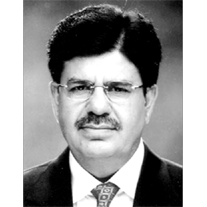
বাংলাদেশে আমাদের অনেক গৌরবের দিবস আছে। আমরা দিবসগুলো যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করি বটে, কিন্তু কতটা নতুন প্রজন্মের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ তা একটু ভেবে দেখার অবকাশ আছে। আমরা অহঙ্কারের ২১ ফেব্রুয়ারি পালন করব। মনে হয় সবই দিবসকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। এর আগে বা পরে এর কোন আবহ তেমন লক্ষ্য করা যায় না। যদিও বইমেলার কারণে ভাষার মাসের একটা আবহ থাকে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, ভাষার চর্চা সবকিছু সকল সময়ের, দৈনন্দিন, বছরব্যাপী। নতুন প্রজন্ম ইতিহাসবিমুখ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের গৌরবের ইতিহাসগুলো তাদের কাছে সেভাবে উপস্থাপন না করতে পারলে ইতিহাস হারিয়ে যাবে। নতুন করে আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন সামনে এসে দাঁড়াবে। আগামী প্রজন্ম তখন তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উত্তরহীন বোবা হয়ে থাকবে। এর দায়িত্ব আমরা এড়াতে পারি না। একে একে সাক্ষী প্রজন্ম হারিয়ে যাচ্ছে। এখনও সময় আছে ইতিহাসকে উজ্জ্বল করে রাখার। আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাস কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আছে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, আছে সুদীর্ঘ ২৩ বছরের সংগ্রামের, ত্যাগের, বিজয়ের ইতিহাস, আছে অহঙ্কারের লক্ষ প্রাণ দেয়ার ইতিহাস পরম্পরা, ধারাবাহিক। সঠিক নির্মোহ ইতিহাস প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম প্রবাহিত করা আমাদের কর্তব্য ও দায়িত্ব। পূর্ব পুরুষের মাতৃভূমির জন্য ত্যাগের ইতিহাস থেকে দেশপ্রেম জাগে আর দেশপ্রেমহীন কোন জাতি এগুতে পারে না; পারে না দেশের কল্যাণ বয়ে আনতে।
এ লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আমরা ১৯৯১ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষক সমিতি, ডক্টরস ফোরাম এবং ছাত্র সংসদ সমন্বয়ে গঠিত একুশে উদ্যাপন কমিটির মাধ্যমে ভাষাসৈনিক সমাবেশের আয়োজন করেছিলাম। অধ্যাপক এ কে এম আবদুস সালামকে আহ্বায়ক এবং ঢামেক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ডাঃ কামরুল হাসান খানকে সদস্য সচিব করে শিক্ষক, চিকিৎসক এবং ছাত্রদের সমন্বয়ে একুশে উদযাপন কমিটি গঠন করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য তুলে ধরা। দেশে-বিদেশে যত সম্মানিত ভাষা সংগ্রামী বেঁচেছিলেন মোটামুটি সবাই এসেছিলেন। আমরা মাসখানেক সময় নিয়ে ব্যাপক প্রচার দিয়েছিলাম। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ভাষাসৈনিকদের পাশাপাশি দেশের সুধীজনদের। সাংস্কৃতিক আয়োজন ছিল বক্তৃতার ফাঁকে ফাঁকে। জানা মতে, দুই-একজন ভাষাসৈনিক বাদ দিয়ে সেদিন সবাই ঢাকা মেডিক্যাল চত্বরে এসেছিলেন, এসেছিলেন ছাত্র-শিক্ষকসহ সব বয়সের মানুষ। নতুন প্রজন্মের ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য আমরা বিশেষ প্রচারের আয়োজন করেছিলাম। ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। ছাপানো হয়েছিল পোস্টার, স্মরণিকা। বিশাল প্যান্ডেল দিয়ে সাজানো হয়েছিল কলেজের ভেতরের ঐতিহাসিক চত্বর। ১৯৫২ সালের পরে ভাষাসৈনিকদের এত বড় সমাবেশ হয়নি বলে উপস্থিত ভাষা সংগ্রামীদের ভাষ্য। সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলেছিল, যা এক ভাষা উৎসবে রূপ নেয়। সেদিন সে চত্বরে ’৫২ প্রজন্ম-নতুন প্রজন্ম মিলেমিশে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সেদিন আমরা ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলাম। নানা বৈচিত্র্য নিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় কবি বেগম সুফিয়া কামাল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা অধ্যাপক এম এ মাজেদ, বায়ান্নর শহীদ শফিউরের স্ত্রী আকলিমা খাতুন, একাত্তরের শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, নব্বইয়ের শহীদ ডাঃ মিলনের মা মিসেস সেলিনা আখতার। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছিলেন ভাষা সংগ্রামী আহেমদ রফিক। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীউল হক, বদরুদ্দিন উমর, ড. আনিসুজ্জামান, কবি শামসুর রাহমান, আমেরিকা প্রবাসী চিকিৎসক আলমগীর, ’৫২ এর ঢামেক ছাত্র সংসদের জিএস ডাঃ শারফুদ্দিন, অধ্যক্ষ অধ্যাপক কবিরুদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক শাহজাহান নুরুস সামাদ চৌধুরী, ডাঃ সাইদ হায়দার, শহীদ মিনারের প্রথম নকশাকারী ডাঃ বদরুল আলমের স্ত্রী ডাঃ আফযালুন্নেসা, ডাঃ হুমায়ুন হাই, নাট্যজন আতাউর রহমান, অর্থনীতিবিদ আতিউর রহমান, পান্না কায়সার, শহীদ জায়া শ্যামলি নাসরিন চৌধুরী, সঙ্গীত শিল্পী আবদুল লতিফ, দোদুল আহমেদসহ অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি। ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে আকাক্সক্ষা ও স্বপ্নের কথা বলে আবেগময় বক্তব্য দেন আবুল হাসনাত মিল্টন ও ইশতিয়াক মান্নান। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আবেগতাড়িত ভাষাসৈনিকগণ। বায়ান্নের সহযাত্রীদের দেখা পেয়ে ফিরে তারা গেছেন সেই বায়ান্নর স্মৃতিবিজড়িত ঐতিহাসিক সময়ে। সভাপতিত্ব করেছিলেন ভাষা সংগ্রামী অধ্যাপক একেএম আবদুস সালাম। কবিতা আবৃতি করেছিলেন অভিনেত্রী ডাঃ তামান্না, অভিনেত্রী শমী কায়সার ও ডাঃ মনজুর। ভাষাসৈনিক, বরেণ্য চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মেডিক্যাল চত্বর। আলোচনায় সকল বক্তাই ’৫২ তে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। সেদিন কলেজের এনাটমি বিভাগের পাশে উদ্বোধন করা হয়েছিল ‘ভাষা আন্দোলন জাদুঘর’। ’৫২-এর আমতলায় নতুন করে রোপণ করা হয়েছিল মৃত সেই আম গাছের স্থলে নতুন আম গাছের চারা। দিনভর আলোচনায় এসেছে ভাষাসৈনিকদের কণ্ঠে ’৫২-এর জলজ্যান্ত ইতিহাস, নানা স্মৃতিচারণ। উঠে এসেছে সেই পুরনো বিতর্ক কার কি ভূমিকা ছিল। নতুন প্রজন্ম আবেগে আপ্লুত হয়েছে বার বার। কবি আসাদ চৌধুরী তাঁর কবিতার বইতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন উপস্থিত সকল ভাষাসৈনিকের।
সমাবেশে যা দাবি করা হয়েছিল : ১) কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাশে ভাষা আন্দোলন জাদুঘর স্থাপন ২) সর্বস্তরে বাংলা চালুর জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ ৩) ভাষা আন্দোলনের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রকল্প গ্রহণ। আমরা ১৯৯১ সালে এ দাবিগুলো সরকারের কাছে উত্থাপন করেছিলাম। এখন পর্যন্ত কতটা কার্যকর হয়েছে দেশের মানুষ তা অবগত নয়।
১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের এক পর্যায়ে বিকেলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের আহ্বানে মওলানা ভাসানির সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। যেখান থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা দেয়া হয়। আন্দোলন দমনে পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকা শহরে মিছিল, সমাবেশ ইত্যাদি বেআইনী ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।
১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি (৮ ফাল্গুন ১৩৫৮) এ আদেশ অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুসংখ্যক ছাত্র ও প্রগতিশীল কিছু রাজনৈতিক কর্মী মিলে বিক্ষোভ মিছিল শুরু করেন। ছাত্ররা একুশে ফেব্রুয়ারি সকালবেলা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং প্রাঙ্গণে ঐতিহাসিক আমতলায় জমায়েত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, যে কোন মূল্যে ১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে। সেই হিসেবে ১০ জন ১০ জন করে গ্রুপে বিভক্ত হয়ে মিছিলসহ ছাত্রছাত্রীরা ১৪৪ ধারা ভাঙার পরিকল্পনা করে। পুলিশের বাধা উপেক্ষা করে বেলা ১২টা নাগাদ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত হয় (যেহেতু এটা প্রাদেশিক পরিষদ ভবনের, বর্তমান জগন্নাথ হলের কাছাকাছি ছিল)। ছাত্ররাই বেশি ছিল সেখানে। ছাত্রদের চেষ্টা ছিল পরিষদ ভবনের সামনে যাওয়া এবং ঘেরাও করা। লক্ষ্য ছিল, পরিষদ প্রস্তাব নেবে বাংলা ভাষার পক্ষে এবং সেটা গণপরিষদে পাস করাবেন। কিন্তু সে পর্যন্ত যাওয়া গেল না পুলিশের শক্ত ব্যারিকেড, প্রবল লাঠিচার্জ এবং টিয়ার গ্যাসের কারণে। বেলা ৩.২০ মিনিটে সরকারী হিসেবে পুলিশ ২৬ রাউন্ড গুলি ছোঁড়ে। মূলত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েতে এবং হোস্টেলের উল্টোদিকে রাস্তার ওপরে পুলিশ গুলি ছোঁড়ে। মিছিলটি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের কাছাকাছি এলে পুলিশ ১৪৪ ধারা অবমাননার অজুহাতে আন্দোলনকারীদের ওপর গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে নিহত হন বাদামতলী কমার্শিয়াাল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক, সালাম, এমএ ক্লাসের ছাত্র বরকত ও আব্দুল জব্বারসহ অনেকে। ১৭ জন যুবক আহত হন। শহীদদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে ওঠে রাজপথ। শোকাবহ এ ঘটনার অভিঘাতে সমগ্র পূর্ব বাংলায় তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা- শোভাযাত্রাসহকারে ভঙ্গ করে ১৪৪ ধারা। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান শফিক, রিক্সাচালক আউয়াল এবং অলিউল্লাহ নামক এক কিশোর। ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি মেডিক্যাল ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহীদ মিনার, যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন দৈনিক আজাদ পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন।
ক্রমবর্ধমান গণআন্দোলনের মুখে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গৃহীত হয়। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হলে ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লিখিত হয়।
এত ত্যাগের বিনিময়ে আমাদের মায়ের ভাষার অর্জিত অধিকার এখনও সর্বস্তরে চালু হয়নি। তবে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই নানা সরকারী আদেশ হয়েছে। কিন্তু কার্যকর কতটা হয়েছে সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। কেন বাস্তবায়ন হচ্ছে না, সে বিষয়গুলো চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পদ্মা-মেঘনা-যমুনা যেমন আমাদের ঠিকানা, তেমনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত ২৪ বছর আমাদের আন্দোলন-সংগ্রাম-ত্যাগ-সংস্কৃতি সাফল্য আমাদের স্বাধীনতার ঠিকানা। ’৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে কিভাবে আমরা ধাপে ধাপে মুক্তিযুদ্ধে পৌঁছে গেলাম এবং স্বাধীনতা অর্জন করলাম, এর পুরো ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে হবে। যার ভিত্তিতে তারা এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামীর বাংলাদেশে। তাই আজ আবার দাবি তুলতে চাই-
১) সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর কার্যকর পদক্ষেপ চাই।
২) ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস একটি প্রকল্পের মাধ্যমে দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।
৩) সরকারের পাশাপাশি জনগণকে এসব বিষয়ে উদ্যোগী ও সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।
৪) নানা সভা-সমাবেশ-আলোচনার মাধ্যমে নিরন্তর নতুন প্রজন্মের কাছে ভাষা আন্দোলন-স্বাধীনতার ইতিহাস তুলে ধরতে হবে।
আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অবশ্যই বাংলা ভাষা সর্বস্তরে চালু হবে এবং দ্রুতই প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের আত্মপরিচয়।
লেখক : সাবেক উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়








