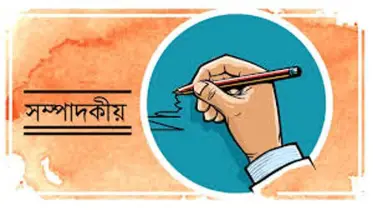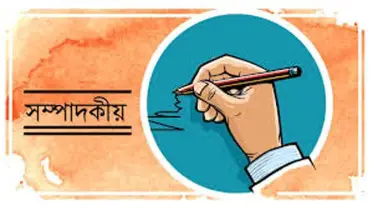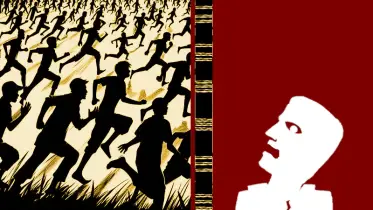বাংলাদেশ গত কয়েক দশক ধরে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, তবে এর পাশাপাশি আয় বৈষম্যের মতো দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাও প্রকট হয়েছে, যার প্রমাণ বৈষম্য নির্দেশকারী গিনিসহগের ক্রমাগত বৃদ্ধি; ১৯৭৩ সালে ছিল ০.৩৬, ২০১০ সালে ০.৪৫৮, ২০১৬ সালে ০.৪৮২, ২০২২ সালে ০.৪৯৯ এবং ২০২৪ সালে নিশ্চিতভাবেই ০.৫-এর উপরে (০ অর্থ সবার আয় সমান এবং ১ সম্পূর্ণ বৈষম্য)। নৈতিক অর্থনীতি শাস্ত্রের দৃষ্টিতে এই অবস্থায় যে কোনো সভ্য সমাজে ধনীদের ওপর উচ্চহারে করারোপ অতি আবশ্যক। কিন্তু যে দেশে মোট আয়ের ৪১ শতাংশ ধনী ১০ শতাংশ পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত এবং আইন প্রণয়ন ও রাজনীতিতে ৭০ শতাংশ ব্যবসায়ীর উপস্থিতিতে রাজনীতি করাই একটি পেশা হয়ে যায়, সে দেশে সরকার-আমলা-রাজনীতিবিদ সবাই-ই যে ধনীদের তোষামোদ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। এসব সত্ত্বেও অনেকের আশা ছিল, জুলাই অভ্যুত্থানে বিপুলসংখ্যক শিশু-কিশোর-তরুণের প্রাণ বিসর্জনসৃষ্ট অন্তর্বর্তী সরকার হয়তো ভিন্নপথে হাঁটবে। বালাই সার, অন্তর্বর্তী সরকার উল্টো স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রথম (আসন্ন ২০২৫-২৬ অর্থবছর) বাজেটের অপেক্ষাকৃত ছোট করে ইতিহাস তৈরির কথা ভাবছে, যা আবার প্রতিদিন গণমাধ্যম আলো করে রাখা থিংকট্যাংকের (বিশ^ব্যাংক-আইএমএফ-সরকারি বড় চাঁদাপ্রাপ্ত) অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও রাজনীতিবিদ শ্রেণি সাধুবাদ জানাচ্ছে। এই অবস্থা আসলে বাংলাদেশে গেঁড়ে বসা স্বজনতুষ্টি রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অথচ ২০০ বছর অপেক্ষার পর একবার পাওয়া জনমিতিক লভ্যাংশের সর্বোচ্চ ব্যবহার (শেষ হবে ২০২৩-৪০ সময়কালে, প্রবীণ জনগোষ্ঠী ২০৪০ ও ২০৫০ সালে যথাক্রমে ১৫ ও ২২ শতাংশ), বৃহৎ ভোক্তাবাজারের চাহিদা পূরণ (২০২২ সালে বিশে^র ১৭তম, ২০৩০ সালে ৯ম), অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তন (তৈরি পোশাক রপ্তানি-রেমিটেন্সে অতিরিক্ত নির্ভরতা, উৎপাদন বৈচিত্র্যের অভাব এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও ভঙ্গুর), সামাজিক স্থিতিশীলতা (উচ্চ বৈষম্যে অবক্ষয়ক্লিষ্ট) এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা সক্ষমতা (২০২৪ সালে ১২৮ দেশের মধ্যে ১০৬তম, উদ্ভাবনে ১৩৩ দেশের মধ্যে ১০৬তম) অর্জন- এই পাঁচটি মূল ক্ষেত্রেই বড় অংকের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য। বিশে^র ধনী দেশগুলো তাদের উন্নতির প্রাথমিক স্তরে বার্ষিক বাজেট প্রণয়নে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন এবং দীর্ঘমেয়াদি সমৃদ্ধি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে ধনীদের কাছ থেকে উচ্চ কর আদায় করেছে। এমনকি এখনো শীর্ষ ১০ শতাংশ আয়কারী যুক্তরাষ্ট্রের মোট ফেডারেল করের ৬০ শতাংশের বেশি এবং আয়করের ৭২ শতাংশ প্রদান করে, যা সময়ের সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে।
রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় ও বৃহৎ বাজেট প্রণয়নে ধনিক শ্রেণির তীব্র বাধা দেওয়ার অনেক কারণ রয়েছে, যার সবই অন্যায়-অন্যায্য। রাষ্ট্র ও সরকার ধনিক শ্রেণির এসব বাধার কথা ফলাও করে স্বীকারও করে। যেমন জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়েই অর্থমন্ত্রী বলেন, ‘বাংলাদেশে বর্তমানে সম্পদ কর আইন কার্যকর নেই। ... আমরা পর্যালোচনা করে দেখেছি অনেক বিত্তশালী করদাতার বিপুল পরিমাণ সম্পদ রয়েছে। কিন্তু তারা তেমন কোনো আয় প্রদর্শন করেন না। ফলে প্রদেয় আয়কর কম হওয়ায় তাদের তেমন কোনো সারচার্জও প্রদান করতে হয় না।’ (২০১৯-২০ বাজেট বক্তৃতা, সমতা ও ন্যায্যতা, অনুচ্ছেদ ২২১, পৃ. ৮০-৮১)। ধনীদের এসব অপকর্ম সরকারের মেনে নিয়ে বাস্তবায়ন করে দরিদ্র শ্রেণিমুখী কর কাঠামো ও আইন করে ব্যবসায়ীদের মুনাফা সুরক্ষার মাধ্যমে এবং ধনী-গরিবকে একই পাল্লায় রেখে ভ্যাট আদায়ের মাধ্যমে। বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণি, বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্প, ওষুধ শিল্প এবং ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতের মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলো এমন বাজেট প্রস্তাব বিরোধিতা করে, যা তাদের করের বোঝা বৃদ্ধি করে সদা-সর্বদা মুনাফায় হ্রাস টানে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে যখন তৈরি পোশাক খাতে করপোরেট কর ১৫-১৮ শতাংশ করার প্রস্তাব করা হয়, তখন একসঙ্গে বিজিএমইএ-বিকেএমইএ তেলেবেগুনে জ¦লে উঠেছিল। শেষে সরকার নতি স্বীকার করে করের হার কমিয়ে দেয়। এরাই আবার এখন আসন্ন বাজেটেও কৌশলগত আর্থিক সুবিধা, উৎপাদন-রপ্তানির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য পণ্য ও পরিষেবার বিবেচনায় সম্পূর্ণ ভ্যাট অব্যাহতিসহ নানা সুবিধা চেয়েছে। একইভাবে ওষুধ খাত স্থানীয় উৎপাদনের ওপর নির্ভরশীল হলেও ধনী ফার্মা ব্যবসায়ীরা কর ছাড় ও মুনাফা সুরক্ষার দাবিতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে। আবার ব্যাংকিং খাতের বেশির ভাগ মালিক রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী, যারা চান না যে বড় বাজেটের জন্য ব্যাংকিং খাতে কর বৃদ্ধি বা কঠোর আর্থিক নিয়ম ও সীমা আরোপ করা হোক। আসন্ন বাজেটের আগে তারা ইতোমধ্যেই বলে রেখেছে, দেশের ব্যাংকিং খাত ইতোমধ্যেই বিপুল খেলাপি ঋণ ও অনিয়মের জর্জরিত। তাই কর বৃদ্ধি করা যাবে না।
ধনিক শ্রেণির বৃহৎ বাজেটের বিরোধিতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সম্পদ পুনর্বণ্টনের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধ। ধনী গোষ্ঠীগুলো আশঙ্কা করে যে বৃহৎ বাজেট যদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কল্যাণে ব্যয় হয়, তাহলে সম্পদ পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক প্রভাব হ্রাস পাবে। তারা আরও মনে করে যে বড় বাজেট সাধারণত অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সুরক্ষা খাতে ব্যয়িত হয়, যা বাজারে রাষ্ট্রের প্রভাব বাড়ায় এবং বেসরকারি খাতের সুযোগ সীমিত করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন দীর্ঘমেয়াদে ধনী ব্যবসায়ীদের রাজনৈতিক প্রভাবও কমিয়ে দিতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে যখন গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বড় বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছিল, তখন প্রভাবশালী ঠিকাদার ও নির্মাণ খাতের ব্যবসায়ীরা নিয়ন্ত্রণ হারানোর আশঙ্কায় এর তীব্র বিরোধিতা করেছিল। আবার বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান আয় ও সম্পদের বৈষম্য এই আশঙ্কাকে আরও বাড়িয়ে তোলে যে বৃহৎ বাজেট বৈষম্য কমাতে সহায়ক হতে পারে, যা ধনিক শ্রেণির স্বার্থের পরিপন্থি। এই যুক্তির অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. আবুল বারাকাতের জাতীয় সংসদ থেকে সংগ্রহ করা বাজেট দলিলের ওপর গবেষণায়, যেখানে তিনি দেখেছেন, বিগত ৫০ বছরে উন্নয়ন বাজেটের আওতায় বরাদ্দকৃত মোট প্রকল্প-কর্মসূচির সংখ্যা ছিল ১,০৬,৫৩৫টি। এসব উন্নয়ন প্রকল্প-কর্মসূচিতে দেশের মোট জনসংখ্যার ৪৭.৬৩ শতাংশ প্রতিনিধিত্বকারী পারিবারিক কৃষির মানুষের ন্যায্য হিস্যার ৮০ শতাংশ ধনিক শ্রেণি আত্মসাৎ করেছে, দিয়েছে ২০ শতাংশ দিয়েছে (বৈষম্যমাত্রা ৪০৩.৩৫ শতাংশ); আদিবাসী মানুষ মোট জনসংখ্যার ২.৯৪ শতাংশ (সরকারি হিসাবে ১ শতাংশের কম) বরাদ্দ হয়েছে মোট বাজেটের বড়জোর ১.৬৭ শতাংশ (৬৩ শতাংশই অনুন্নয়ন বরাদ্দ, বৈষম্যমাত্রা ৩৭৬ শতাংশ); মোট জনসংখ্যার ৮২.৭ শতাংশ গ্রাম-শহরের দরিদ্র-বিত্তহীন-নিম্নবিত্তের কৃষি-ভূমি-জলা সংস্কারউদ্দিষ্ট মানুষের জন্য বরাদ্দ হয়েছে মাত্র ০.২৭ (বঞ্চনামাত্রা ৩০,৭৬৩ শতাংশ)।
স্বজনদের তুষ্ট পুঁজিবাদ বা ক্রনি ক্যাপিটালিজমের প্রভাবও বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণির বৃহৎ বাজেটের বিরোধিতার অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ৯০ শতাংশ সংসদ সদস্য ও রাজনীতিবিদই প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ব্যবসায়ী। ১০ শতাংশ অন্যান্য পেশার হলেও তারাও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা নিয়ে চলেন। এ রকম প্রেক্ষাপটে আইন প্রণয়ন ও নীতিনির্ধারণে ব্যবসায়ীদের স্বার্থকে সবাই অগ্রাধিকার দেয়। আবার রাজনৈতিক দলগুলোও নির্বাচনী তহবিল সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন খাতের ধনিক শ্রেণির চাঁদাবাজি-বখরার ওপর নির্ভরশীল, যা বড় বাজেট প্রণয়নে বাধা সৃষ্টি করে। এজন্যই বাজেট প্রণয়নে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলো সরকারি প্রকল্প, আমদানি শুল্ক ছাড় ও ঋণ সুবিধার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি মুনাফা নিশ্চিত করতে চায়। মুদ্রাস্ফীতি ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার ভয়ও ধনিক শ্রেণির বৃহৎ বাজেটের বিরোধিতার আরেকটি কারণ। তারা আশঙ্কা করে যে বড় বাজেটের ফলে বাজারে অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে তাদের সম্পদের মূল্য হ্রাস পাবে এবং বৃহৎ প্রকল্প ও সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি অর্থায়নের জন্য সরকার বৈদেশিক ঋণ নিলে মুদ্রা বিনিময় হারে চাপ বাড়বে, যা ব্যবসায়ীদের মুনাফা কমিয়ে দেবে। আসলে ক্রনি ক্যাপিটালিজম এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে, যেখানে ব্যবসায়িক সাফল্যে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার পরিবর্তে রাজনৈতিক সংযোগ-অনুগ্রহ জরুরি। এখানে ব্যবসায়ী-রাজনীতিবিদ-আমলা সীমাহীন ভোগবাদী লোভের সমস্বার্থের বৃত্তে বন্দি।
বাংলাদেশে সম্পদ পুনর্বণ্টন এবং কর ব্যবস্থা সংস্কারের প্রচেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে শক্তিশালী ধনিক শ্রেণি এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এই প্রতিরোধ মূলত আর্থিক সুবিধা, রাজনৈতিক প্রভাব এবং ক্ষমতার ভারসাম্য সংরক্ষণের জন্য হয়ে থাকে। সম্পদশালী ব্যক্তিরা তাদের কর দায় এড়াতে কর ফাঁকি, কর অব্যাহতি এবং আইনি ফাঁকফোকরের সুবিধা গ্রহণ করে থাকে। অথচ ধনী ও দরিদ্র দেশের বার্ষিক বাজেটের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায় যে ধনী দেশগুলো সাধারণত তাদের জিডিপির একটি বড় অংশ বাজেটে বরাদ্দ করে এবং তারা আয় ও ভোগের ওপর কর আরোপে নির্ভরশীল, যা দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ খাতে অনেক বেশি সম্পদ ব্যয় করে। ধনী দেশগুলোতে প্রায়ই একটি প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিপরীতে, দরিদ্র দেশগুলো তাদের জিডিপির একটি ছোট অংশ বাজেটে বরাদ্দ করে এবং তারা শুল্ক ও অ-কর রাজস্বের ওপর বেশি নির্ভরশীল।
উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশে ধনিক শ্রেণি ও রাজনৈতিক দলগুলোর বৃহৎ বাজেটের বিরোধিতা একটি জটিল বিষয়, যা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। মুনাফা সুরক্ষা, সম্পদ পুনর্বণ্টনের বিরোধিতা, ক্রনি ক্যাপিটালিজমের প্রভাব এবং অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতার ভয় ধনিক শ্রেণির বাজেট বিরোধিতায় অবদান রাখে। কিন্তু ধনিক শ্রেণির তো বোঝা উচিত, ২০৩০ সালে তাদের লুটপাটের এই ভূমি বিশে^র নবম বৃহত্তম ভোক্তাবাজারে পরিণত হবে, যেখানে ঐতিহাসিক জনমিতিক লভ্যাংশ ধীরে ধীরে অস্তাচলগামী। কয়েকটি বছর ধরে বড় অঙ্কের বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করলে উৎপাদনশীল কর্মশক্তিতে ভরপুর মোট জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশের যদি আয়-রোজগার বাড়ে, তাহলে তাদের মুনাফার পাল্লায়ও ভারী হবে। এই জনমিতিক সুবিধা ব্যবহার করে উচ্চ কর্মসংস্থান ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি না করা হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যখন ধনী দেশে ধনিক শ্রেণির গোলামি করবে, তখন বাংলাদেশের ধনিক শ্রেণি ধনী দেশের নাগরিক হলেও সেখানে তৃতীয় শ্রেণির মর্যাদাই পাবে। তা ছাড়া বিশ^জুড়ে হোয়াইট সুপ্রিমেসি ও বর্ণবাদী মনোভাব তীব্রভাবে ছড়িয়ে পড়ার যুগে যদি বড় বাজেট দিয়ে বাংলাদেশের দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষা, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্য খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করা যায়, পাশাপাশি দেশের ভোক্তাবাজারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য অবকাঠামো ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ বাড়ানো যায়, তাহলে স্থানীয় উৎপাদন ও শিল্পায়নের প্রসার ধনিক শ্রেণির আয়-উন্নতিতেও সহায়ক হবে। বৃহৎ বাজেট দিয়ে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আর্থিক স্থিতিশীলতা আনা গেলে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ হবে, যা দীর্ঘমেয়াদে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী করবে; যার বড় অংশই ধনিক শ্রেণির পরবর্তী প্রজন্মগুলোরই হস্তগত হবে। শিল্প, কৃষি ও সেবা খাতে বৈচিত্র্য আনা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও ডিজিটাল অর্থনীতির উন্নয়ন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা গেলে বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেলেও ধন-সম্পদে অনেক এগিয়ে থাকার সুবাদে তেলঝোলে থাকা ধনিক শ্রেণির আর্থিক সক্ষমতাও অনেক অনেক বাড়বে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল