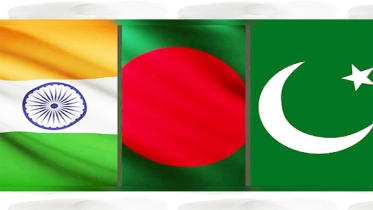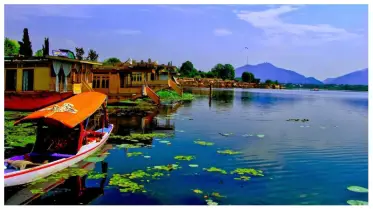এবারও মে দিবসের আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংগ্রামের দীর্ঘশ্বাস যেন আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়ে উঠছে। বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি ও বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েনের পটভূমিতে এবারের মে দিবস শুধুই প্রতীকী আনুষ্ঠানিকতার দিন নয়, বরং শ্রমিকের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর আত্মজিজ্ঞাসার ও পুনর্বিবেচনার এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। আর এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে মূল্যস্ফীতি ১০ শতাংশের কাছাকাছি, অথচ আয় বৃদ্ধির হার ৪-৫ শতাংশ। এই চিত্র শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার অসহায়ত্ব ও বেদনাই তুলে ধরছে। ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের এক জরিপে দেখা গেছে, শ্রমিকদের প্রায় ৭০ শতাংশ মনে করেন যে, বর্তমান মজুরি দিয়ে মাসের শেষ পর্যন্ত চলা সম্ভব নয়। এর মধ্যে আবার বেকারত্বের হারও উচ্চ এবং সরকারের স্বীকৃতি ছাড়াই গড়ে ওঠা অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যা মোট শ্রমশক্তির ৮৫ শতাংশেরও বেশি। এমন এক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, সামাজিক নিরাপত্তা ও কর্মস্থলের নিরাপত্তা দুরাশা। এখানে হাতেগোনা সৎ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের কর্মক্ষেত্রে কর্মরর্ত লোক ছাড়াই যে কোনো শ্রমপেশার শ্রমিক জীবিকা নির্বাহের জন্য বাধ্য হয়ে অতিরিক্ত কাজ খোঁজে। কিন্তু কাজের অভাব ও কম মজুরি তাদের জীবনকে শুধু অনিশ্চিতই করে তুলছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ জীবনটাকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়ে অনির্দিষ্ট যাত্রায় শামিল হচ্ছে। প্রকৃত অর্থে বাংলাদেশে শ্রমিকজীবন কার্যত ক্রমবর্ধমান মুনাফাকামী নিয়োগকর্তা, ক্রমহ্রাসমান মুদ্রা মূল্যমান ও আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি অর্থ ব্যবস্থার চিরস্থায়ী নিষ্পেষণে দলিত-মথিত হচ্ছে, যেখানে জীবনধারণই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরও বাংলাদেশের চিত্র এমন হওয়ার কথা নয়।
বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের পথে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেও সমাজের গভীরে প্রোথিত কিছু সমস্যা আমাদের অগ্রযাত্রাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। সব শ্রেণি-পেশার শ্রমজীবী মানুষের জীবনে বহুমাত্রিক সংকট থাকলেও বিভিন্ন গবেষণা ও সংস্থার প্রতিবেদন মূলত তিনটি জ্বলন্ত সমস্যার ভয়াবহতা ও ব্যাপকতা আমাদের সবার জন্যই উদ্বেগজনক, যার মধ্যে রয়েছে শিশু শ্রমিকের অমানবিক জীবন, শ্রমজীবী নারীদের প্রতি অব্যাহত বৈষম্য-বঞ্চনা-অবহেলা এবং অভিবাসী শ্রমজীবীদের দুর্ভাগ্যলিপি। এই তিন অঙ্গনের করুণ চিত্র সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের স্পষ্টতম প্রতিফলন। কেননা দারিদ্র্য, শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিক চাপ বাংলাদেশের শিশু-নারী-অভিবাসীদের অমানবিক এক ব্যবস্থায় উপার্জনে লিপ্ত হতে বাধ্য করছে। শিশুশ্রম নির্মূলে জাতীয় শিশুশ্রম নির্মূল নীতি গ্রহণ করা হলেও তার বাস্তবায়ন এখনো অনেক দূরে। ইউনিসেফ এবং আইএলওর ২০২৪ সালের যৌথ রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের সংখ্যা ১৩ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৮ শতাংশ বেশি। অথচ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (ঝউএ) অনুযায়ী ২০২৫ সালের মধ্যে সকল ধরনের শিশুশ্রম বিলুপ্তির অঙ্গীকার রয়েছে। বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরোর শিশুশ্রম জরিপ (২০২৫) বলছে, দেশের ৫-১৭ বছর বয়সী প্রায় ৬.৮ শতাংশ শিশু কোনো কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত, যাদের ৭৩ শতাংশ ঝুঁকিপূর্ণ পেশায়। সাম্প্রতিক গবেষণা ও মাঠ পর্যায়ের চিত্র বলছে, প্রাতিষ্ঠানিক খাতের বাইরে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত যেমন ছোট কারখানা, ওয়ার্কশপ, হোটেল, রেস্তোরাঁ, গৃহস্থালি কাজ, পরিবহন খাত ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রমিকের সংখ্যা উদ্বেগজনক। পোশাক শিল্পে আন্তর্জাতিক চাপের কারণে শিশুশ্রম কমানোর কিছু সাফল্য থাকলেও অন্যান্য খাতে এটি নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এই শিশুরা কেবল তাদের মৌলিক অধিকার, যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং বিনোদন থেকেই বঞ্চিত নয়, তারা প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হচ্ছে অমানবিক শোষণ ও নির্যাতনের। তাদের কাজের পরিবেশ প্রায়ই অস্বাস্থ্যকর ও বিপজ্জনক। দীর্ঘ কর্মঘণ্টা, অপর্যাপ্ত মজুরি (অনেক ক্ষেত্রে নামমাত্র বা শুধু খাদ্য), শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনাও নতুন নয়। ভারী জিনিস উত্তোলন, ক্ষতিকর রাসায়নিক বা ঝুঁকিপূর্ণ যন্ত্রপাতির সঙ্গে কাজ করার কারণে অনেকেই স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছে এবং দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। আইনের দৃষ্টিতে এটি অপরাধ হলেও নজরদারির অভাব এবং দারিদ্র্যপীড়িত বাস্তবতা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। শিশুশ্রমের মূল কারণ দারিদ্র্য, শিক্ষার সুযোগের অভাব এবং অর্থনৈতিক চাপ। বিশেষ করে কৃষি, নির্মাণ, হোটেল-রেস্তোরাঁ ও গৃহস্থালি কাজে শিশুশ্রম বাড়ছে। এ শিশুদের অধিকাংশই শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থেকে জীবনভর দারিদ্র্যের চক্রে আবদ্ধ হচ্ছে। বাস্তবতা বলছে, শিশুদের শিক্ষায় ফেরাতে এবং তাদের পুনর্বাসনে পরিকল্পিত ও দীর্ঘমেয়াদি উদ্যোগ ছাড়া এ লক্ষ্য অর্জন অসম্ভব হবে। সস্তা শ্রমের সহজলভ্যতা কিছু অসাধু নিয়োগকর্তাকে শিশুশ্রম ব্যবহারে উৎসাহিত করছে। কাক্সিক্ষত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জন করতে হলে এই বিশাল সংখ্যক অধিকারবঞ্চিত শিশুকে শিক্ষার আলোয় ফিরিয়ে এনে মূলধারায় যুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।
বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী শ্রমিকদের অবদান অনস্বীকার্য। পোশাক শিল্প থেকে শুরু করে কৃষি, নির্মাণ, গৃহস্থালি কাজ, অভিবাসন সব ক্ষেত্রেই নারীরা শ্রম দিচ্ছেন এবং দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, তাদের এ অবদান প্রায়ই স্বীকৃতি পায় না এবং তারা প্রতিনিয়ত নানারকম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হন। নারী শ্রমিকদের বঞ্চনা ও নিগ্রহ যেন তাদের চিরন্তন ভাগ্যলিপি। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে বাংলাদেশে নারী শ্রমিকরা একই ধরনের কাজ করেও পুরুষের তুলনায় গড়ে ২২-৩০ শতাংশ কম মজুরি পান, ক্ষেত্রবিশেষে আরও বেশি হতে পারে। বিশেষ করে কৃষি, গৃহস্থালি এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প খাতে এই বৈষম্য আরও প্রকট। উদাহরণস্বরূপ নারী কৃষি শ্রমিকের দৈনিক মজুরি পুরুষের তুলনায় প্রায় ২৫ শতাংশ কম। পাশাপাশি মাতৃত্বকালীন ছুটি, কর্মস্থলে স্যানিটেশন, নিরাপত্তা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধের মতো মৌলিক অধিকার নিশ্চিত না হওয়ায় নারী শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। শ্রমদানে ইচ্ছুক নারীর শ্রমের এমন অবমূল্যায়ন আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে গেছে। মজুরি বৈষম্যের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নারীরা প্রায়শই নিরাপত্তাহীনতা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের সম্মুখীন হন। শারীরিক ও মৌখিক হয়রানি, এমনকি যৌন হয়রানির শিকার হওয়ার ঘটনাও ঘটে। চাকরির অনিশ্চয়তা এবং সুযোগ-সুবিধার অভাব তাদের জীবনকে আরও কঠিন করে তোলে। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে কিছুটা উন্নতি হলেও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের বিশাল সংখ্যক নারী শ্রমিক কার্যত কোনো আইনি সুরক্ষা বা সামাজিক নিরাপত্তার আওতায় আসেন না। নারীর প্রতি সমাজের সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গি এবং লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন এই বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে। নীতিনির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় নারীদের পর্যাপ্ত প্রতিনিধিত্ব নেই।
শ্রমিকদের জীবনের ক্রমবর্ধমান সংকট নিরসনে কেবলমাত্র স্লোগান নয়, প্রয়োজন বাস্তবিক পদক্ষেপ। পুঁজিবাদী বিশ^ ও সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শোষণ এবং বঞ্চনা আবশ্যিক ও চিরন্তন হলেও রাষ্ট্র ও সমাজের নীতিনির্ধারকদের কিছু দায় আছে, যার মাধ্যমে শ্রমিকদের ক্রমবর্ধামন শোষণ ও বঞ্চনাধারার হ্রাস কিছুটা টেনে ধরা সম্ভব। এজন্য বাংলাদেশকে প্রথমেই রাষ্ট্রের মজুরি বোর্ডকে মূল্যস্ফীতি অনুযায়ী ন্যূনতম মজুরি সমন্বয় করতে হবে, শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় ২০০৬ সালের শ্রম আইন এবং পরবর্তী সংশোধনীগুলো বাস্তবায়নে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে, কর্মের সংস্থান ও শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিশুশ্রম রোধ ও ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুদের রক্ষা করতে হবে, নারী শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য ও পুরুষদের সমপর্যায়ের বেতনসহ নিরাপদ কর্মপরিবেশ- পৃথক স্যানিটেশন, মাতৃত্বকালীন সুবিধা এবং যৌন হয়রানি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে, বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রীয় দূতাবাসগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে এবং বিদেশগমন প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে হবে, ভবিষ্যতের চাকরির বাজারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ও কারিগরি প্রশিক্ষণ বাড়াতে হবে, জাতীয় বাজেটে শ্রমিকদের কল্যাণে বরাদ্দ বৃদ্ধি নিশ্চিত করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শক্তিশালী করতে হবে।
লেখক : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
প্যানেল