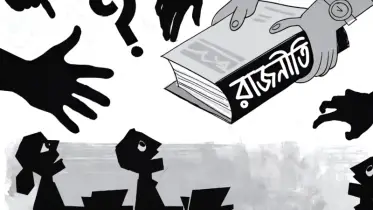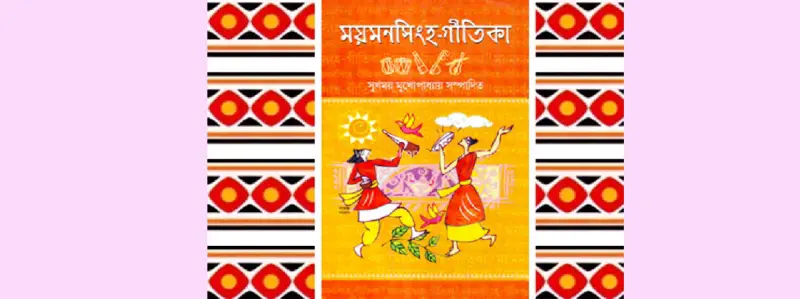
.
জারি-সারি, ভাটিয়ালি, পুঁথি-পালাগানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। তেমনি এক গৌরবগাথা সংকলন ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’। ২০২৩ সালে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে। সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন ১৯২৩ সালের ২৪ নভেম্বর এই গীতিকার সম্পাদকীয় লেখেন বলে সেই দিনটিকে প্রকাশের শতবর্ষ উদ্যাপিত হলো। বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলা বিশেষ করে গারো পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রবাহিত হাওড়াঞ্চলের জীবনের ১০টি পালা দিয়ে সাজানো হয়েছে এ গীতিকা। দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত সংকলনে ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’র জন্ম। যার মাধ্যমে বিশ্ববাসী প্রথম জানতে পেরেছে বাংলার লোকজ সংস্কৃতির গৌরবময় ইতিহাস। দীনেশচন্দ্র সেনের পূর্ববঙ্গ গীতিকার চারটি খন্ডের প্রথম খন্ডটি ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’। ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দীনেশ সেন সম্পাদিত গীতিকাটি প্রকাশ করে। এরপর গীতিকাটি পূর্ববঙ্গ গীতিকাতেও সংযুক্ত হয়।
নেত্রকোণা, দুর্গাপুর, গারো পাহাড়, কিশোরগঞ্জ, বাজিতপুর, খালিয়াজুরি ও কেন্দুয়ার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে ঘুরে চন্দ্রকুমার দে পালাকার, বয়াতি, মাঝিমাল্লার কাছ থেকে ঘটনা সংবলিত পালাগুলো সংগ্রহ করেন। মানুষের মুখে মুখে রচিত এসব কাব্যপালা সংগ্রহ করে জনসম্মুখে তুলে ধরার মৌলিক কৃতিত্বটাও চন্দ্রকুমার দে’র। সেটি দীনেশ চন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন ‘সৌরভ’ পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯১৩ খ্রি: অব্দে ময়মনসিংহের পত্রিকা সৌরভে চন্দ্রাবতী (প্রাচীন মহিলা কবি) সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখেন চন্দ্রকুমার দে। সেটি পড়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি দীনেশ চন্দ্র সেন। সেই সূত্র ধরে তিনি খুঁজতে থাকেন চন্দ্র কুমারকে । পুরনো বন্ধু কেদারনাথের সহযোগিতায় এক সময় তাকে পেয়েও যান। অসুস্থ চন্দ্রকুমারের চিকিৎসার ভার নিজেই বহন করলেন। সুস্থ হয়ে উঠলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে লাগিয়ে দেন গাথা সংগ্রহের কাজে। নেত্রকোণা জেলার কেন্দুয়ার চন্দ্রকুমারের অবদানের কথা স্মরণ করতে গিয়ে শ্রী দীনেশচন্দ্র সেন মৈমনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় বলেন, ‘কি কষ্টে যে এই সকল পল্লীগাথা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি ও তাঁহার ভগবানই জানেন এবং কতক আমি জানিয়াছি। এই সকল গান অধিকাংশ চাষাদের রচনা। এইগুলির অনেক পালা কখনই লিপিবদ্ধ হয় নাই। পূর্বে যেমন প্রতি বঙ্গপল্লীতে কুন্দ ও গন্ধরাজ ফুটিত, বিল ও পুষ্করিণীতে পদ্ম ও কুমুদের কুঁড়ি বায়ুর সঙ্গে তাল রাখিয়া দুলিত- এই সকল গানও তেমনই লোকের ঘরে ঘরে নিরবধি শোনা যাইত ও তাহদের তানে সরল কৃষকপ্রাণ তন্ময় হইয়া যাইত।’ ধারণা করা হয়, চন্দ্রকুমারের সহযোগিতা না থাকলে হয়তো গাথাগুলো সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়ত। দুঃখ, কষ্ট, নানা দৈন্যদশার সঙ্গে লড়াই করে তিনি সাহিত্যচর্চা করে গেছেন। যার সহযোগিতা না থাকলে কালের আবর্তে হয়তো গ্রামবাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এসব পালাগান অনেক আগেই হারিয়ে যেত।
তার জীবনটাও ছিল দুঃখে ভরা। খুব অল্প বয়সেই মাতৃহারা হন। কৈশোরে গ্রামের জমিদার তার পিতার সহায়সম্পত্তি চোখের সামনে কেড়ে নিলে, পিতা রামকুমার অচিরেই শোকে-দুঃখে পৃথিবীর মায়া কাটান। এরপর পেট বাঁচাতে চন্দ্র নিজগ্রামের মুদি দোকানে ১ টাকা বেতনের চাকরি নেয়। কিন্তু ভাবুক ও সাংসারিক বিষয়াদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ চন্দ্রকে কিছুদিনের মধ্যেই ঐ দোকান থেকে অর্ধচন্দ্র পেতে হয়। দোকানের খাতায় হিসাব-নিকাশের বদলে ছড়া-কবিতা লিখে রাখায় মালিক মহাবিরক্ত হয়ে একদিন বিদায় করে দেন তাকে। এরপর হতভাগা চন্দ্রকুমার কলেরায় আক্রান্ত হন। পরিত্রাণের আশায় হাতুড়ে চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হয়েছিলেন। এতে সুস্থ তো হলেনই না, উপরন্তু মানসিক বৈকল্য দেখা দিল, যা প্রায় দু’বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই চরম দুর্দিনে এক গ্রাম্য জমিদার তাকে মাসিক ২ টাকা বেতনে তহশিল আদায়ের চাকরি দেন। এই চাকরিটিই চন্দ্রের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তহশিল আদায় করতে চন্দ্রকে গ্রাম থেকে গ্রামে ঘুরতে হতো। ঐ সময়ই তিনি কৃষকদের কণ্ঠে শুনতে পান অপূর্ব সব পল্লিগাথা ও উপাখ্যান। গ্রাম-গ্রামান্তর ঘুরে তহশিলের বদলে তিনি লিখে আনতে লাগলেন পল্লির গায়েনদের গাওয়া উপাখ্যান। এসব কারণে একদিন এ চাকরিটিও হারাতে হয় তার। এর কিছুদিন পর ময়মনসিংহ হতে কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘সৌরভ’ পত্রিকায় চন্দ্রনাথ লেখালেখি শুরু করেন। উক্ত পত্রিকায় চন্দ্রকুমার দে’র লোক সাহিত্যের ওপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ সালে সৌরভ পত্রিকায় মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর ওপর প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ পড়ে মুগ্ধ হন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন। তারপর পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের মাধ্যমে চন্দ্রকুমার দে’র সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাকে দিয়ে দিনের পর দিন কষ্টসাধ্য সাধনার মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গীতিকাগুলো সংগ্রহ করান।
উল্লেখ্য, ময়মনসিংহ হতে প্রকাশিত সৌরভ পত্রিকায় পবিত্র কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদকারী গিরিশচন্দ্র সেন, বাংলার স্বভাব কবি গোবিন্দ দাস, চন্দ্রকুমার দে ও সৌরভ কুমার রায়সহ তখনকার সময়ের নামকরা কবি-সাহিত্যিকগণ লিখতেন। উল্লেখ্য, সৌরভ পত্রিকার সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার ছিলেন একজন ইতিহাসবিদ, সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। তিনি সে সময়ে উত্তর-পূর্ববঙ্গের ইতিহাস ও সাহিত্যকে সমগ্র বঙ্গসমাজে পরিচিত করাতে সহায়তা করেছেন। অনেকে পালাগুলোকে পূর্ববাংলার অশিক্ষিত চাষাভূষাদের মাথামু-ু বলে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন হাল ছেড়ে দেননি। তিনি চাষাভুষাদের রচিত এসব কাব্যকথার মাঝেই সাহিত্যের আসল সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। যে কথা উঠে উঠেছে তার নিজমুখে, ‘কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার দর্পে উপেক্ষা করিয়া বলিলেন, ‘ছোটলোকেরা, বিশেষত, মুসলমানেরা, ঐ সকল মাথামুন্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহুভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন? আপনি এই ছেঁড়া পুঁথি ঘাটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।’ ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এসব বুদ্ধিজীবীর আহ্বানে দীনেশচন্দ্র সেন সাড়া দেননি। তিনি বরাবরই ছিলেন উপনিবেশবাদী চিন্তাধারার বিপক্ষে।
গীতিকাটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে দীনেশচন্দ্র সেন আরও বলেন, ‘পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। যে সকল ঘটনা অশ্রুসিক্ত হইয়া লোকেরা শুনিয়াছে, যে সকল অবাধ ও অপ্রতিহত অত্যাচার যমের দুর্জয় চক্রের ন্যায় সরল নিরীহ প্রাণকে পিষিয়া চলিয়া গিয়াছে- সেই সকল অপরূপ করুণ কথা গ্রাম্য কবিরা পয়ারে গাঁথিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা ছন্দের- শব্দৈশ^র্যের কাঙাল হইতে পারেন, তাঁহারা হয়ত বড় বড় তালমানের সন্ধান জানিতেন না, কিন্তু তাঁহাদের হৃদয় অফুরন্ত কারুণ্য ও কবিত্বের উৎসস্বরূপ ছিল। যাঁহারা লিখিয়াছিলেন, তাঁহাদের অশ্রু ফুরাইয়া গিয়াছে, কিন্তু এই সকল কাহিনীর শ্রোতাদের অশ্রু কখনও ফুরাইবে বলিয়া মনে হয় না।’
ড. দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা লোকসাহিত্যে এক অবিস্মরণীয় নাম। ১৮৬৬ সালে ৩ নভেম্বর মানিকগঞ্জ জেলার বগজুরি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বৈদ্যব্রাহ্মণ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ঢাকা জেলার ধামরাই উপজেলার সুয়াপুর গ্রামে। সিলেটের হবিগঞ্জের এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকালে গ্রামবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে প্রাচীন বাংলার পুঁথি সংগ্রহ করেন এবং সেসব উপকরণের সাহায্যে ১৮৯৬ এ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ শিরোনামে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করেন। ১৯১১ সালে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘হিস্ট্রি অব বেঙ্গলি লিটারেচার’ প্রকাশিত হলে তা সর্বমহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। ১৯১৩ সালে কলকাতা বিশ^বিদ্যালয় তাঁকে ‘রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ’ প্রদান করে এবং এরই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি মৈমনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্পাদনা করেন।
১৯২৩ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন মৈমনসিংহ গীতিকা বইটি প্রকাশিত হয়, এ গীতিকার পালাগুলো ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ ভারতবর্ষের সাহিত্য সুধীজনের মাঝে ব্যাপক সমাদৃত হতে থাকে। অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষরা যে এত সুন্দর শিল্প সৃষ্টি করতে পারে, অনেকে তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কোনো কোনো পালাকে তো ইউরোপের জ্ঞানীগুণীরা জনপ্রিয় সাহিত্যগুলোর সঙ্গে তুলনা করেন। গীতিকার মূল্যায়নে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বর্ণনায় উঠে এসেছে সে কথা, ‘ইউরোপের মধ্যযুগীয় রোমান্স ‘ট্রিস্টান ও ইসল্ট’ এবং ‘অকাসিন ও নিকোলেটের’ অমর প্রেমের কাহিনী আজ পৃথিবীর সকল সাহিত্য-রসিকের কাছেই সুপরিচিত। তাদের অবিস্মরণীয় প্রেমের উৎস থেকে, যুগে যুগে সাহিত্যিকগণ পেয়েছেন প্রেরণা- প্রেমিক পেয়েছেন শান্তি। আমাদের মৈমনসিংহ গীতিকার ‘মহুয়া’ পালাটির ইংরেজি অনুবাদ পড়ে ইউরোপের বহু জ্ঞানীগুণী পন্ডিতও পালাটির সঙ্গে উপরে বর্ণিত ইউরোপীয় কাহিনী দু’টির তুলনা করেছেন।’
লেখক : তথ্যপ্রযুক্তিবিদ, কলামিস্ট, দেশের প্রথম ডিজিটাল নিউজ সার্ভিস আবাস-এর চেয়ারম্যান- সাংবাদিক, বিজয় কীবোর্ড ও সফটওয়্যার-এর জনক
[email protected]
www.bijoyekushe.net
www.bijoydigital.com
আনন্দপত্র.বাংলা