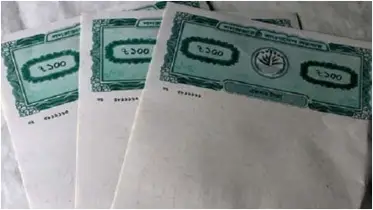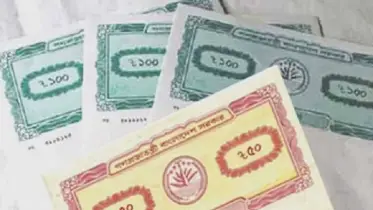ছবি: সংগৃহীত
বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মিথ্যা ও মানহানিকর তথ্য ছড়ানো একটি ভয়াবহ সামাজিক সমস্যা হয়ে উঠেছে। একসময় এই ধরনের অপপ্রচার মৌখিকভাবে বা লিফলেট ছাপিয়ে ছড়ানো হতো। কিন্তু বিগত এক দশকে প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারের ফলে এসব অপরাধ এখন ছড়িয়ে পড়ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে—ফেসবুক, ইউটিউব, এক্স (সাবেক টুইটার), ইনস্টাগ্রামসহ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে।
এইসব অপরাধের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—মিথ্যা তথ্য, বিভ্রান্তিকর বক্তব্য কিংবা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাউকে বা কোনো প্রতিষ্ঠানকে হেয় করার জন্য মানহানিকর কনটেন্ট ছড়িয়ে দেওয়া। অনেকসময় অপরাধীরা ভুয়া আইডি, নাম-পরিচয় গোপন রেখে বা নাম-সদৃশ অ্যাকাউন্ট তৈরি করে এসব কাজ চালায়। তারা মনে করে, যেহেতু এটি ‘ভার্চুয়াল জগত’, তাই তাদের শনাক্ত বা আইনের আওতায় আনা সম্ভব নয়। কিন্তু বাস্তবে বিষয়টি মোটেই তেমন নয়।
বাংলাদেশে মিথ্যা ও মানহানিকর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিকার রয়েছে দীর্ঘদিন ধরেই। দণ্ডবিধি ১৮৬০-এর সংশ্লিষ্ট ধারা এবং পরবর্তীতে প্রণীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এইসব অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার সুযোগ রেখেছে।
তবে ডিজিটাল অপরাধ বেড়ে যাওয়ার প্রেক্ষাপটে সরকার সাইবার সিকিউরিটি আইন ২০২৩ চালু করেছে। এই আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে—
ধারা ২৯: যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট, ফেসবুক, ইউটিউব, ব্লগ বা অন্য কোনো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তবে এটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।
প্রথমবার এই অপরাধে দোষী প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।
অপরাধটি পুনরাবৃত্তি হলে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড এবং ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করা হবে।
ধারা ৩১: যদি কোনো ইলেকট্রনিক কনটেন্ট আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাতে পারে এমন কিছু হয়, তাহলেও এটি অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এই ধারায় সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান রয়েছে।
আইন অনুযায়ী, অপরাধ সংঘটনের সময় যে আইন কার্যকর ছিল, বিচারও সেই আইন অনুসারেই হবে। তাই আগের আইনে দায়ের করা মামলা পুরোনো আইন অনুযায়ীই চলবে।
সাইবার অপরাধের বিস্তার রোধে সচেতনতা ও আইন প্রয়োগ জরুরি। ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এমন কোনো মিথ্যা ও মানহানিকর কনটেন্টের শিকার হন, তাহলে যথাযথ আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম কোনো ‘নিরাপদ গোপন স্থান’ নয়—আইনের হাত সেখানে পৌঁছাতে পারে।
এসএফ