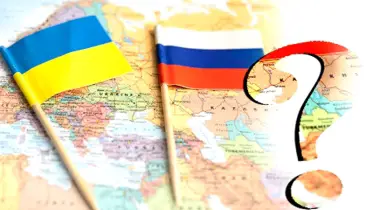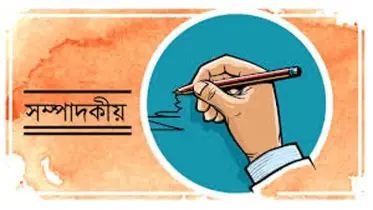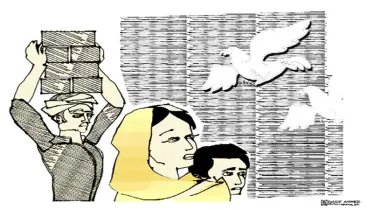শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সার্বিক উন্নয়নকে টেকসই করা যায়। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন বিষয়ে প্রচারের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত কাঠামো, পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনিক নীতিমালা এখনো অস্পষ্ট। উন্নত ও প্রযুক্তিগত গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অগ্রগতির কলাকৌশল প্রণয়নের কেন্দ্রবিন্দুও বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান সৃষ্টি, উদ্ভাবনী চিন্তা-চেতনার বিকাশ মূলত বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন গবেষণা এবং দক্ষ শিক্ষকদের একটি নির্দিষ্ট কাঠামোতে সমন্বিত করে যেভাবে উদ্ভাবন ও উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে, তা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে শিল্পপ্রতিষ্ঠান সংযোগে নতুন পণ্য তৈরি করতে পারে। তা দিয়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিযোগিতামূলক বিশ্ববাজারে টিকে থাকা সহজ হয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগারে যেসব বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সুলভ থাকে না, শিক্ষকরা ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সংযোগের মাধ্যমে সহজেই সেসব ব্যবহার করতে পারেন। এই সরঞ্জাম শিক্ষকদের গবেষণার অতিরিক্ত সুযোগ সৃষ্টি করে, যা দেশের উৎপাদনশীলতায় অবদান রাখে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এ সংযোগের মাধ্যমে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের জন্য ভবিষ্যতের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত দক্ষ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাপ্লিকেশনগুলোতে প্রশিক্ষিত হতে পারেন এবং তারা জাতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কর্মশক্তি হিসেবে অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে পারেন। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স কারিকুলামের ডিজাইন করা উচিত। কারণ, শিল্পপ্রতিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি পাচ্ছে না। তাই বিদেশ থেকে দক্ষ কর্মী নিয়োগ দিতে হয়। আবার বেকারের সংখ্যাও কম নয়। দুই পক্ষের মধ্যে ফারাক রয়েছে, তাই বিশ্ববিদ্যালয়কেই উদ্যোগ নিতে হবে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুসারে জনশক্তি তৈরি করা সময়ের দাবি।
আমাদের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর অনেক গ্র্যাজুয়েটের কারিগরি দক্ষতায় ঘাটতি রয়েছে। ফলে তারা বেকার থেকে যান। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন এবং চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্পপ্রতিষ্ঠানে সংযোগ প্রয়োজন। তাই বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে খুবই দ্রুত দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে, কর্মজীবনের পাশাপাশি জীবনে সফল হওয়ার জন্য সঠিক চিন্তা, যোগ্যতা এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই শিক্ষার্থীদের কীভাবে যোগাযোগে দক্ষতা বাড়ানো যায়, সে বিষয়ে শিক্ষকদের ক্লাসে পড়ানো উচিত। শিক্ষার পুরানো মডেল বাদ দিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে হবে। উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে হতে হবে আদর্শ প্রতিষ্ঠান। এটি নিশ্চিত, শিক্ষার্থীরা আজ সফট স্কিল ছাড়া চাকরির বাজারে বা বিশ্বায়নের যুগে টিকে থাকতে পারবে না।
যেমন- অ্যাকাউন্টিং। এখন আর গতানুগতিক অ্যাকাউন্টিং পড়ালে হবে না। শিক্ষার্থীকে নতুন প্রযুক্তি এবং সফটওয়্যারের সঙ্গে সংযুক্ত করে পাঠদান করতে হবে, যাতে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে একজন আদর্শ হিসাবরক্ষক তৈরি করা যায়। অডিট অ্যাকাউন্টিংয়ের একটি অংশ। উদাহরণস্বরূপ, একটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কোম্পানির অডিট করতে একজন অডিটর লেনদেনের স্কেল এবং সব জটিল বিষয়ে মানিয়ে নিতে পারেন না। অর্থপূর্ণ অডিটের ফল নিশ্চিত করতে সফটওয়্যার প্রোগ্রাম ব্যবহার করতে হবে। ব্যবসার এই নতুন ভাষা বোঝা, পরিমাপ করা, রিপোর্ট করা- এসব অনুষঙ্গে হিসাবরক্ষক বা অডিটরকে উন্নত প্রযুক্তিগুলো গ্রহণ করতে হবে। এভাবে অন্যান্য ডিসিপ্লিনে আমাদের শিক্ষার্থীদের গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে টিকে থাকা কঠিন হবে। উচ্চশিক্ষায় ভাবতে হবে, যাতে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের সময় আমাদের অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জিত হয়।
দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা হলো শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখানে দক্ষতা বা যোগ্যতা অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়। যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষা পরিমাপ করে, শিক্ষার্থী আসলে কতটুকু শিখেছে; শ্রেণিকক্ষে কতটা সময় ব্যয় করা হয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটা স্পষ্ট, এক ক্রেডিট সমান ১৪ বা ১৫ ঘণ্টার পুরানো সংজ্ঞা এখন আর তত কার্যকর নয়। অধিকন্তু যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষায় পৃথক শিক্ষার্থীর ওপর আলাদাভাবে দৃষ্টি দিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব গতিতে শিখতে, লক্ষ্যযুক্ত জ্ঞান এবং দক্ষতা আয়ত্ত করতে যতটা সময় লাগে, শিক্ষকদের ততটা কার্যকরী সময় দিতে হবে।
পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বিশ্ব এখন অর্থনীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিচ্ছে। যেমন- একজন নিয়োগকর্তা জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে সফ্ট স্কিল কী আছে, সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। চাকরিপ্রার্থী কতটুকু নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে জানেন বা ব্যবহার করতে দক্ষতা সেখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বাজারের পরিবর্তিত চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সাড়া দিতে হবে। যেমন- নিয়োগকর্তারা তাদের প্রতিষ্ঠানে এমন লোক চান, যারা যে কোনো পরিস্থিতি মানিয়ে নিতে পারে। তাই আমেরিকান ম্যানেজমেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের পরামর্শ অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যেসব দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তা হলো ৪ সি (ঈ)-কমিউনিকেশন, কোলাবরেশন, ক্রিয়েটিভিটি এবং ক্রিটিকাল থিংকিং। উচ্চশিক্ষায় এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে। সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কোর্স কারিকুলাম ঢেলে সাজাতে হবে। উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দুই শ্রেণিতে ভাগ করা উচিত, যার মধ্যে কিছু থাকবে শুধু গবেষণাভিত্তিক। আর অন্যগুলো হবে অ-গবেষণাভিত্তিক, যেখানে তাত্ত্বিক পড়াশোনা করিয়ে সনদ প্রদান করবে। গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সব কোর্স চালু করতে পারবে না। এ বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। যার ফলে, শিক্ষায় গবেষণা কাজকর্মের মান বাড়বে এবং ইতিবাচক প্রভাব পড়বে টেকসই উন্নয়নে। একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিত করে যে, এমনভাবে কোর্স কারিকুলাম ডিজাইন করবে, যাতে জব মার্কেটে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণকে প্রকৃত ব্যবসায়িক বা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার মূল চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
গবেষণা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। অর্থনৈতিক ও শিল্প কাঠামো, বিজ্ঞান, ব্যবসায়িক বা অন্যান্য গবেষণার স্তরকে প্রভাবিত করে। মূলত গবেষণা ও উন্নয়ন এবং উদ্ভাবনকে উৎপাদনশীলতার চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সরকারকে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য প্রণোদনা হিসেবে ক্রমবর্ধমান সংখ্যক বিশেষ আর্থিক সুবিধা দিয়ে যাওয়া জরুরি। দেশের সার্বিক উন্নয়নে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই। গবেষণা ছাড়া উন্নয়নকে টেকসই করা কঠিন হয়ে পড়ে। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক কর্মক্ষমতা এবং সামাজিক অর্জনে গবেষণা ও উন্নয়নের অবদান থাকায় সরকার গবেষণাকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে। মানসম্মত গবেষণার জন্য দরকার বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা। গবেষণার জন্য সরকার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ এবং প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ দিচ্ছে। কিন্তু এগুলো কতটুকু কার্যকর, তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। কারণ, এগুলোতে বেশির ভাগই সরকারি আমলারা যাচ্ছেন। অন্যদের সুযোগ থাকলেও তা সীমিত। সরকার গবেষণার জন্য প্রচুর টাকা খরচ করছে। কিন্তু দেশের উন্নয়নের জন্য কাজে আসছে কি না সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। গবেষণার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করা একান্ত জরুরি। কারণ, ফেলোশিপের মাধ্যমে বিদেশে গিয়ে ডিগ্রি অর্জন করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে হবে। অনেকেই সরকারি টাকায় বিদেশে গিয়ে মাস্টার্স বা পিএইচডি করে থাকে, পরে দেখা যায় সে আর গবেষণার কাজ চলমান রাখে না। তাহলে এ ধরনের ফেলোশিপ দিয়ে দেশের উপকার কী হবে? তাই যে কোনো ফেলোশিপ দেওয়ার ক্ষেত্রে তারা দেশের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা রাখবে সেটা বিবেচনা করা খুবই প্রাসঙ্গিক।
শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞরা অনেক বছর ধরে বলে আসছেন। অতীতে বাজেটেও তার প্রতিফলন হয়নি। অঙ্কের হিসাবে বরাদ্দ বেড়েছে মাত্র, বাস্তবে বাড়েনি। বাজেটে শিক্ষা খাতে উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো সুখবরও ছিল না। বাজেট যতটা ব্যবসা উপযোগী, তারচেয়ে বেশি শিক্ষাবান্ধব হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষায় জিডিপি এর ৫ শতাংশ বা মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ করবে বিগত সরকারের প্রতিশ্রুতি ছিল। তা এখনো রক্ষা হয়নি। শিক্ষা ও প্রযুক্তি মিলে একটি খাতে বাজেটে বরাদ্দ দেওয়া হয়, যা হওয়া উচিত নয়। দেশের টেকসই উন্নয়নের জন্য শিক্ষাকে পৃথকভাবে মোট বাজেটের ২০ শতাংশ বরাদ্দ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার উন্নয়ন ছাড়া বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। সর্বোপরি, শিক্ষায় অনেক উন্নয়ন সত্ত্বেও জিডিপির তুলনায় শিক্ষা বাজেটে বরাদ্দ বাড়েনি। আফগানিস্তানের মতো যুদ্ধবিধ্বস্ত জায়গায় শিক্ষায় বরাদ্দ জিডিপির ৪ শতাংশের বেশি। সেখানে বাংলাদেশে গত অর্থবছরে শিক্ষায় বরাদ্দ ছিল জিডিপির ১ দশমিক ৬৯ শতাংশ। তাই শিক্ষা-গবেষণা খাতে আসন্ন বাজেটে বরাদ্দ বাড়ানো জরুরি।
লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
ময়মনসিংহ
প্যানেল