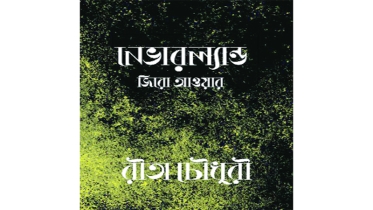(পূর্ব প্রকাশের পর)
কড়াদা ওর মাকে নিয়ে যে ঘরটায় থাকত সেটির ভিটা মাটির; চারপাশে বাঁশের বেড়া আর মাথার ওপর পাতিটিন। তবু সবকিছু ঝকঝকে তকতকে; কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। সন্ধ্যার পর মহিলা শাঁখ বাজাত; ঘণ্টা বাজিয়ে আরতি নিবেদন করত রাধা-গোবিন্দর ছবির সামনে।
আমি দূর থেকে চেয়ে দেখতাম; কখনো খারাপ লাগেনি; হিংসা-দ্বেষ এসবের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নিজের ভেতর টের পাইনি। ওই বয়সে কড়াদার প্রতি এতটাই মুগ্ধতা ছিল যে ওর বেসুরো কণ্ঠের সকল গান আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি এখনো স্পষ্ট শুনতে পাই কড়াদা গাইছে ‘প্রভাত সমীরণে শচীর আঙিনা মাঝে গৌরচান নাচিয়া বেড়ায়রে..’। আরেকটা গান সে প্রায়ই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাতে জাল নিয়ে হেঁড়ে গলায় গাইতে শুরু করত, ‘ওরে সুজন নাইয়া আমি নদীর কূল পাইলাম না।’
বড় হয়ে যখনি এই গানগুলো শুনেছি, সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর এক অজানা আনচান টের পেয়েছি। গানের চরণের ভেতর দিয়ে আমার শৈশব-কৈশোর কথা কয়ে উঠত; কম বয়সের বায়োস্কোপের নেশার মত সেগুলো আমাকে কিছুক্ষণ বুঁদ করে রাখত।
আমার দাদাজান এমনভাবে আমাদের মনটিকে তৈরি করে দিয়েছিলেন যে কড়াদাকে কখনো আমাদের আশ্রিত হিসাবে ভাবিনি। আমার চাচাত ভাইদের মতই ছিল ওদের অস্তিত্ব। একান্নবর্তী পুরো পরিবারটির সঙ্গে ওদের অস্তিত্ব মিশে গিয়েছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধটুকু ছিল অটুট। আমাদের ঈদের আনন্দে ওদের অংশগ্রহণ ছিল সত্য। তবে তা নির্দিষ্ট মাত্রার বাইরে যেত না কখনো। আমরাও ওদের লক্ষ্মীপুজোয় বাজি পোড়াতে আর সন্দেশ-নাড়– খেতে মুখিয়ে থাকতাম। তবে দাদাজানের স্থির করা একটি নির্দিষ্ট লক্ষণরেখা পর্যন্ত ছিল আমাদের যাতায়াত। এই সংযমটুকু ছিল বলেই ছোটবেলা থেকে আমার ভেতর একধরনের পরমত সহিষ্ণুতা বোধ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। এই বোধটুকু আমার আব্বা পেয়েছেন দাদাজানের কাছ থেকে। আর আমি লাভ করেছি যৌথভাবে আব্বা ও দাদাজান দুজনার কাছ থেকে।
কড়াদার মায়ের শুচিবাই ছিল। বিধবা মানুষ; সারাবছর আলাদা চুলায় নিজের জন্য নিরামিষ রেধে খেতেন। আবার ছেলের জন্যে মাছও রেধে দিতেন। মাছের চুলা ছিল আলাদা। মাছ রান্নার পর মাসিমাকে পুকুরে গিয়ে গোসল করতে দেখতাম। এমন কি, উনার ডেরার আশপাশে এক- দুটো হাড় দেখতে পেলেও কড়াদার মা সেটি ফেলে চরম বিতৃষ্ণা নিয়ে কাপড়চোপড় সমেত পুকুর থেকে গোসল সেরে আসতেন।
এ নিয়ে আমাদের কোন প্রশ্ন ছিল না। কখনো কেউ এসব নিয়ে সামান্য মশকরার সুরে কথা বলতে চাইলেও দাদাজান বাধা দিতেন। চোখ বড় বড় করে বলে উঠতেন, ‘ছাড়াবাড়িত যাছ?’
‘মাঝে মাঝে।’ যার মুখ থেকে কড়াদার মায়ের শুচিবাই নিয়ে ঠিসিঠাট্টা ঝরত তার উত্তর।
‘ছাতা সমান কড়–ই গাছটা নজরে আয়ে?’
‘জ্বে।’
‘ওইটার নাম কি জানছ?’
‘জ্বে। বৃন্দাবন।’
‘ওই বৃন্দাবন কার নাম সেটা জানছ না? আমাদের পূর্বপুরুষ। বৃন্দাবন ম-ল। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মনের দুঃখে মুসলমান হইছে। তাগোরে কেমনে হেলা করি ক।’ দাদাজান শূন্য দৃষ্টি দিয়ে সেই গাছটিকে কল্পনা করে নিতেন। কখনো ছাড়াবাড়িতে পায়চারী করতে গেলেও আমি লক্ষ্য করেছি অপলক চোখে তিনি স্মৃতিবাহী সেই কড়–ই গাছটির দিকে তাকিয়ে রয়েছেন।
দাদাজানের এই উদার মানসিকতার ছোঁয়া আমরা সবাই পেয়েছি। আমার বাবাকেও দেখেছি সহনশীল এক মন নিয়ে সবকিছু পরখ করে দেখতে। তাকে কখনো হুটহাট মন্তব্য করতে শুনিনি। দাদাজানের মত রাশভারি ব্যক্তিত্ব তার নেই। তবে বিচার করবার এক অপূর্ব দক্ষতা তিনি অর্জন করেছেন। কারো ওপর রেগে গেলে যেমন চটজলদি মুখ আলগা মন্তব্য করেন না তেমিন কারো ওপর প্রচ- আপ্লুত হয়ে উঠলেও সংযমের সঙ্গে তা প্রকাশ করেন। নিজের ওপর এই নিয়ন্ত্রণ পারিবারিক সূত্রে তার পাওয়া। আম্মার হাজারটা সাংসারিক অত্যাচারেও তা খুইয়ে বসেননি কখনো। এজন্য আব্বাকে আমি সবসময় বাহবা দিই।
অথচ আব্বার চাচাত ভাইরা ঠিক উনার মতো নয়। লেখাপড়ায় যেমন বেশিদূর এগোয়নি তেমনি এক ধরনের গ্রাম্য গোয়ার্তুমি আর মূর্খতা নিয়ে সারাজীবন আব্বাকে হিংসা করতে দেখেছি। বাড়ির সমস্ত সম্পদ ওরা দুই ভাই মিলে জবরদখল করে খাচ্ছে। এ নিয়ে আম্মা কখনো মুখ খুললেই আব্বার বাধা উত্তর, ‘আল্লাহপাক তো তোমাদের অনেক দিছে। এদিকে আর তাকাইও না।’
আব্বাও খুব একটা কিছু আশা করেন না। তবে সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর শেষ বয়সে আব্বার খায়েস হয়েছিল গ্রামের বাড়ি গিয়ে বসবাস করবার। শেষ পর্যন্ত তিনি তা পারেননি। ভাইয়েরা এমন সব কুৎসিত আচরণ করছিল যে গ্রামে যাওয়ার শেষ ইচ্ছেটাও আব্বা হারিয়ে ফেলেন। তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ঢাকায়, আমাদের নিজস্ব ছয়তলা বাড়িতে। আমরা চার ভাইবোন ঘিরেছিলাম তাকে। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে ফ্যাসফ্যাসে গলায় শুধু বলেছিলেন, ‘গ্রামের সঙ্গে তোরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখিস না। ঘন ঘন যাবি। শেকড়হীন থাকা ভাল নয়। আর মনটাকে ছোট বানাস না। মনের আলোয় চলতে শিখলে আনন্দে থাকবি। তোরা সবাই আনন্দে থাকিস।’ কথাগুলো বলে তিনি চোখ বড় বড় করে নিঃশ্বাস নিলেন। একটু পর ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। আমরা সবাই জড়িয়ে রইলাম আব্বাকে। শেষবারের মতো অনুভব করতে চাইলাম এক অন্তর্মুখী পিতার উষ্ণ সত্তাকে।
আব্বার শেষ কথাগুলো মেনে প্রতি বছর একবার গ্রামের বাড়ি বেড়াতে আসি আমরা। বাড়িটা আমাকে সবসময় টানে। শহরের কেনা ফ্ল্যাটে ফার্মের মুরগির মতো খাচাবদ্ধ থাকতে গিয়ে যখনি হাঁফিয়ে উঠেছি তখনি ছুটে এসেছি এখানে। কখনো একা, কখনো পুরো পরিবার নিয়ে। আবার কখনো ভাইবোন সবাইকে নিয়ে দুদিনের জন্যে বনভোজন-বিলাসিতায় ডুবসাতার দিতে। উদ্দেশ্য একটাইÑ এখানে কদিন থেকে নিজেকে চাঙ্গা করে যাওয়া। এর পেছনে সহায়-সম্পদ দখলের কোন ইচ্ছা আমাদের নেই। চাচাত ভাইদের স্পষ্ট করেই আমরা সবাই বলেছি, আমরা শুধু কদিন থাকতে চাই এখানে। তোমাদের সম্পদে ভাগ বসানো আমাদের ইচ্ছে নয়। আব্বার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সাধু-সন্তদের মত আমরাও সমস্ত উত্তরাধিকার ছেড়ে দিয়েছি; তোমাদের দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই।
একথা স্পষ্ট করে দেয়ার পর ওদের আদর-যতœ পেতে আর কোন বাধা রইল না আমাদের। এখন গ্রামের বাড়িতে পা রাখলেই পরম মমতায় আমাদের মত অতিথি-পাখিদের আদরযতœ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে ওরা।
আমরাও প্রতি বছর বুকের গহীনে ‘ফিরে চল ফিরে চল মাটির টানে’র সুর গচ্ছিত রেখে গ্রামের জল-হাওয়ায় নিজেদের ভাসিয়ে দিই।
আমি বৃষ্টিবেলায় আকাশের দিকে তাকিয়ে কড়াদার কথা ভাবি। কড়াদা শরীরে একখানা ন্যাংটি জড়িয়ে শীতলক্ষ্যার জলে মাছ ধরছে আর সেই লাফানো মাছ দেখে আমার মত এক কিশোর পরম আনন্দে লাফাচ্ছি। দাদিজান একসঙ্গে এত মাছ দেখে বিরক্ত হচ্ছেন, ‘কড়ার আর কা-জ্ঞান হইল না। অত মাছ দিয়া আমি কী করুম।’
দুপুরে পুরো বাড়ি জুড়ে তাজা মাছ ভাজার গন্ধ। হাতের ওপর দিয়ে পাতে পড়ছে তেল জবজবে ভাজা মাছ। খেতে চাইছি না। তবু দাদাজান বলছে, ‘খা। খা। শহরে এগুলান কই পাবি? খাঃ।’
অথচ সেই কড়াদার কোন খবরই পেলাম না একাত্তরের পর। যেন ভোজভাজির মত কড়াদার মা আর ও হারিয়ে গেছে এ বাড়ি থেকে। যাকে জিজ্ঞাস করেছি সে-ই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ‘কী জানি। জানের ভয়ে পালাইয়া গেছে হয়তো।’
কেউ উত্তর দিয়েছে, ‘মালাউন যেখানে যায়, ওই হিন্দুস্তানে গিয়া বইয়া রইছে, দেখ গা।’
আমি চাকরি করা মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক লোক। আমার বাবাও একই জীবন যাপন করতেন। প্রকৃতিগতভাবে দুজনই সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে চলছি। দাদাজান কেবল ব্যতিক্রম। তিনি প্রকৃতির মত উদার ও নিষ্ঠুর এক স্বভাব নিয়ে সবার ওপর কর্তৃত্ব করে গেছেন সারাজীবন। তার তিরোধানের পর থেকে এক ধরনের স্বার্থপরতা শীতলক্ষ্যা পাড়ের কাজী পরিবারটিকে গ্রাস করে ফেলে। সবাই নিজ নিজ ভাবনা নিয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে পড়লেন যে যত রকমের কুটিলতা ও সাংসারিক হীনতা তা ধীরে ধীরে সবার ভেতর সেধিয়ে গেল।
আমাদের দাদাজান অতীতের এক স্মৃতি হয়ে গেলেন। আর একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় কড়াদা ও তার মা হারিয়ে গেলেন কাজী বাড়ির এই চৌহদ্দি থেকে।
ভুলেই গেছিলাম ওদের কথা। তবু দাদাজানের এই বাড়িটিতে এলে হঠাৎ করে ওরা যেন কথা বলতে শুরু করে দেয়। ছাড়াবাড়িতে এখন দালান-কোঠা উঠে গেছে। জায়গার দাম চড়া। যার ভাগে যেটুকু পেয়েছে সে-ই সেখানে ঘর তুলে বসবাস করছে। স্মৃতি জাগানিয়া সেই বৃক্ষগুলো কবেই কেটে ফেলা হয়েছে। নদীটা দখল হতে হতে দৃষ্টিসীমানার বাইরে চলে গেছে।
শহরের মত এখানেও আকাশ দেখা যায় না। ইটকাঠের বাড়িঘর দৃষ্টিকে খাবলে ধরে। দুচারটা গাছ যাও বা বেঁচে আছে, একটু তাকালেই মনে হবে, ওদের বুঝি কেউ নেই। নিঃসঙ্গ- নিষ্প্রাণ-নিষ্প্রভ কতগুলো ডালপালা। শহরের মতই লাগে।
তবু বৃষ্টি হলে ওরাও সতেজ হতে শুরু করে। অর্ধমৃত মানুষের মত ওরাও যেন কিছু বলতে চায়। ঠোঁট নড়ে। চোখের পাতা কাঁপে। আমি স্পষ্ট শুনতে পাই ওদের কোঁকানি, ‘জল। একটু জল। আরও জল।’
আমি বেরিয়ে আসি ঘর ছেড়ে। আমার মাথামুখ বেয়ে টিপটিপ বৃষ্টি ঝরছে।
সজনে গাছের ডাল বেয়ে দুফোঁটা অশ্রুর মত জল চুঁইয়ে পড়ল ঠিক আমার নাকের ডগায়। আমি তাকিয়ে দেখলাম মাথার ওপর কচি সজনে ডালটাকে। বৃষ্টির কোমল ছোঁয়া পেয়ে ও তিরতির করে কাঁপছে। এ কম্পনের ভেতর এক ভাষা লুকিয়ে থাকে। দাদাজান বুঝতে পারতেন; কৈশোরে দাদাজানের সাহচর্য পেয়ে এই ভাষা বোঝার ক্ষমতা কিছুটা আমার ভেতরের সংক্রমিত হয়েছিল। কিন্তু শহরে থেকে থেকে এখন আর এর অবশিষ্ট নেই। ভালবাসার মত ওই ক্ষমতাটুকুও কবে আমাকে ছেড়ে গেছে, টেরই পাইনি।
তবু এরকম বাদলা দিনে আড়া-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে গিয়ে এক রকমের দুঃখবোধ আঁকড়ে ধরছে আমায়। যত রকমের অক্ষমতা আমার অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে রয়েছে, সব যেন আলগা হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে আমার ভেতর থেকে। নিজের ভেতর থেকে এক ধরনের নিঃস্বতাবোধ দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। এক বিখ্যাত মানুষের উক্তি নিজের মত করে আমার বাবা প্রায়ই বলে বেড়াতেন, ‘মানুষ হয়ে জন্মেছিস, দুনিয়ার দেয়ালে একটু দাগ হলেও রেখে যা।’
আমার হাঁ করা চেহারার দিকে তাকিয়ে সরকারী চাকুরে বাবা এর ব্যাখ্যা দিতেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে। মাঝে মাঝে আইনস্টাইনের কথাও বলতেন। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার অনুরাগ ছিল বলে তাকেই তুলে আনতেন। তাঁর সময়ে কত রাজা মহারাজা নওয়াব অমাত্য জজ-ম্যাজিস্ট্রেট শাসন করেছেন; কিন্তু যত বড় শাসক বা অর্থশালী হউক না কেন, এখন সবার ঠাঁই ইতিহাসে। সবই অতীত, সবই ইতিহাস। ধূলা ঝেড়ে তারপর জানতে হবে তাদের মত মহামান্যদের কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? একেবারে হিন্দুবাড়ির কাঁসার বাসনকোসনের মত ঝকঝকে তকতকে। সূর্যের আলোয় নিজের মুখ পর্যন্ত দেখা যায়। দুনিয়ার দেয়ালে লিখতে হলে এরকমই লিখতে হবে; যুগের পর পর যুগ যাবে; পলির ওপর পলি পড়বে; পলেস্তারার ওপর পলেস্তারা; তবু ঠিক ভেসে উঠবে সবকিছু ছাপিয়ে। দুশ বছর পরও ইট-কাঠ-পাথরের শহরে সব ছাপিয়ে এক নিষ্কলুষ কিশোর ঠিক গেয়ে উঠবে, ‘আমারে ডাক দিল কে ভেতরপানে।’ অমরত্ব তো এরই নাম।
আমার আব্বার সেই অনুভবটুকুই এখন আমাকে পেয়ে বসছে। কিছু হতে না পারা কিংবা কিছু করতে না পারার এক অবসাদ আমাকে তাড়া করে ফিরছে। বৃষ্টির ছোঁয়া পেয়ে বুকের গহীনে ঘুমিয়ে পড়া সব যাতনা একসঙ্গে সুর মেলাচ্ছে। আমার জন্ম-মৃত্যু, হওয়া-না-হওয়া, ইহলোক-পরলোক, লৌকিক-অলৌকিক চেতনাসহ সমস্ত অস্তিত্ব। নিজের ভেতর থেকে অনেকগুলো আমি একসঙ্গে কেঁদে উঠতে চাইছে; কাঁদতে কাঁদতে অতৃপ্ত আত্মার অমোঘ এক বাণী হয়ে সুর ধরছে, ‘ওরে সুজন নাইয়া আমি নদীর কূল পাইলাম না।’
ঠিক তখনি আশপাশ থেকে অতি চেনা এক কণ্ঠ যেন আমায় ডেকে উঠল, ‘শরাফত শরাফত। আমারে দেখতে পাইতেছিস? আমি এইখানে।’
কড়াদার গলা। এ গলা কখনো ভুলবার নয়। কত ঘণ্টা কত দিন মুগ্ধ হয়ে এ মানুষটির সঙ্গে আমি বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। কত রকমের গালগপ্প মানুষটার মুখ থেকে শুনেছি। কত ফুল কত বৃক্ষের নাম জেনেছি। রঙ-বেরঙের কত মাছ কত নৌকার পরিচয় পেয়েছি। তার গলা আমি ভুলি কি করে? মানুষ দুঃখ ও অপমানের দিন ভুলে গেলেও কোন সুখস্মৃতি সে ভুলে যায় না। সে সেগুলো নিজের ভেতর জাগিয়ে রাখতে ভালবাসে। কড়াদা আমার সেই স্মৃতি, যা এ জীবনে এরকম করে আর কখনো পাওয়া হয়ে ওঠেনি। এই দীনতা থেকেই তো আমি সুযোগ পেলে দাদাজানের এ বাড়িতে ছুটে আসি। হারানো গাছপালা নদীপুকুর হাতড়ে আমার কৈশোরটাকে খুঁজে ফিরি। কেন যেন বারবার করে মনে হয় আমি এখনো কড়াদার পিছু হাঁটতে চাই, ঠিক আগের মত।
‘কড়াদা, আমার হাতটা ধর। এই জায়গাটা পিছল।’ নদীর পাড় বেয়ে নিচে নামতে গিয়ে কতবার যে এই সাহায্য চেয়েছি তার কাছে।
সেই লোকটারই কণ্ঠস্বর এই নিরিবিলি নির্জন জায়গাটায় বৃষ্টি আর হাওয়া ভেদ করে আমার কানে এসে পৌঁছাচ্ছে, ‘শরাফত শরাফত। আমারে দেখতে পাইতেছিস? আমি এইখানে।’
বৃষ্টির তীর উপেক্ষা করে আমি আকাশের দিকে তাকালাম। মাথার ওপর পুরনো ঘি-র মত কালচে আকাশ। সেখানে কোথাও কড়াদা নেই। ডানে তাকালাম। বীচিকলার কতগুলো ঝোপ। পাশে ডাল-পালাহীন একটা মড়া কাঁঠাল গাছ; জলে ভেজা ছাতাপড়া কালো কুচকুচে শরীরটি গোখরো সাপের শরীরের মত লাগছে। বাঁদিকে চোখ রাখলাম, আরে, এ তো কড়াদার প্রিয় বৃক্ষ। তমাল। এদিকটায় একসময় প্রচুর তমাল গাছ ছিল। কড়াদা তমাল ফল পিষে রস করে তাতে চিনি মিশিয়ে কত যে খেতে দিয়েছে আমায়। এ সম্পর্কে কিছু বললেই বলত, ‘এর অনেকগুণ। খাঃ।’ বলে কড়াদাও চুমুক দিত তাতে। ওই বয়সে আমি দেখতে খুব চিকনচাকন গড়নের ছিলাম। প্রায়ই আম্মা আমার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকতেন। কড়াদার প্রস্তুতকৃত সেই সরবত খেয়ে আমার কেবলি মনে হত, আমি মোটা হয়ে যাচ্ছি। কড়াদার কথা কখনো মিথ্যা হবার নয়। এমনি বিশ্বাস ছিল ওর উপর। বসন্তকালে এর গোলাপী ফুল কানের খাঁজে গুঁজে কড়াদা ঘুরে বেড়াত নদীর পাড় ধরে। আমাকেও গুঁজে দিত। লজ্জা হত। তবু দুই কানে দুই ফুল নিয়ে কড়াদার পিছুপিছু চলতাম। আনন্দভরা শিহরণ টের পেতাম ভেতরে।
একদিন কড়াদা বলল, ‘জানছ, মায়ে একখান গান গায়। গাই?’
আমি হ্যাঁ-না কিছু বলবার আগেই কড়াদা শুরু করে দেয়, ‘না পোড়াইয়ো রাধার অঙ্গ, না ডুবাইয়ো জলে। মরিলে বান্দিয়া রাইখো তমালের ডালে গো তমালের ডালে।’ গলায় সুর নেই কড়াদার। তবু গানের কথা এখনো আমার মনে গেঁথে রয়েছে।
গান থামিয়ে তারপর বলত, ‘আমার বড় কৃষ্ণ হইতে ইচ্ছা করে। এই গাছে বইয়া বাঁশি বাজাইত কৃষ্ণ। যদি আমি বাজাইতে পারতাম।’ কণ্ঠে এক ধরনের দুঃখবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠত তখন।
আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কড়াদার কষ্ট নিমিষেই আমাকে ভিজিয়ে দিত।
সেই কড়াদার প্রিয় বৃক্ষের কাছেই দাঁড়ানো আমি। এখানে এ ধরনের প্রায় সবগাছগুলোকে কেটে ফেলা হয়েছে। এটি কিভাবে বেঁচে গেল বুঝতে পারছি না। শীতালক্ষ্যার সুনসান পাড়ে কড়াদার স্মৃতি নিয়ে ও বেঁচে রইল কি করে? আর এদ্দিন আমারই বা চোখে পড়েনি কেন এটি? নাকি বৃষ্টি মাঝে মাঝে কিছু স্মৃতিকে ইচ্ছে করেই উসকে দেয়। এমনও তো হতে পারে, বৃষ্টিশেষে যেদিন ঝকঝকে রপালি রোদে চারধার ঝলমল করে উঠবে, হয়তো সেদিন আর এ বিরল গাছটিকে দেখতে পাব না। এটি কেবল বৃষ্টির মাদকতায় বেড়ে ওঠা কোন এক কল্পতরু! স্মৃতি জাগিয়ে তুলে পরক্ষণে মিলিয়ে যায়!!
ঠিক তখনি কড়াদা ডেকে উঠল, ‘শরাফত শরাফত। আমারে দেখতে পাইতেছিস? আমি এইখানে।’
স্পষ্ট টের পেলাম, ডাকটা ওই তমাল গাছ থেকেই আসছে। অপলক দৃষ্টিতে আমি তাকিয়ে রইলাম গাছটার দিকে। হঠাৎ পাতার আড়ালে ঢাকা কড়াদার চিরচেনা মুখখানা চোখে পড়ে গেল। বোকা বোকা সেই হাসি। ড্যাব-ড্যাব করা পাথুরে চাহনি। মনে হচ্ছে বিশাল পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা এক প্রস্তর মুখ।
আমার সারা শরীর শিউরে উঠল। নিজেকে মনে হচ্ছে ভীতসন্ত্রস্ত কোন কিশোর, এই রাশভারী প্রকৃতির মাঝখানে নিঃসঙ্গ ও হতচকিত। এ অবস্থায় কী করব বুঝতে পারছি না।
চোখের সামনে অগুনতি বৃষ্টির ফোঁটার শিহরণে শীতালক্ষ্যা বারবার করে কেঁপে উঠছে। নদীর ওপারে মিশকালো মেঘের সঙ্গে মিশে রয়েছে সবুজ গাছগাছালির রেখা। এরই ভেতর থেকে উড়ে আসছে বকের দল। যেন মেঘলা আকাশের তলায় হাসতে হাসতে ওরা এখান থেকে ওখানে উড়ে চলেছে।
আমার দৃষ্টি সেদিকে বদ্ধ রইলেও ভেতরকার বিস্ময় আর শঙ্কাবোধ কিছুতেই হ্রাস পাচ্ছে না। কড়াদার পাতায় ঢাকা মুখটি যত দেখছি তত শিহরিত হচ্ছি। কিছুই যেন ঠাহর করা সম্ভব হচ্ছে না।
কড়াদা যেন আগেকার মতই আমাকে বুঝতে পারল। বলে উঠল, ‘ভয় পাইতাছিস ক্যান। আমি কড়া। তর কড়াদাদা।’
আমার চোখজোড়া ফ্যাকাশে। ঠোঁট অকারণে কাঁপছে। মনে হচ্ছে বিড়বিড় করছি।
কড়াদার মুখখানা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল; বলল,‘ আমারে ভয় পাইস না। আমি ভূত হয়ে আছি এখানে। তবে মন্দ ভূত নারে। ভালা ভূত। শীতলক্ষ্যার মাছ খাইয়া বাঁইচা রইছি। আইচ্ছা একটা কতা রাখবি?’
পাল্টা কোন প্রশ্ন করার মত অবস্থা আমার নয়।
বুঝতে পেরে কড়াদা নিজে থেকে বলে উঠল, ‘কাঁচা মাছ খাইতে খাইতে শরীরে মুহে আঁইশটা গন্ধ অইয়া গেছে। বহুদিন রিটা মাছের ভাজা খাই না। তর মায়ের হাতের রিটা মাছের ভাজা আমারে খাওয়াইতে পারবি?’
আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নাড়ি। (চলবে)
শীর্ষ সংবাদ: