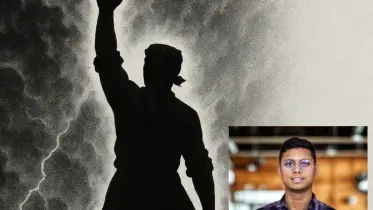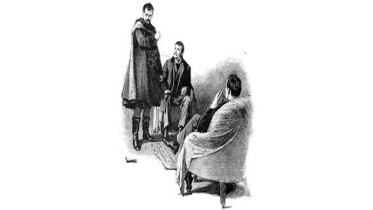সাম্যবাদী কাজী নজরুল
‘মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র্য, ঋণ, অভাব অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণস্তূপের মতো জমা হয়ে আছে- এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম’- বলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম আজীবন। যখন সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, তখন রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির বলশেভিক বিপ্লব চলছিল।
১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে সেই বিপ্লব জয়ী হয়। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টি শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। কমিউনিস্ট পার্টির লাখ ছিল সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। সেনা ছাউনিতে থেকেও সেনানিবাসের সকল বাধা উপেক্ষা করে, বিপদের ঝুঁকি নিয়ে নজরুল রুশ বিপ্লবের সকল খবর এমনকি নানা নিষিদ্ধ গ্রন্থ সংগ্রহ করতেন। রাশিয়ার বিপ্লবের সৈনিকেরা ‘লাল ফৌজ’ নামে অভিহিত ছিল।
লালফৌজের সাফল্যে তিনি এতটাই গর্ববোধ করতেন যে নিজের ব্যারাকের বন্ধু বান্ধবদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন; রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তির খবর পেয়ে রুশ বিপ্লব সন্বন্ধে আলোচনা হয়, সারারাত হৈ-হুল্লোড় হয়। সেনানিবাস থেকে কলকাতার পত্রিকায় ছাপাবার জন্য নজরুল ইসলাম যে গল্প লিখে পাঠান, সেই ‘ব্যথার দান’ গল্পের প্রধান দুই চরিত্র ‘লাল ফৌজে’ যোগ দেয়-এর চেয়ে ভালো কাজ তারা দুনিয়ায় আর খুঁজে পায়নি।
পত্রিকা সম্পাদক, মুজফ্ফর আহমদ, ‘লাল ফৌজে’র বদলে ‘মুক্তি সেবক সৈন্যদের দল’ লিখে দেন কারণ ব্রিটিশ ভারতে ‘লাল ফৌজ’ কথা উচ্চারণ করাও দোষের ছিল। সেনাবাহিনীর চাকরি শেষ হয়ে গেলে নজরুল কলকাতায় এসে (মার্চ ১৯২০) থাকতেন মুজফ্ফর আহমদের সঙ্গে। দুজনের আদর্শ ছিল এক। দুজনে ঠিক করেন যে তারা কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজে এগিযে যাবেন, তারা কমিউনিস্ট বইপত্র পড়তে থাকেন।
সে সময় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ভারতবর্ষের দায়িত্বে ছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় (এম এন রায়)। ১৯২১ সালে এম এন রায়ের বার্তাবহ নলিনী গুপ্ত কলকাতা এলে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে নজরুল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের সূত্রপাত করেন।
১৯২০ সালের জুলাই মাসে নজরুল ও মুজফ্ফর আহমদ দুজনেই ফজলুল হকের ‘নবযুগ’ পত্রিকায় যোগ দেন। এ পত্রিকায় নজরুল স্বাধীনতার কথা লিখেছেন, লিখেছেন কৃষক শ্রমিকের কথা, শ্রেণি সংগ্রামের কথা। নবযুগে প্রকাশিত তার ‘ধর্মঘট’, ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’, ‘মুখবন্ধ’ এ রকম আরও কিছু রচনা শ্রমিক আন্দোলনে প্রেরণা সৃষ্টির অংশ। ব্রিটিশ সরকারের কাছে এ সকল লেখা ছিল সহ্যাতীত। এ জন্য পত্রিকাটিকে সাবধানও করে দেওয়া হয়। তবু নজরুল দমেননি।
‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’ লিখে ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের হুমকি দিলেন। এই জন্য সরকার পত্রিকাটি বন্ধ করে দিল। এই মুহাজিরিন সম্পর্কে সকলের হয়তো সঠিক ধারণা নেই। ব্রিটিশ ভারত পুরোটইি ‘দারুল হরব’- যুদ্ধক্ষেত্র, তাই এ দেশ থেকে হিজরত করে অন্য দেশে যেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে এসে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে- এমন বক্তব্য দিয়েছিলেন মুসলিম আলেমগণ।
এ থেকেই দেশত্যাগের বা মুহাজির আন্দোলনের সূত্রপাত। প্রায় আঠারো হাজার মুসলমান সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে দেশত্যাগ করেন; এদের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তান রাশিয়া প্রভৃতির সহায়তায় যুদ্ধ করে ভারতকে ইংরেজমুক্ত করা। এদেরই অংশগ্রহণে ১৯২৫ সালে আফগানিস্তানে সাম্যবাদী আদর্শে গঠিত হয় প্রবাসী স্বাধীন ভারত সরকার।
মাওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী, মাওলানা বশির, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, মৌলবী বারাকাতুল্লা এই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন; মুহাজির ছাত্ররাও এ সরকারের বিভিন্ন পদে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রী বারাকাতুল্লা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী এবং আরও অনেকে সোভিয়েতেও যান। মাওলানা ওবায়দুল্লা সিন্ধী স্বাধীন ভারতের যে খসড়া গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেন তাতে বলা হয়, ‘আমরা চাই ভারতবর্ষের মাটি থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উচ্ছেদ।
এমন ব্যবস্থা পত্তন করতে যাতে সমাজের শ্রমজীবী শ্রেণিগুলোর কল্যাণ সুরক্ষিত হয়। এমন এক কর্মনীতি আমি তৈরি করেছি যা সমাজতন্ত্রী বা কমিউনিস্ট কারও কাছেই আপত্তিজনক বলে বিবেচিত হবে না।’ তাশকন্দ ও মস্কোতে যে মুহাজিরগণ গিয়েছিলেন তারা ইসলামের সাম্যবাদে উদ্বুদ্ধ ছিলেন এবং তারা তাদের সাম্যবাদী চেতনা আধুনিক-সাম্যবাদ তথা কমিউনিজমের অভিমুখী করেন (এম এন রায় ); মুহাজিররা লাল ফৌজের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন (মুজাফ্ফর আহমদ)।
এই মুহাজির যুবকেরা ভারতের (প্রবাসী) কমিউনিস্ট পার্টির ভিত্তি স্থাপনে এম এন রায়কে বাধ্য করেছিলেন (১৯২০)। এই (প্রবাসী) কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ছিলেন জনৈক মুহাজির। এই মুহাজিরদেরই একজন শওকত উসমানী পরে কানপুর বলশেভিক ষঢ়যন্ত্র মামলায় (১৯২৩-১৯২৫) দ-প্রাপ্ত হন। মুহাজিরিনের এই সাম্যবাদী সংশ্লিষ্টতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য নজরুল তাদের প্রতি অতিমাত্রায় সহমর্মী ছিলেন।
সীমান্ত অতিক্রমকালে এই মুহাজিরদের একটি দলের উপর ইংরেজ সরকারগুলো চালায়। নজরুল ইসলাম প্রতিবাদে ফুসে ওঠেন, প্রতিশোধ নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে লেখেন ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?’। ‘নবযুগ’ বন্ধ হয়ে যায়। জরিমানা দিয়ে ফজলুল হক পুনরায় ‘নবযুগ’ প্রকাশ করেন। কিন্তু কিছুদিন পর নজরুল ‘নবযুগ’ ত্যাগ করেন।
পরে হাফিজ মসউদ আহমদ নামক চট্টগ্রামের এক ব্যক্তি মুজফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুলের সঙ্গী হন; হাফিজ মসউদ আহমদ কুরআনের হাফিজ, এবং শিক্ষা লাভ করেন দেওবন্দ মাদ্রাসায়; খলিফা ওমর যে ‘সোশালিজমের’ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন সেই আদলে মসউদ আহমদ একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করার প্রস্তাব করেন, আর্থিক সহায়তাও করেন; এই মসউদ আহমদের আর্থিক সহায়তায় নজরুল ইসলাম ‘ধুমকেতু’ পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করেন (১৯২২ আগস্ট)।
‘ধুমকেতু’ পত্রিকা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্দীপনা সৃষ্টির পাশাপাশি সাম্যবাদী চেতনা প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ‘ধুমকেতু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়’, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শাসনতন্ত্রে কার্ল মার্কসের সোসিয়ালিজমের সাম্য, লেনিনের বলশেভিজমের সমানাধিকার সমস্তই থাকবে এ কথাও প্রকাশিত হয় (‘ধুমকেতু’ ত্রয়োদশ সংখ্যা, ১৩ অক্টোবর ১৯২২) ।
‘ধুমকেতু’ পত্রিকাতে মুজফ্ফর আহমদ লেখেন, ‘প্রথম খলিফা চতুষ্টয়ের সময়ে যে মুসলিমতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটাকে ভিত্তি করেই বর্তমানের সমূহতন্ত্র বা সাম্যবাদ গড়ে উঠেছে। হজরত ওমর সাম্যের যে আদর্শ আপনার জীবনে দেখিয়ে গেছেন তার তুলনা জগতে নেই। বর্তমান সময়ে রুশ সে আদর্শেরই অনুসরণ করার চেষ্টা করছে, অনেকটা সফলকামও যে না হয়েছে তা নয়।
সাম্যের আদর্শ দেখিয়ে মুসলমানেরা বিশ^ জয় করেছিল। সকল মানুষ সমান অধিকার না পেলে স্বাধীনতা-টাধিনতা কিছুই হবে না।’ ধুমকেতু পত্রিকায় প্রকাশিত হতো টলস্টয়ের অবলম্বনে ‘দাসত্ব’ নামক ধারাবাহিক প্রবন্ধ, ‘খাটে একদল, ভোগ করে আর এক দল হাজার হাজার লোক কাজের জন্য তিলে তিলে ক্ষয় হয়, কিন্তু কারখানার মালিক হয় অন্য জন।’
‘ধুমকেতু’র এসকল কার্যক্রমের জন্য ব্রিটিশ সরকারের গোয়েন্দা পুলিশ নজরুলের গতিবিধি ও তার রচনাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজখবর করত। তাদের এক প্রতিবেদনে লেখা হয় ‘ওরা (কমিউনিস্টরা) সরাসরি প্রচার কাজ শুরু করেছে। তাদের বিশেষ সংবাদপত্র ‘ধুমকেতু” তিনবার অভিযুক্ত হয়েছে।’
‘আনন্দময়ীর আগমনে’ কবিতাকে উপলক্ষ করে নজরুলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারি হয় (আসলে মূলে ছিল ‘ধুমকেতু’তে নজরুলের স্বাধীনতা ঘোষণা)। কেউ কেউ নজরুলকে গা ঢাকা দিতে বলেন। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের তরফ হতে ভারতবর্ষের দায়িত্বে থাকা মানবেন্দ্রনাথ রায় বার্লিন থেকে মুজফফর আহমদকে লিখেছিলেন কবিকে ইউরোপে পঠিয়ে দিতে। নজরুল রাজি হননি।
তিনি গ্রেপ্তার হন, তার কারাদ- হয়, ধুমকেতু পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। কারামুক্তির পর নজরুল নব উদ্যমে শ্রেণি সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ১৯২৫ সালের নভেম্বরে হেমন্ত সরকার, কুতুবউদ্দীন আহমদ, আব্দুল হালিম সকলে মিলে ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়’ নামক দল গঠন করেন। নজরুল হন দলের সাধারণ সম্পাদক।
সাংগঠনিক কমিটিতে মুজফফর আহমদের নাম ছিল না কারণ ১৯২৩ সাল থেকে তিনি কানপুর বলশেভিক ষঢ়যন্ত্র মামলায় বন্দি ছিলেন। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় মানবেনদ্রনাথ রায়, নলিনী গুপ্ত, মুহাজির শওকত উসমানী এরাও আসামি ছিলেন।
বলশেভিক ষঢ়যন্ত্র মামালার আসামিদের অপরাধ এই ছিল যে তারা ভারতের ইংরাজ স¤্রাটকে শাসন ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে ১৯২১ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছে এবং বলশেভিকবাদ (কমিউনিজম) ভারতে ঢুকে পড়লে ব্রিটিশ সা¤্রাজ্যের সর্বনাশ হবে। ১৯২১ সালে নজরুলও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন কিন্তু তিনি আসামি হননি।
‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের মুখপত্র ‘লাঙল’ এর প্রধান পরিচালক ছিলেন নজরুল; দলের ঘোষণাপত্র নজরুলের নামে লাঙলে প্রকাশিত হয় (১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫)-কলকারখানা রেলওয়ে প্রভৃতি জাতীয়করণ, ভূমির স্বত্ব স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন পল্লীতন্ত্রের উপর ন্যস্ত করা (রাশিয়ার সোভিয়েত-প্রথার অনুরূপ), কলকারখানার মুনাফায় শ্রমিকের অংশ প্রাপ্তি, মহাজনী-প্রথার পরিবর্তে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের দ্বারা ঋণ প্রদান ইত্যদি।
এই কর্মসূচি কমিউনিস্ট ম্যানেফেস্টোর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিছুদিন পর ‘শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়’ ‘বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলে’ পরিণত হয়; এ দলের কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। এই দলের সংগঠকদের পরিচয় দিতে গিয়ে নজরুল বলেন এরা সব ‘বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি।’ ‘লাঙল’ পত্রিকা পরিণত হয় বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের সাপ্তাহিক মুখপত্র, প্রধান পরিচালক থাকেন নজরুল।
১৫ এপ্রিল ১৯২৬ সংখ্যায় লাঙলের শিরোনাম পৃষ্ঠায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক কাস্তে হাতুড়ি ছাপা হয়। কাস্তে হাতুড়ি খচিত লাল পতাকা ও ফেস্টুন নিয়ে বেঙ্গল পিজ্যান্টস এন্ড ওয়ার্কার্স পার্টি (বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল) ১৯২৮ সালে রাস্তায় বের হযেছিল। লাঙল নাম পরিবর্তিত হয়ে ‘গণবাণী’ হয়েছিল এবং সম্পাদক হয়েছিলেন মুজফ্ফর আহমদ।
লাঙল ও গণবাণীতে প্রকাশিত হতো কার্ল মার্ক্সের রচনা, লেনিনের রচনা, ও অন্যান্য কমিউনিস্ট সাহিত্য; এ ছাড়া ‘কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো’র বাংলা অনুবাদ, ভারতীয় কমিউনিস্ট কনফারেন্স ও ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সংবাদসমূহ এতে প্রকাশিত হতো। বস্তুত কমিউনিস্ট সাহিত্য বাংলা ভাষায় প্রকাশের পথিকৃত হলো কাজী নজরুলের লাঙল, গণবাণী।
নজরুল তখন পুরোদস্তুর মার্কসবাদী, লেখেন, ‘কার্ল মাক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে।’ লাঙলের প্রথম সংখ্যায় নজরুলের সাম্যবাদী কবিতাসমূহ ছাপা হয় (ডিসেম্বর ১৯২৫)। গণবাণীতে-প্রকাশিত হয় কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ভাব অবলম্বনে নজরুলের অন্তর ন্যাশনাল সংগীত- জাগো অনশন বন্দি ওঠো রে যত, তার রক্ত-পতাকার গান- ওড়াও ওড়াও লাল নিশান ইত্যাদি!
শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টি এবং কৃষক ও শ্রমিক দলের কর্মসূচি নিয়ে কাজী নজরুল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রমিক সম্মেলন, কৃষক সম্মেলন, ধীবর সম্মেলন এবং জনসভায় সাম্যবাদের সপক্ষে বক্তৃতা দেন, উদ্দীপনামূলক সংগীত পরিবেশন করেন।
এ সকল সম্মেলনকে সামনে রেখেই তিনি রচনা করেন- ‘ওঠরে চাষি জগদ্বাসী ধর কষে লাঙল’, শ্রমিকের গান- ‘যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা/রাজা উজির মারছে মজা’, ধীবরের গান- ‘আমরা নিচে পড়ে রইব না আর’। এ সময়েই নজরুল তার মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে লেখেন - নায়ক আনসার রাশিয়ার বলশেভিকদের গুপ্তচর, কার্ল মার্কস, লেনিন, ট্রটস্কি, স্টালিনের অনুসারী, সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কমিউনিস্ট মতবাদ প্রচার করে এবং তাদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করছিল।
১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে কুষ্টিয়ায় কৃষক সম্মেলনে গ্রেট ব্রিটেনের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ফিলিপ স্প্র্যাট উপস্থিত ছিলেন; উপস্থিত ছিলেন নজরুল এবং মুজফ্ফর আহমদও।
নজরুলের সাম্যবাদী কর্মকা- ব্রিটিশ সরকারের তীক্ষè গোয়েন্দা নজরদারিতে সব সময় ছিল। কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগের ফাইলে (১৯২৬ সালে আই বি ৩২০/১৯২৬) লেখা হয় ‘কুতুবুদ্দীন, আব্দুল হালিম, কাজী নজরুল ইসলাম ও হেমন্ত সরকারকে সাথী করে, নলিনী গুপ্ত (কানপুর বলশেভিক মামলার দ-প্রাপ্ত আসামি) লেবার স্বরাজ পার্টি গঠন করেছে- বেঙ্গলে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্দেশ্যে।’
মিরাট কমিউনিস্ট ষঢ়যন্ত্র মামলা (১৯২৯-৩৩)-এর অফিসিয়াল প্রসিডিংয়ে উল্লেখিত হয় ‘কমিউনিস্ট পার্টির আদি রূপ হচ্ছে লেবার স্বরাজ পার্টি যা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২৫ সালের ১ নভেম্বর, এর পরিপূর্ণ দলিল প্রকাশিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরে।’ শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টি এবং বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল গঠন ছাড়াও নজরুল একা সাম্যবাদী সংগঠন গড়ে তোলারও চেষ্টা করেন এমনটির প্রমাণ পাওয়া যায় ব্রিটিশ গোয়েন্দা ফাইলে যেখানে বলা হয় -মুসলিম গোপন রাজনৈতিক সংগঠন বলশেভিজম প্রচার করছিল, নজরুল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন; পুলিশের ধারণা নজরুল কুমিল্লায় গোপন বিপ্লবী দল গঠন করেছেন।
১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে কানপুরে ‘ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি’ গঠিত হয়। আগে থেকে তাতে কাজী নজরুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা (১৯২৪), মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলার (১৯২৯) কাগজপত্রে নজরুল ইসলামের নাম আসে।
মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় নজরুল স্বাক্ষরিত লেবার স্বরাজ পার্টির ঘোষণাপত্র একজিবিট হিসাবে পেশ হয়। ১৯৩১ সালে এই মামলায় কমরেড মুজফফর আহমদ যে বিবৃতি দেন তাতে তিনি কাজী নজরুল ইসলামের নামও উল্লেখ করেন। কিন্তু ভাগ্যক্রমে নজরুল এ মামলায়ও আসামি হননি।
আশ্চর্যজনক যে, নজরুল আনুষ্ঠানিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেননি, এবং কৃষক ও শ্রমিক পার্টি প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর পর দল থেকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছেন। ১৯২৯ সালে কুষ্টিয়ায় কৃষক সম্মেলনের পর থেকে পার্টির কাজে তিনি একেবারেই অনুপস্থিত। জীবিকার তাড়নায় সংগীত জগতে ব্যস্ততা এর কারণ হলেও হতে পারে।
তবে তার সাম্যবাদী তৎপরতা থেমে থাকেনি। কবিতা গান নাটকে, অভিভাষণে তিনি সাম্যবাদী আদর্শ প্রচার করে গেছেন। সংগীতের জগতে অন্যান্য সংগীতের সঙ্গে তিনি ইসলামি গানও লিখেছেন। ইসলামি গানের অনেকটিতেই তিনি সাম্যের কথা সরবে উচ্চারণ করেছেন- ‘পাঠাও বেহেশত হতে হজরত পুনঃসাম্যের বাণী’, ’সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা, উচ্চ-নিচের ভেদ ভাঙ্গি দিল সবারে বক্ষ পাতি’ ইত্যাদি। ইসলামি সাম্যবাদের একজন একনিষ্ঠ অনুরক্ত ছিলেন নজরুল ইসলাম।
ধর্মীয় চিন্তাচেতনায় কবির একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে ১৯৪০-এর দিকে। সচেতন জীবনের এই সায়াহ্নে কবি সর্বশক্তিমান ¯্রষ্টার কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, তার ধ্যান জ্ঞান ভক্তি ভালবাসা বক্তৃতা বিবৃতি সবই নিবেদন করেন সেই পরম করুণাময়ের প্রতি।
উনিশ শ’ একচল্লিশ সাল নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট শাসনের প্রায় পচিশ বছর পূর্ণ হয়, দেশটি পরাশক্তিতে পরিণত হয়, সকল মানুষের আর্থিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়; কিন্তু জনগণের আর্থিক বৈষম্য কতটুকু নিরসন হয়, শ্রেণিহীন সমাজ কতটুকু প্রতিষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে প্রশ্ন রয়েই যায়।
কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ কোন্দল দ্বন্দ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনেকে শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের লাখ থেকে বিচ্যুত করে, কমিউনিজমকে শুধু কাগজ কলমে সীমিত করে। নজরুল হয়তো তা লক্ষ্য করেছিলেন। যে নজরুল ইসলাম ১৯২৬ সালে মার্ক্সিজম কমিউনিজমের কথা লিখতেন, তিনিই ১৯৪১ সালে লিখলেন, ‘আমি বুঝি না কো কোনো সে ‘ইজম’ কোনোরূপ রাজনীতি, /আমি শুধু জানি, আমি শুধু মানি, এক আল্লার প্রীতি।’ ‘নির্যাতিতের আল্লাহ তিনি, কোনো জাতি নাই তার, / যুগে যুগে মারে উৎপীড়কেরে তাহার প্রবল মার।’
ধর্ম সম্পর্কে কমিউনিস্টদের দৃষ্টিভঙ্গি এরকম ছিল যে, ‘ধর্মের বিধান সকল দেশে সকল কালেই রাজা বা শাসনকর্তার মুখের দিকে চেয়ে রচিত হয়েছে। প্রথমে যে মূর্তিতে ধর্ম প্রচারিত হয়েছে সে মূর্তি তার কিছুকাল পরেই পরিবর্তিত হয়ে গেছে রাজা-বাদশার প্রয়োজনে (কমরেড মুজফফর আহমদ)।’ নজরুলও এ কথার প্রতিধ্বনি করেন - ‘পৃথিবীতে ধর্ম প্রচারকের নামে . . শয়তান বাহির হইয়াছে। . . ইহারা ঘোর স্বার্থপর একদল ধনিকের ঘুষ ও বেতন-ভোগী।’
তবে বিশুদ্ধ ধর্মকে তিনি কখনো অশ্রদ্ধা করেননি। ইসলাম ধর্মের সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতির প্রতি ছিল তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা- তিনি বলেন ‘ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞান ভা-ারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এই নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। . . সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে।
আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে- এ শিক্ষাই ইসলামের।’ কবির এই বক্তব্যের উৎস হচ্ছে পবিত্র কুরআন। কুরআনের আদেশ হচ্ছে, ‘ধনসম্পদ যেন তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তিত না হয়’ (কুরআন ৫৯.৭ সুরা হাশর, আয়াত ৭), বিত্তবানের ‘সম্পদে অধিকার আছে বঞ্চিতের’ (কুরআন ৫১.১৯, ৭০.২৪); আল্লাহ আদেশ করেন সাম্যের (কু ১৬.৯০)।
আধুনিক সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক লক্ষ্য যেখানে- সমাজের সকলে পরিশ্রম করবে এবং পরিশ্রম অনুযায়ী ভোগ করবে, পরবর্তী ধাপে (সাম্যবাদে) সকলে সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ করবে; সেখানে মুহাম্মদ (স;) ও তার সহযোদ্ধাগণের লক্ষ্য ছিল- সমাজের সকলে সাধ্য অনুযায়ী পরিশ্রম করবে এবং অর্জিত সম্পদ সকলে সমানভাবে ভাগ করে নেবে।
সশস্ত্র শ্রেণি-সংগ্রাম এবং অজ¯্র আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে মুহাম্মদ (স:) এবং তার সহযোগীগণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে অধিষ্ঠিত হয়ে এই সমানাধিকার বাস্তবে রূপায়িত করেন। ব্যক্তি মালিকানার অব্যবহৃত কৃষি-ভূমি রাষ্ট্রায়ত্ত করে হযরত ওমর তা দিয়ে দিয়ে দিয়েছেন এমন কৃষককে যার আবাদযোগ্য জমি ছিল কম; মুহাম্মদ (স:) ও খলিফাদের আমলে চারণভূমি, সেচের পানি, খনি ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সম্পদ বলে বিবেচিত হয়েছে; রাষ্ট্রের প্রশাসক ও সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রার মান এক করার সার্থক প্রচেষ্টা হয়েছে। এঁরাই নজরুলের আদর্শ।
বিশাল রাষ্ট্রের পরিচালক হয়েও মুহাম্মদ (স:) বাস করেছেন মাটির দেওয়াল দেওয়া খেজুর পাতার ছাউনিতে। ‘হজরত ওমর হজরত আলী এরা অর্ধেক পৃথিবী শাসন করেছেন; কিন্তু নিজেরা কুঁড়ে-ঘরে থেকেছেন, ছেড়া কাপড় পরেছেন . . রাজকোষের টাকায় বিলাসিতা করেননি (নজরুলের ভাষ্য ১৯৩৮)।’ নজরুল পরিচালিত লাঙল পত্রিকায় এক সময়ে (৭ মাঘ ১৩৩২) প্রকাশিত হয়েছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মিলনে প্রদত্ত মৌলানা হাসরত মোহানীর ভাষণ, ‘সাম্যবাদের চেয়ে ইসলামই ধনিকতন্ত্রের অধিকতর বিরোধী।’
ইসলামে-আস্থাশীল বাংলার-সংখ্যাগরিষ্ঠ-মানুষের উপর নজরুল ইসলাম কোনো নতুন ইজম চাপিয়ে দিতে চাননি বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বিশ^াসের সীমারেখাতেই সাম্যবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটানোর প্রয়াস পেয়েছিলেন। ১৯৪১ এ কলকাতায় ফজলুল হক ছাত্রাবাসে তিনি বলেন, ‘ইহা কোরান মজিদে আল্লার বাণী তিনি যে ধনীদের উদ্বৃত্ত অন্ন দিয়েছেন, ক্ষুধাতুরের সেই উদ্বৃত্ত অন্নে হিসসা আছে।
তাদের এই প্রাপ্য যে বঞ্চিত করে, সে ভোগী, দোজখের নার (অগ্নি) প্রজ্বলিত তাহারই জন্য।’ কবিতায় তিনি আহ্বান করেন, ‘আজি ইসলামি-ডঙ্কা গরজে ভরি জাহান,/নাই বড় ছোটো- সকল মানুষ এক সমান,/ . . ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই,/সুখ-দুখ-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,/নাই অধিকার সঞ্চয়ের!/. . দুজনার হবে বুলন্দ-নসিব, লাখে লাখে হবে বদনসিব?/এ নহে বিধান ইসলামের ॥ / . . ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে/তৃষ্ণাতুরের হিসসা আছে ও পিয়ালাতে।’ এই হিসসা আদায়ের জন্য তিনি সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলেন (১৯৪১), ‘আজ মুখ ফুটে, দল বেঁধে বল, বল ধনীদের কাছে,/ওদের বিত্তে এই দরিদ্র দীনের হিসসা আছে।’ ‘আল্লার দেওয়া পৃথিবীর ধন-ধান্যে/সকলের সম অধিকার;/ . . ইহাই নিয়ম আল্লার।/এক করে সঞ্চিত, বহু হয় বঞ্চিত-/জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে- সঙ্ঘবদ্ধ হও!/আপনার অধিকার জোর করে কেড়ে লও!/নইলে আল্লার আদেশ না মানিবে,/ পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে;/. . রবে না দারিদ্র্য, রবে না অসাম্য,/সমান অন্ন পাবে নাগরিক গ্রাম্য,/রবে না বাদশা রাজা জমিদার মহাজন,/কারও বাড়ি উৎসব কারও বাড়ি অনশন,/কারও অট্টালিকা কারো খড়হীন ছাদ,/রবে না এ ভেদ, সব ভেদ হবে বরবাদ।/নির্যাতিত ধরা মধুর সুন্দর প্রেমময় হোক!/জয় হোক, আল্লার জয় হোক!/সাম্যের জয় হোক! (নবযুগ ১৯৪১ ফেব্রুয়ারি)।’
‘উপবাস যার দিনের সাধনা নিশিথে শয়নসাথী,/যাহারা বাহিরে গাছতলে থাকে, ঘরে জ¦লে নাকো বাতি, / . . তারা তিেিল তিলে মরে এবার আনিয়াছে খোদার মার। (১৯৪১)’। এমনই ছিল কমিউনিস্ট আন্দোলনের সময়ের সেই আহ্বান, ‘শোন্ অত্যাচারী ! শোন্ রে সঞ্চয়ী!/ছিনু সর্বহারা, হব সর্বজয়ী।/ওরে সর্বশেষের এই সংগ্রাম মাঝ/নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ।/ হবে নিখিল মানব জাতি সমুদ্ধত।’- জাগো অনশন বন্দি ওঠরে যত- এরই প্রতিধ্বনি ভিন্ন সময়ে ভিন্ন আঙ্গিকে ভিন্ন ভাষায়।
‘জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,/জাগিছে কৃষাণ ধুলায়- মলিন, /জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন/জাগে মজলুম বদ-নসিব!/ মিনারে মিনারে বাজে আহ্বান-/‘আজ জীবনের নব-উত্থান!’/ . . আজান ফুকারি এস নকিব !’ ‘আল্লার আদেশেই(!)’ সশস্ত্র সংগ্রামের অঙ্গীকার তার, ‘দরিদ্র মোর ব্যথারসঙ্গী, দরিদ্র মোর ভাই; /. . মোর আল্লার হুকুম পেয়েছে এ হুকুম-বর্দার, /উহাদেরি তরে যুদ্ধ করির হাতে লয়ে তলোয়ার / . . আমরা গরিব মোরা শতকরা নিরানব্বই জন, /আমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইব করিয়া পরাণ-পণ।
/লোভী রাক্ষস ভোগীদের সংহার করি পৃথিবীতে/পূর্ণ সাম্য আনিব, দানিব অমৃত বঞ্চিতে।’ সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদ কামনা করেছেন, ‘তোমার নামের মহিমায়- ফিরে পাব/শান্তি, সাম্য . . / তুমি বল দাও, তুমি আশা দাও, পরম শক্তিমান! /. . . সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের মিটাও মিটাও সাধ,/. . আমরা কাঙাল, আমরা গরিব, ভিক্ষুক মিসকিন,/ভোগীদের দিন অস্ত হউক, আসুক মোদের দিন।’
ধর্মের বিভেদ তিনি মানতেন না। সকল ধর্মের মাঝে তিনি সেই এক সর্বশক্তিমানকে খুজেছেন। সর্বশক্তিমান কোনো বৈষম্য চান না। তাই কবি আহ্বান করেন, ‘আমি মৃতের দেশে এনেছি রে/মাতৃ নামের গঙ্গা ধারা।/ . . আয় আশাহীন ভাগ্যহত/শক্তি-বিহীন পদানত/(আয় রে সবাই আয়)/এই অমৃতে আয়, উঠবি বেচে/জীবন্মৃত সর্বহারা ॥’ তার বিশ^াস- সকল ধর্মই শোষণহীন শ্রেণিহীন সমাজ গঠনে প্রত্যাশী, ‘এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন /. . সেথা রইবে না কো ছোঁয়াছুঁয়ি উচ্চ-নিচের ভেদ /. . দীন-দরিদ্র রইবে না কেউ, সমান হবে সর্বজন।’
সচেতন জীবনের সায়াহ্নে যখন তিনি স্রষ্টার কাছে পরিপূর্ণ আত্মনিবেদিত তখন বলেন, ‘আমি এই বিদ্বেষ-জর্জরিত কুৎসিত সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব; . . -সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, প্রেম সে আবার ফিরে পাবে।
. . সেই সাম্য, অভেদ, শান্তি, আনন্দ, সেই প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম প্রেমময়ের কাছ থেকে।’ অনেকের সঙ্গে নজরুলের স্বাতন্ত্র্য এইখানে- তিনি ছিলেন ধর্ম ও সাম্যবাদের সহাবস্থানে বিশ্বাসী।