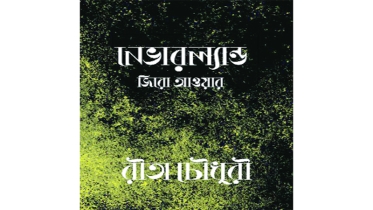বিরিশিরি এখনও আমার স্মৃতির উল্লেখযোগ্য একটি অংশ দখল করে আাছে। পেশায় এখন একজন প্রতিষ্ঠিত আইন ব্যবসায়ী। জেলা দেওয়ানি ও ফৌজদারি উভয় আদালতে আমি স্বনামধন্য উকিল। জেলা শহরেই বাস আমার। বাবা-মা গ্রামের বাড়িতেই থাকেন। আর বাবা-মা’র টানেই এখনও মোটরবাইক হাঁকিয়ে গ্রামের বাড়ি যাই। বিরিশিরি হয়েই বাড়ি যেতে হয়। নামাজের সময় হলে বিরিশিরি মসজিদে নামাজ আদায় করে নিই। আর এ মসজিদে ঢোকামাত্র সুদূর অতীতে ফিরে তাকাই। তখন মনে মনে বলি, এ জনপদের মানুষ হানাদার পাক সেনাদের সবকিছু ঘৃণার চোখে দেখলেও- এ মসজিদটা অন্তত বর্জন করেনি। বিরিশিরি এলাকার মানুষের ধারণা, পাকবাহিনী অপরাধ করলেও মসজিদের তো কোন দোষ নেই। তাই আপামর মুসলিম জনসাধারণ নামাজের জন্য খোদার এ ঘর মসজিদকে গ্রহণ করে নিয়েছে। অবশ্য আজ প্রায় সাড়ে চার দশক পর পাকাবাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে এ মসজিদটা অন্তত টিকে রয়েছে। মসিজদে নামাজের জন্য ঢুকলে আজও আমার মনের পর্দায় একে একে সুদূর একাত্তরের কথাগুলো ভেসে উঠে।
বিরিশিরি পাক হানাদারদের সুরক্ষিত ক্যাম্পে আমিই ছিলাম সবচেয়ে খুদে রাজাকার। বয়স আর কত ছিল। অনুমান তেরো-চৌদ্দ। অবশ্য নিজের ইচ্ছায় রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাইনি। বাবা ছিলেন খাঁটি মুসলিম লীগার এবং পাক সরকারের একজন অনুগত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। বাধ্য হয়ে তাঁকে থানা শান্তি কমিটির প্রধান হতে হয়। থানা সদর থেকে আমাদের গ্রামের বাড়ির দূরত্ব প্রায় দশ-এগারো কিলো। কাজেই স্বাধীনতাবিরোধী হওয়ার কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের হামলার ভয়ে অত্মরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত বাবার ইচ্ছার প্রতিফলনই ঘটে। আমি হয়ে গেলাম খুদে রাজাকার। তবে আমার কাজ কিন্তু অস্ত্রচালনার মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মূল কাজ ছিল পাক বাহিনীর স্পাই হয়ে মুক্তিবাহিনীর খোঁজ-খবর সংগ্রহ করা। তবে বিপদমুক্ত দূরত্বেই অবস্থান করতাম। আমার মতো কিশোর একটা ছেলে পাক বাহিনীর গুপ্তচর হতে পারে-সাধারণ মানুষ তা ভাবতেও পারত না। বাবার ধারণা ছিল, শক্তিশালী পাকবাহিনীর কবল থেকে মুক্তিযোদ্ধারা কখনই এদেশ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আমার বয়স কম ছিল বলে অতশত বুঝতাম না। তাই অস্তিত্বের প্রয়োজনে এবং বাবার নির্দেশে পাকবাহিনীর অধীন রাজাকার বাহিনীতে চাকরি করতাম। মুক্তিবাহিনীরা কখনও আক্রমণ করলে শুরু হতো ধুন্ধুমার যুদ্ধ। তখন আমি পাকবাহিনীর সুরক্ষিত ক্যাম্পে আশ্রয় নিতাম। কিশোর ছেলে আমি। কৈশোরের কমনীয় চেহারার দিকে পাক বাহিনীর সদস্যদের লোল দৃষ্টি পড়েছে কখনও। সে জন্য আদরের অজুহাতে আমাকে কেউ কেউ ক্রমাগত চুমু দিত। সেসব যে কেবল আদর ছিল না, বরং তাতে যৌনতার বিষয় ছিল, তা কিন্তু ঢের বুঝতে পেরেছিলাম। হয়ত ওদের হিং¯্র থাবায় বলাৎকারের শিকারও হতে পারতাম। কিন্তু বাবা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান হওয়ায় সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে ছিল তার ওঠাবসা। তাই সেপাইগুলো হয়ত বা তাদের থাবা বিস্তার করতে সাহস করেনি। সিপাইদের ওসব বাড়াবাড়িকে আমি আদর হিসাবেই বাধ্য হয়ে মেনে নিতাম। বিরিশিরি ক্যাম্পের পাক মিলিটারি-রাজাকার নির্বিশেষে সবাই আমাকে আদর করত।
কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিকে পাকসেনাদের মেজাজ কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছিল। মুক্তিবাহিনীর ক্রমাগত আঘাতে পর্যুদস্ত হয়ে রুক্ষ মেজাজে কথা বলত আমাদের সঙ্গে। এমন কি এ দেশ স্বাধীন হবার আগে ওরা আমাদের তেমন বিশ^াসও করত না। এর কারণও অবশ্য ছিল। আমাদের রাজাকারদের কিছু সদস্য সোমেশ^রী নদীর ওপারে দুর্গাপুরে গিয়ে অস্ত্রসহ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। তাই পাক বাহিনীর এ ক্যাম্পে আমাদের অবশিষ্ট রাজাকারের উপস্থিতি ওদের চোখে ভুল ভাষায় অনূদিত হচ্ছিল। আর তার চূড়ান্ত ফলাফল পেলাম ক’দিন পর। হঠাৎ এক সন্ধ্যায় আমাদেরকে এতিম এবং অরক্ষিত অবস্থায় রেখে ওরা ঢাকার উদ্দেশে পালাল। সেটা ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকের ঘটনা। আমাদের বাঘের মুখে ফেলে রেখে কাপুরুষের মতো পালিয়ে গেল ওরা। প্রথম সংবাদটা আমি বাবার মুখে শুনি। ফ্যাকাশে মুখে বাবা আড়ালে ডেকে নিয়ে আতঙ্কের দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকান। তারপর বলেন, হারামির বাচ্চারা আমগরে থুইয়া পালাইয়া গেছে।
-তাইলে অহন কী উপায় বাবা...?
-আর কোনো কতা নাই, চল-তাড়াতাড়ি পালাই।
এ কথা বলেই বাবা আমার হাতে ধরে নিয়ে পাকবাহিনীর পেছনে পেছনে রাতের অন্ধকারে ছুটলেন দক্ষিণ দিকে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল। সামনে চেয়ে দেখি, রাতের অন্ধকারের চেয়েও ঘনীভূত আমাদের ভবিষ্যত। বাবার সঙ্গে পা চালিয়ে যেতে যেতে নিচু স্বরে বললাম, বাবা! এখন আমাদের কী হবে?
-জানি না। চল...
-কোথায় যাব আমরা?
-কিশোরগঞ্জে তোর বোন-জামাইয়ের বাড়িতে।
-ঐখানে গেলে কি বাঁচন যাইব?
-তর বইন-জামাইয়ের বড় ভাইয়ের ছেলে আফাজ উদ্দীন নাকি মুক্তিবাহিনীর কমান্ডার। আমারে খুব শ্রদ্ধা-ভক্তি করত। ওর সামনে যাইয়া পড়লে...
-যদি মাইরা ফেলায়..
-না মারব না। চোখের পর্দা বলতে একটা জিনিসি তো আছে, নাকি?
ছদ্মনামে আত্মগোপন করে ঝুঁকিপূর্ণ পথে কখনও ট্রেনে, কখনও হেঁটে শেষ পর্যন্ত কয়েকদিনে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর গিয়ে পৌঁছলাম। আমার বড়ভগ্নিপতি গ্রামের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। বোনের বাড়ি আসার পরপরই দেশ স্বাধীন হয়। আমার ভগ্নিপতি মুক্তিবাহিনীর কোম্পানি কমান্ডারের চাচা বলেও এলাকায় তার দারুণ প্রভাব। বাবা তো ন্যাকা সেজে বুবুর ঘরের ভেতর সেই যে ঢুকেছে, আর তার মেয়ের জামাইয়ের মুখোমুখি হয় না। ১৬ ডিসেম্বর রাতেই আমার দুলাভাই অতি সংগোপনে স্থানীয় কোম্পানি কমান্ডার তার ভাইস্তাকে ডেকে তাদের বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসেন। তার সঙ্গে তখন আরও ক’জন সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা সদস্য। কোম্পানি কমান্ডারের নির্দেশে ওরা বাড়ির বৈঠকঘরে অবস্থান করছিল। কোম্পানি কমা-ার আফাজ উদ্দীনকে দুলাভাইয়ের শয়নকক্ষে ডেকে এনে সব খুলে বলেন। অতঃপর আমাকে তাঁর সামনে উপস্থাপন করেন। আমাকে দেখেই তিনি বলেন, কী খবর মামু! আপনার আব্বা কই? ডাইক্যা আনেন দেহি শালা নানাভাইরে!
বুবু তো ভাসুরপুত্রের কথা শুনে ভয়ে প্রথমে থতমত খেয়ে যান। পরে বুঝতে পারেন, নানাকে কৌতুকছলে কথাগুলো বলেছেন কোম্পানি কমান্ডার। শেষে অবশ্য তিনি বলেন, ঠিক আছে। কী আর করণ যাইব! আমগর আশ্রয়ে যখন আইস্যাই পড়ছে...। তবে খুব সাবধান। নানা যেন ভুলেও বাড়ির বাইরে না যান। আর মামু!
-জি, মামা।
-আপনার কিন্তু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে অইব। নাইলে...বলা তো যায় না। ছেলে মানুষ, আবার কার হাতে যাইয়া ধরা পড়েন।
কোম্পানি কমান্ডারের এ কথা শুনে বুবু বলেন, ওরে না হয় আমিই বাড়ির ভেতরে দেইখ্যা-দেইখ্যা রাখমু।
-ঠিক আছে চাচি। তবে মামু! আগামীকাল কিন্তু আমার সঙ্গে আপনার এক জায়গায় যাওন লাগব।
আগ্রহভরে বললাম, ঠিক আছে, আমি যামু।
কিন্তু কেন আমাকে নিয়ে যাবে, তা কিন্তু ভাবিনি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের শত্রুপক্ষ হয়েও বেঁচে থাকার একটা নিশ্চয়তা যে কত বড় প্রাপ্তি তা ওই রাতেই উপলব্ধি করলাম। সারারাত দুশ্চিন্তামুক্ত হয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলাম। অন্তত কয়েক মাসের মাঝে এমন শান্তিপূর্ণ ঘুম আর হয়েছে বলে মনে পড়ে না। যুদ্ধ মানেই তো জীবন-মৃত্যু খেলা। আর এ খেলাই তো কাছে থেকে দেখেছি ক’টি মাস ধরে। আর যুদ্ধের পরাজিত সৈনিক হয়ে মৃত্যুর কাছাকাছি এসেও পাচ্ছি বেঁচে থাকার আশ^াস।
পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই বুবু আমার জন্য সকাল সকাল রান্না সম্পন্ন করেছেন। বুবুর আদরের ছোট ভাইটিকে যতœ করে খাওয়ালেন। সকালের খাওয়া শেষে আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি। এর মাঝেই সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীর দল এসে উপস্থিত হয়। বুবুর ভাসুরের ছেলে সোজা এসে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। প্রথমে তাদের ঘরে প্রবেশ করে। খানিক পরেই বুবুর ঘরে ঢুকে আমাকে বলেন, চলেন মামা!
বুবু তখন এগিয়ে এসে আমার হাতটা কোম্পানি কমান্ডারের হাতে তুলে দিয়ে কেঁদে কেঁদে বলেন, আগে আল্লাহ, পাছে আপনে বাজান! আমার আদরের ছোড ভাইডারে আপনার হাতে সইপ্যা দিলাম...
বলেই বুবু কণ্ঠরুদ্ধ হলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানি কমান্ডার বলেন, আপনি কোন চিন্তা করবেন না চাচি। আমি থাকতে মামার কোন ভয় নাই। বরং আমার সঙ্গে থাকলেই মামা নিরাপদে থাকব। কারণ, বিরিশিরি অনেক দূরে হলেও-এ এলাকার মানুষের কেউ কেউ কিন্তু জানে আপনার বাবার ভূমিকার কথা। আপনার ভাইদের কথাও জানে।
জবাবে বুবুর মুখে আর রা ফুটেনি। কারণ, কোম্পানি কমান্ডার পরম আত্মীয় হলেও তো তার কাছে আজ করুণার পাত্র। আমাকে নিয়ে রওনা হলো ওরা। মনে হলো, ওরা কোন গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে যাচ্ছে। আমি এই প্রথম দেখলাম সশস্ত্র কোন পরিপূর্ণ মুক্তিযোদ্ধা দল। নিরীহ এক হরিণ শাবক হয়ে বাঘের দলের সঙ্গে হেঁটে চললাম আমি। হোসেনপুরের আদু মুন্সির বাজার এলাকা থেকে পায়ে হেঁটে কিশোরগঞ্জের উদ্দেশে হেঁটে চলি। বুবুর ভাসুরের ছেলে, কোম্পানি কমান্ডার আফাজ উদ্দীনকে আমিও তো মামা বলে ডাকি। তিনিও তাঁর দলের সকল সদস্যের কাছে মামা বলে আমাকে পরিচয় করে দেন। বয়সে অনুজ হলেও আত্মীয়তা সম্পর্কে কোম্পানি কমান্ডার যেহেতু আমাকে মামা ডাকেন, সে জন্য মুক্তিযোদ্ধা এ দলের সবার কাছে আমি কমন মামা হয়ে যাই। ফলে শত্রুপক্ষের পরাজিত একজন সৈনিক হয়েও অল্প সময়ে আমি তাদের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।
প্রায় দু’ঘণ্টা হাঁটার পর কিশোরগঞ্জ শহরে ঢোকার পথে ভয়বহ দৃশ্যের শুরুটা দেখলাম। সে দৃশ্য আমার হাঁটার সাথীদের জন্য আনন্দের হলেও আমার জন্য ছিল অত্যন্ত মর্মান্তিক ও চরম কষ্টকর একটা বিষয়। দেখলাম, রাস্তার দু’পাশে রক্তাক্ত মানুষের লাশ। ভয়ে আৎকে উঠে বললাম, রাস্তার দুই পাশে এত মানুষের লাশ পইড়া আছে ক্যান আফাজ মামা?
-মানুষের না তো, ঐগুলো রাজাকারের লাশ।
এ বিশেষ শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার বুকের ভেতরের প্রাণপাখিটাও ছটফট করতে শুরু করে। যতই শহরের ভেতর দিকে এগোচ্ছি, ততই রাস্তার দু’পাশে দেখতে পাচ্ছি লাশের পর লাশ। কোনটা এখনও ছটফট করছে, কোনটা জবাই করা পশুর মতো গোঙাচ্ছে। এসব গোঙানির শব্দ আর তাজা রক্তের ¯্রােতে বাতাস ভারি হয়ে যাচ্ছে। এসব দৃশ্য দেখে আমি আর আমাতে টিকে থাকতে পারিনি। যেনো মৃত্যুর আগেই ভেতরে ভেতরে মরে গেলাম আমি। মৃত্যুদ-াদেশ প্রাপ্ত কয়েদির মতো নির্বাক হেঁটে চলছি তাদের সঙ্গে। সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা দলটির সঙ্গে আমার প্রাণহীন দেহটাই যেন হেঁটে যাচ্ছে। হঠাৎ মামা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, কী মামা! রাজাকারদের লাশ দেখে কেমন লাগতেছে!
-জি মামা!
ফ্যাকাশে মুখে অনেকটা নির্বোধের মতো শব্দটি উচ্চারণ করলাম। আমার বিধ্বস্ত মুখের মানচিত্র থেকে ওই একটি শব্দ শুনেই মামা আমার আন্তর্জগতের বিপন্ন অবস্থাটা সহজেই আঁচ করতে পারলেন। সদ্য স্বাধীন দেশে শত্রুপক্ষের সদস্য হয়েও বিনা শাস্তিতে পার পেয়ে যাব আমি? মনে আমার এমন প্রশ্ন জাগে কখনও। এমন অনেক অধীর জিজ্ঞাসাই মনের ওই অপরাধী আঙিনাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে চলে। একটা প্রশ্ন তখন বার বার আমার মনের ভেতর উচ্চকিত হয়ে উঠল, আর তা হলো, এখানকার রাজাকার বাহিনী কি নিরীহ জনগণের ওপর এত জঘন্য অত্যাচারই করেছে, যার জন্য প্রতিশোধপরায়ণ জনসাধারণ হিংসায় উন্মত্ত হয়ে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠেছে। ভাবতে আমার অবাক লাগে, সতীর্থরা রক্তাক্ত হয়ে ছটফট করছে, অথচ আমি এখনো বেঁচে...! বিরিশিরি এলাকায় থাকলে আমারও অবস্থা কি এমনই হতো? এতক্ষণে সোমেশ^রী নদীর ¯্রােতে অন্যান্য রাজাকারের লাশের সঙ্গে কি ভেসে যেত আমারও লাশ! এসব ভেবে আত্মধিক্কারে একেকবার মনে মনে বলি, তাই বরং ভাল ছিল। তাহলে আর এমন বীভৎস দৃশ্য দেখতে হতো না। এভাবে বেঁচে থেকে দুর্বহ যন্ত্রণা পাওয়ার চেয়ে একটা গুলির আঘাতে যন্ত্রণাহীন মৃত্যু বুঝি অনেক ভাল...। যখন আমি এসব ভাবনার অতলে ডুবে আছি, তখনি আফাজ মামা ডেকে বলে, কী মামা! কেমন লাগতেছে?
না। কোন জবাব আমি দিতে পারিনি। মৃতের মতো আমি তাদের সঙ্গে শহরের পথে হেঁটে চলছি। পথের দু’পাশে স্বপক্ষবাহিনীর সদস্যদের স্তূপীকৃত লাশ। বুঝতে পারলাম, মামা আমাদের পিতা-পুত্রকে যে সম্ভাব্য পরিণতি থেকে আত্মীয়তাসূত্রে বাঁচিয়ে রাখলেন, তা উপলব্ধি করার জন্যই আমাকে সঙ্গে করে এনেছেন। অথচ আমি যে এমন ভয়াবহ দৃশ্য আর দেখতে পারছি না। তবু তাদের সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি। শহরের ভেতরের রাস্তায় মামাদের গন্তব্যে যাওয়ার আগ পর্যন্ত আমার মনের রাজ্যে চলছিল অপরাধবোধে আত্মোপলব্ধিজাত প্রচ- অনুশোচনা। তখন কেবলি মনে হয়েছে, অন্তর্গত লজ্জা-ঘৃণা আর আত্মগ্লানিতে ভেতর রাজ্যের আমি কেবলই কুঁকড়ে যাচ্ছি। আত্মধিক্কারে নিজেকে জাতির কাছে, দেশের কাছে বড় নীচ, বড় ছোট মনে থাকে। এ যে কত বড় শাস্তি -তা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারও উপলব্ধি করার কথা নয়।
সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে মফস্বলের একটি শহর কেন্দ্রে এসে বুঝতে পারলাম, এখানে এত ব্যাপকহারে রাজাকার নিধনের আসল কারণ। এখানকার রাজাকার বাহিনী পাক সেনাদের দোসর হয়ে নিরীহ জগণের জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি করেছিল। সঙ্গত কারণেই রাজাকারদের প্রতি নিপীড়িত আমজনতা ছিল বড় ক্ষুব্ধ। অন্যদিকে নিজেদের কৃতকর্ম সম্পর্কে ওরা ছিল শঙ্কিত। তাই ওরা মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ না করে বরং শহরতলীর এক বিরাট বাড়িতে ওরা সমবেত হয়েছিল। মুক্তিবাহিনীর সম্ভাব্য আক্রমণের গুজব ছড়িয়ে পড়লে, কাপুরুষ রাজাকাররা তাদের সেই গোপন আস্তানায় অস্ত্রশস্ত্র রেখে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যাচ্ছিল।
কিন্তু প্রতিশোধপরায়ণ ক্ষুব্ধ জনসাধারণের হাতে পড়ে তাদের এমন করুণ পরিণতি হয়। জনসাধারণের মামুলি অস্ত্রের আঘাতে ব্যাপকহারে প্রাণ দিতে হয়েছিল তাদের। অল্পসংখ্যক রাজাকার কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণের সৌভাগ্য বরণ করতে পেরেছিল। বিকেলবেলায় মামাদের সঙ্গে ফিরছিলম আমি। সারা পথে আমার মুখে আর কোন রা ফুটেনি। অবশ্য মামা আমাকে বার কয়েক কৌতুক করে খোঁচা দিয়ে বলেছেন, মামা কেমন দেখলেন?
জবাবে আমি কোন কথা বলতে পারিনি। কিভাবে-কোন লজ্জায় উত্তর দেব আমি! আমার ভেতর-দেশে আত্মদহনের প্রকা- অগ্নিকু- তো সব সময় শা শা রবের শব্দাতীত শব্দে জ্বলছিল কেবল। খুব কষ্ট হয় আমার। দেশের কাছে-জাতির কাছে দেবার মতো কী জবাব আছে আমার! যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন এদেশ ও জাতির কাছে করুণার পাত্র হয়েই বাঁচতে হবে। এর যে কী যাতনা-তা আমার মতো ভুক্তভোগীরই কেবল বোঝার কথা।
ঢাকা, বাংলাদেশ মঙ্গলবার ৩০ এপ্রিল ২০২৪, ১৭ বৈশাখ ১৪৩১