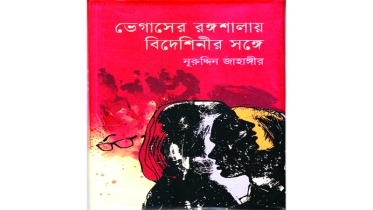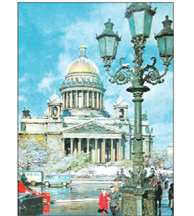
পূর্ব প্রকাশের পর
আমার আর দূরে সরে থাকতে হলো না, আলাউদ্দিনই দূরে সরে গেল। ঐ ঘটনার পর আরও দু’একবার আমার রুমে এসেছে ইলিয়েনা। আলাউদ্দিনের মধ্যে হয়তো অপরাধবোধ ছিল, সে ভালোভাবে কথা বলতে পারেনি ইলিয়েনার সঙ্গে। ইলিয়েনা স্বভাবিকভাবে হাই-হ্যালো বলেছে, অস্বস্তি এড়াতে কিছু একটা অজুহাত দিয়ে বাইরে কোথাও চলে গেছে আলাউদ্দিন। এইসব অস্বস্তিরও শেষ হলো যখন সে এক ফ্লোর নিচে সিঁড়ির পাশের ছোট ঘরটাতে চলে গেল।
শীতের ছুটিতে এবার আলাউদ্দিন দু’বার লন্ডন গিয়েছিল, বাণিজ্য করতে। বাণিজ্যে লক্ষ্মির বসত, তাই সে হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করার বদলে বাণিজ্যে নেমেছে। বেশি ট্রিপ, বেশি প্রফিট। ছুটিতে একবারের বেশি কাউকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দেয় না ডিন অফিস থেকে- আলাউদ্দিনের বেলায় ব্যতিক্রম। তামারা আর ভেরা ওকে সবরকম সহায়তা করে, তাই অনুমতি পেতে কোনো অসুবিধা হয় না আলাউদ্দিনের- সবই দামি দামি উপহারের কেরামতি, সেই সঙ্গে আলাউদ্দিনের ক্যারিশমা আর অভিনয়ের গুণ। একই ক্যারিশমা দেখিয়ে ও সিঙ্গেল রুম বাগিয়ে নিয়েছে। দুর্নীতি জিনিসটা সব জায়গায়ই আছে, সব সিস্টেমেই আছে। তবে সিস্টেমের নিচের দিকে ছোট কর্মচারী, ছোট দুর্নীতি। উপরের দিকে সবই বড় বড়, দুর্নীতিও মেগা সাইজের।
দ্বিতীয়বার সে আর নিয়াজ খান গেল একসঙ্গে, ফিরলো একসঙ্গে। ওদের এবারের প্ল্যানটা অভিনব। আলাউদ্দিনের মিউজিক সেটের সাউন্ড বক্স দু’টো বিশাল। প্রথমে ওগুলোর ভিতর থেকে যন্ত্রপাতি-তারটার সবকিছু বের করে ফেললো ওরা। রাশিয়া থেকে লন্ডন যাওয়ার সময় বাক্সের ভিতরে ভওে নিলো রাশান ক্যামেরা, ক্যাভিয়ারের ক্যান আরও এমন জিনিস যেগুলো রাশিয়ায় খুব শস্তা, কিন্তু বার্লিন কিংবা লন্ডনে বেশি দামে বিক্রি হয়। বর্ডারে ইমিগ্রেশন অফিসারদের ওরা বললো নষ্ট সাউন্ড বক্স মেরামত করতে নিয়ে যাচ্ছে গ্রুন্ডিগ কোম্পানির কাছে। ফেরার পথে ওগুলোর ভিতরে ঠেসে নিয়ে এলো এখানে বিক্রি করার জন্য দামি দামি জিনিস। দ্বিমুখি ব্যবসা, চক্রবৃদ্ধি লাভ! আসা-যাওয়ার পথে দেখি আলাউদ্দিনের রুমের সামনে ক্রেতাদের ভিড়। ওদের দেখলেই চেনা যায়। সারাক্ষণ সিঁড়ির ল্যান্ডিংয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে।
এখন আলাদা রুমে থাকি আমরা দুজন, উপর-নিচে দুই ফ্লোরে। আমাদের মধ্যে আগের মতো হৃদ্যতা না থাকলেও যোগাযোগ আছে, দূরত্বও তৈরি হয়েছে কিছুটা। দেখাসাক্ষাৎ হয় সবসময়, কথাবার্তা হয়। আলাউদ্দিনের সব কথাই এখন ব্যবসা, টাকা আর ডলার ঘিরে। এর মধ্যেই পরীক্ষা আসে। আমরা পরীক্ষা দিই। পরীক্ষার একটা নিয়ম হলো একবারে কেউ পাশ করতে না পারলে দ্বিতীয়বার এমনকি তৃতীয়বারও চেষ্টা করতে পারে। অধ্যাপক এক সপ্তাহ পরপর পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। এরকমই এখানে নিয়ম। ইথিওপিয়ার তেখলে আর আলজিরিয়ার আলীকে দেখা যেত একই পরীক্ষা দু’তিনবার করে দিচ্ছে। এই দলে মাঝে মাঝে আলাউদ্দিনকেও দেখা যেতে লাগলো। তবে আমি জানি মেধার অভাবে না, মেধা ওর যথেষ্টই আছে, শুধু সময়ের অভাবে আলাউদ্দিনের এই অবস্থা। ওর বেশিরভাগ সময় চলে যাচ্ছে ব্যবসার নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কার করতে আর টাকা গোনার পিছে সময় দিতে দিতে। টাকা গোনা নিয়ে মজার এক ঘটনা ঘটেছিল একদিন।
আলাউদ্দিনের পাশের রুমেই থাকতো আমাদের সহপাঠি সাত ফুট লম্বা সেই বিগ জো আর ওর রুমমেট আফগানিস্তানের শাহ গুল। জো আর গুল দু’জন ছিল দুই রকম, সম্পূর্ণ উল্টো স্বভাবের। বিগ জো ছুটির দিনে গলা পর্যন্ত ভোদকা খেয়ে খুব হৈচৈ করতো। তবে এগ্রেসিভ ছিল না জো, ফানি ছিল খুব, মজা করতো। সামনে যাকেই পেত তাকে বলতো আয় পাঞ্জা লড়ি! ঐ সাত ফুট দৈত্যের সঙ্গে কে পাঞ্জা লড়বে? ওকে করিডোরে দেখলেই সহপাঠিরা ভয়ে পালাতো, রুমের দরজা বন্ধ করে দিত- হোক মজার, তবু দৈত্য তো ! আর জো দৌড়ে গিয়ে দরজায় দুমদুম কিল মেরে অনুরোধ করতো- আচ্ছা, পাঞ্জা লড়তে হবে না, আয় গল্প করি...।
গুল বেচারা ছিল শান্ত স্বভাবের আর লেখাপড়ায় খুব ভালো। অ্যালকোহল স্পর্শ করতো না, চা বানাতো, আর নিজে রান্নাবান্না করে মাংস-রুটি দিয়ে চা খেতো। শীতের দিনে ওকে দেখতাম ইয়া বড় এক কেতলি হাতে কিচেনে যাচ্ছে আর আসছে। দেখা হলে জিজ্ঞেস করতাম কী রে গুল, চা হচ্ছে নাকি?
- হচ্ছে, খাবি আয়। সবসময় ডাক দিত গুল। মাঝে মাঝে যেতাম ওর রুমে। ওর চায়ের স্বাদটা ছিল চমৎকার, বানানোর কায়দাও অদ্ভুত। চা-পাতা, চিনি, দুধ সব একসঙ্গে দিয়ে অনেকক্ষণ জ্বাল দিত প্রথমে। বেশ ঘন হয়ে এলে তখন কেতলিতে ছেড়ে দিত এক মুঠো এলাচ। গ্লাসে যখন ঢালতো সারা ঘরে ভুরভুর করতো এলাচের গন্ধ। আয়েশ করে চুমুক দিত গুল, আমাকে জিজ্ঞেস করতো চা কেমন হয়েছে রে?
আমি বলতাম দারুণ! আমার দেশে ঘন দুধের সর দিয়ে বানায় মালাই চা। আর তোরটা হয়েছে মালাই-এলাচ-গুলচা।
প্রাণ খুলে হাসতো গুল ওর চায়ের প্রশংসা শুনে। ধীরে ধীরে অবশ্য ওর হাসিটা মলিন হয়ে গেল। ১৯৭৯ সালে আমরা যখন তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, সেই বছর থেকে আফগানিস্তানে সৈন্য পাঠাতে শুরু করলো সোভিয়েত ইউনিয়ন। মিডিয়া ছিল নিয়ন্ত্রিত। সেখানে আফগান যুদ্ধের বিষয়ে তেমন কিছু শোনা যেত না। শাহ গুল দেশের চিঠি পেত, একবার সে ঘুরেও এলো দেশ থেকে। ওর কাছেই শুনলাম তার দেশের লোকেরা সোভিয়েত বাহিনীকে দখলদার বাহিনী হিসেবে দেখতে শুরু করেছে এবং যুদ্ধ করছে তাদের বিরুদ্ধে। প্রচুর হতাহত হচ্ছে দুই পক্ষেই। গুলের কথার প্রমাণও পেয়ে গেলাম কিছুদিনের মধ্যে।
আমার প্রথম বর্ষের রুমমেট পাভেল যাকে বন্ধুরা ডাকতো পাশা, যার সঙ্গে আমি টেবিল টেনিস খেলতাম প্রায়ই, সেই পাশার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি। হঠাৎ একদিন ভার্সিটির করিডোরে দেখা হয়ে গেল। চেহারা তেমনই আছে, কপালের উপরে তেমনি একগোছা চুল, শান্ত একজোড়া চোখ, একটা হাত শুধু নাই, আর মুখের হাসিটা উধাও হয়ে গেছে। আমি বিস্ময়াহত চোখে তাকিয়ে থাকলাম আর মনে মনে ভাবলাম যুদ্ধ মানুষের মুখের হাসি এভাবেই কেড়ে নেয় তাহলে! হ্যান্ডশেক করে হাতটা আর ছাড়লো না পাশা, একপাশে টেনে নিয়ে গেল আমাকে। চারপাশে সতর্ক চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললো ‘আমি আফগানিস্তানে ছিলাম। কাউকে বলা বারণ। তোকে বিশ্বাস করে বললাম।’ এরপর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলতে লাগলো ‘পুরোনো হোস্টেলে এসে উঠেছি। এখন আবার ভর্তি হবার অনুমতি পেয়েছি। আমার রুম নাম্বার একশো পনেরো, দোতলায়। তুই আসিস মাঝে মাঝে, টেবিল টেনিস খেলবো আমরা আগের মতো। আমি এখনো খেলতে পারি।’ বলে অক্ষত ডান হাতটা দেখালো পাশা, যেটা এতক্ষণ আমি ধরে ছিলাম। এবার এক চিলতে হাসিও ফুটলো ওর মুখে, বড় মলিন সেই হাসি।
দিন দুয়েক পর উইক এন্ডে পুরোনো হোস্টেলে গেলাম। কিছুক্ষণ টেবিল টেনিস খেলা হলো। এক হাতেও ভালোই খেলছিল পাশা। আমি অবশ্য খুব জোরে চাপ মারছিলাম না, যদিও আমার খেলা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে এখন। ইদানিং প্র্যাকটিস করছি সপ্তাহে দু’দিন বাধ্য হয়ে। ফিজিক্যাল এডুকেশনের ক্লাসগুলো ফাঁকি দিচ্ছিলাম খুব- একদিন ইন্সট্রাকটর ডেকে পাঠালেন। বললেন, শোনো অপু, তুমি অলস ছেলে বুঝতে পারছি, তবে এতটা ফাঁকিবাজি চলবে না। তোমাকে আমি একটা অফার দিতে পারি।
- কী অফার গেনাইদি লিওনিদোভিচ?
- আমি খবর পেয়েছি তুমি ভালো টেবিল টেনিস খেলো। এখন থেকে সপ্তাহে একদিন প্রথম বর্ষের ছেলেমেয়েদের টেবিল টেনিস শেখাবে। তাহলে তোমাকে ক্লাস করতে হবে না, ক্লাস মাফ। রাজি?
- ‘রাজি।’ আমি সাথে সাথে বললাম, ‘তবে ক্লাসটা বিকেলের দিকে করলে হয় না? সকালে ঘুম থেকে উঠতে আমার দেরি হয়ে যায়।’
একটু ভেবে নিয়ে ইন্সট্রাকটর বললেন, ‘ঠিক আছে, আগামি সোমবার বিকেল চারটায় ক্লাসের পর তুমি ইনডোর কমপ্লেক্সে চলে এসো। আমি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসবো।’ সেই থেকে আমি প্রথম বর্ষের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে টেবিল টেনিস খেলে আসছি প্রত্যেক সপ্তাহে দু’দিন।
আজকে খেলা শেষে আমি আর পাভেল একটা কফি শপে গিয়ে বসলাম। সেখানেই ওর যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বললো পাভেল। আমাদের ভার্সিটি থেকে দশজনের ছোট একটা দলকে রিক্রুট করা হয়েছিল যুদ্ধের শুরুতেই, তাদের মধ্যে পাভেলের নামটা ছিল। দুই বৎসরের বাধ্যতামূলক আর্মি ট্রেনিং করা ছিল ওর। রিক্রুট করার পরে এক মাসের সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং দিয়ে ওকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় আফগানিস্তানে, সরাসরি যুদ্ধের মাঠে। ‘আমার প্রথম অপারেশনই ছিল পানশির ভ্যালিতে, আর সেখানেই...’ বলতে থাকে পাভেল।
পানশির ভ্যালি! নামটা শুনেই আমি অন্যমনস্ক হয়ে যাই। পাভেল যুদ্ধের বর্ণনা দিতে থাকে- কীভাবে ওরা মুজাহিদিন বাহিনীর অ্যামবুশে পড়েছিল, কীভাবে এয়ার সাপোর্ট পেয়ে অ্যামবুশ থেকে বেরিয়ে এসেছে গুলি করতে করতে আর তক্ষুণি একঝাঁক বুলেট এসে লাগে ওর বাম পাঁজর আর বাঁ হাতে। কীভাবে হেলিকপ্টারে ওকে কাবুল নিয়ে এসেছিল, সেখানে চিকিৎসা দেয়, পরে লেনিনগ্রাদের হাসপাতালে সে সুস্থ হয়ে ওঠে...শুধু বাঁ হাতের হাড় ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে, কেটে ফেলতে হয়েছে হাতটা কব্জির উপর থেকে- এসবই অনুপুক্সক্ষ বর্ণনা করে পাশা...আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। মগজ পর্যন্ত পৌঁছায় না। মগজে একটা নাম খেলা করতে থাকে শুধু... আবদুর রহমান! সেই আবদুর রহমান, যার কথা পড়েছি আমি সৈয়দ মুজতবা আলীর ‘দেশে-বিদেশে’ গল্পে। যার শরীরটা পাহাড়ের মতো, হাতের আঙুলগুলো মর্তমান কলার মতো। হুজুর যদি আদেশ করেন, তাহলে সে রান্নাবান্না থেকে শুরু করে খুনখারাবি পর্যন্ত সব করতে পারে। সেই আবদুর রহমান, কাজের অবসরে যে লেখককে তার জন্মভূমি পানশিরের গল্প শোনতো, স্মৃতির আবেগে বলে উঠতো ‘ইনহাস্ত ওয়াতানাম’! এই আমার জন্মভূমি! সেই আবদুর রহমানের পানশিরে যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হয়ে ফিরে এসেছে পাভেল। কে জানে আবদুর রহমানের পরের প্রজন্ম হয়তো এখন লড়াই করছে পানশিরে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে। হয়তো তার ছেলের ছেলে কিংবা তাদেরই কারো গুলির আঘাতে হাত হারিয়েছে পাভেল- কে বলতে পারে!
কিন্তু পাভেলের দুঃখটা অন্য জায়গায়। যুদ্ধাহত সৈনিক সে, নিজের দেশের পক্ষে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণপন লড়াই করে আহত হয়েছে। মারাও যেতে পারতো। ভাগ্যগুণে বেঁচে ফিরেছে। অথচ তার এই বীরত্বের কোনো মূল্যই যেন নেই। রাশিয়ার মিডিয়ায় একটা শব্দও উচ্চারিত হয় না তার মতো যুদ্ধাহত সৈনিকদের নিয়ে। অথচ পাভেলের আগের প্রজন্মে যারা জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তারা বীর হিসেবে সম্মানিত। তাদের বীরত্ব নিয়ে গল্প, উপন্যাস, গান, কবিতা কত কী লেখা হয়েছে, সিনেমাও তৈরি হয়েছে অনেক।
অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন তার আফগান যুদ্ধফেরত সৈনিকদের বীরত্বের স্বীকৃতি দেওয়া দূরের কথা, তাদের যেন অস্বীকার করতে পারলেই বাঁচে। কারণটা পাভেল জানে। স্টেট পলিসি। কিন্তু কেন এই পলিসি তা সে বুঝতে পারে না। আফগানিস্তানে যুদ্ধ হচ্ছে এবং রুশ সৈন্য হতাহত হচ্ছে- এই কথাটাই নাগরিকদের জানতে দিতে চায় না তার দেশ। একে হয়তো সমাজতন্ত্রের পরাজয় হিসেবে দেখছে কর্তৃপক্ষ, তাই আড়াল করতে চাচ্ছে। তবে একটু একটু করে জানছে মানুষ।
পাভেলের কথা শুনে বাকুর শিক্ষক কিরিলের কথা আমার মনে পড়ে যায়- বুকে অনেক পদক নিয়ে মঞ্চে বসে আছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওয়ার হিরো কনস্তানতিন কিরিল। আমি পাভেলের দুঃখটা বুঝতে পারি। গলায় ক্ষোভ নিয়ে পাভেল বলে- ‘এই যুদ্ধই আমাদের কাল হবে।’ সামনে ঝুঁকে আসে সে, ডানে বাঁয়ে তাকায়, তীব্র চাপা কন্ঠে আবার বলে, ‘এই আফগান যুদ্ধই আমাদের ধ্বংস ডেকে আনবে, তুই দেখিস অপু...।’ ওর মুখটা লাল হয়ে যায় ক্ষোভে দুঃখে।
আমি একটা হাত রাখি আমার বেলারুশ বন্ধু পাভেলের অক্ষত হাতের উপর। এখন নতুন করে ভর্তি হয়ে ও আমার সহপাঠি হয়েছে। আগে ছিল এক ক্লাস উপরে। আমি টের পাই ওর হাতটা একটু একটু কাঁপছে রাগে, দুঃখে আর ক্ষোভে। যুদ্ধ নিয়ে অনেক কথা হয় আমাদের। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কথাও চলে আসে। পাভেল ওর বাবার মুখে শুনেছে। আমি আমার যুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা বলি, নিজের চোখে দেখা সার সার মৃতদেহের কথা বলি... দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকা বস্তি আর বস্তিবাসির মৃত্যুচিৎকারের কথা শুনে পাভেল বলে এইসব দৃশ্য তাকেও দেখতে হয়েছে আফগানিস্তানে। ও জিজ্ঞেস করে, ‘এইসব দৃশ্য দেখে তোরা- বাঙালি ছেলেমেয়েরা কী করেছিলি, চুপচাপ বসে ছিলি?’
- না, আমরা যুদ্ধ করেছিলাম।
- আফগানরাও যুদ্ধ করছে।
- দু’টো যুদ্ধ হয়তো একরকম না রে পাশা।
- ‘সব যুদ্ধই এক’, তিক্ত কন্ঠে পাশা বলে, ‘যুদ্ধ মানেই ধ্বংস আর ধ্বংস! এই যুদ্ধ আমাদের শেষ করে দিচ্ছে!’
দাভিন্সির হারানো ম্যাডোনা
প্যারিসের যেমন লুভর মিউজিয়াম, লেনিনগ্রাদের তেমনি হেরমিতাজ। একদিন গেলাম সেখানে ইলিয়েনার সঙ্গে। ওর সঙ্গে লেনিনগ্রাদের অনেক জায়গা এর মধ্যে ঘোরা হয়ে গেছে আমার, অনেক সিনেমা দেখা হয়েছে, শহরের অপূর্ব সুন্দর পার্কগুলোতে আমাদের দুই জোড়া পায়ের ছাপ পড়েছে বহুবার।
অনেকদিন ধরেই লেনা বলছিল আমাকে একটা মজার পেইন্টিং দেখাতে নিয়ে যাবে। লিওনার্দো দা’ভিন্সির পেইন্টিং। কী পেইন্টিং সেটা আর বলতে চায় না। জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয়- ‘ওখানে গেলেই দেখতে পাবে, বলে দিলে আর মজা কীসের!’
দা’ভিন্সির মোনালিসা, লাস্ট সাপার, ভিট্রুভিয়ান ম্যান- এইসব ছবি আমি দেখেছি। নতুন কী দেখাবে ভেবে পাই না। ইলিয়েনা বলে এগুলো না, অন্য ছবি। ওর চোখেমুখে কেমন একটা রহস্য রহস্য ভাব- মেয়েদের সিন্দুকে কত যে রহস্য!
সেদিন গেলাম আমরা বাসে চড়ে। নেভার ওপারে বিখ্যাত এই আর্ট মিউজিয়াম। বিল্ডিংটাই কী ভীষণ জমকালো! এটা আগে ছিল জারদের উইন্টার প্যালেস। ভিতরে ঢুকে আমার তো মাথা ঘুরে গেল। কত কী দেখার আছে! কত দেশের শিল্পীদের পেইন্টিং, কত ভাস্কর্য! একদিন কেন, এক মাসেও পুরোটা দেখে শেষ করা যাবে না- এতগুলো ঘর!
ঘুরতে ঘুরতে আমরা দা’ভিন্সির ছবির সামনে এসে হাজির হলাম। ছবির নাম ফুল হাতে ম্যাডোনা। মাতা মেরীর ছবি, তাঁর কোলে শিশু যীশু। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে ছবি। কিন্তু দা’ভিন্সির বিশেষত্বই এখানে- তিনি এমনভাবে ছবিটা এঁকেছেন যে একে ধর্মীয় ছবি বলে মনেই হয় না।
ছবিতে মেরীর চোখে যে মাতৃ স্নেহ, মুখে যে হসি- তা হতে পারে সন্তান কোলে যে কোনো মায়ের হাসি। বাঙালি মায়ের হাসি বললেও কেউ আপত্তি করবে না। হাসিমুখে কোলের শিশুকে একটা ফুল দিচ্ছেন একজন মা। দু’জনের মাথার উপরেই দুটো সাদা চক্র এঁকে দিয়েছেন দা’ভিন্সি। সেই সময়ের প্রথা অনুযায়ী এই চক্র দিয়ে ধর্মীয় ছবি বুঝানো হতো। এটুকু বাদ দিলে পুরো ছবিটাই মা আর সন্তানের আনন্দঘন মুহুর্তের অপরূপ এক পেইন্টিং। ছবিটা সুন্দর। এর পিছনের ইতিহাস আরও সুন্দর, আরও চমৎকার। ছবির সামনে দাঁড়িয়ে সেই চমৎকার গল্পটা বললো ইলিয়েনা আমাকে... ‘যুবক লিওনার্দোর সঙ্গে সবসময় থাকতো একটা নোটবই।’ শুরু করলো ইলিয়েনা। ‘নোটবইয়ের এক কোনায় তিনি লিখে রেখেছিলেন এই কথাগুলো- দুটো ম্যাডোনা আঁকতে শুরু করেছি। সময়টা ১৮৭৮ সাল। এর বছর চারেক পর আমরা দেখি মিলানের রাজ দরবারে যাচ্ছেন লিওনার্দো, ডিউকের আমন্ত্রণে। কোন্ কোন্ ছবি সঙ্গে নিচ্ছেন, তার একটা লিস্ট করেছেন তিনি। এই লিস্টের এক কোনায় আবার দেখা যায় তাঁর মন্তব্য- একটা ম্যাডোনা আঁকা শেষ। ম্যাডোনা তো এঁকে শেষ করলেন লিওনার্দো। কিন্তু কোথায় গেল ছবিটা, কার কাছে বিক্রি করলেন তিনি, কিছুই আর এরপরে জানা যায় না। হঠাৎ করেই যেন হারিয়ে গেল দা’ভিন্সির ম্যাডোনা!’ একটু দম নিল ইলিয়েনা।
‘...প্রায় সাড়ে তিনশো বছর পরের কথা।’ আবার বলতে থাকলো সে। ‘১৮২৪ সাল- জারের রাশিয়া। ভোলগা নদীর তীরে ছোট্ট শহর আস্ত্রাখান। শহরের প্রান্তে তাঁবু ফেলেছে সার্কাস পার্টি। ইতালি থেকে এসেছে তারা, সার্কাস দেখাচ্ছে। বড় তাঁবুটার সামনে এসে দাঁড়ালো তিন ঘোড়ায় টানা একটা ত্রইকা। ত্রইকা থেকে নামলো দীর্ঘকায় এক লোক। তার পায়ে হাইবুট, পায়ে ওভারকোট, ঘন ভুরুর নিচে চোখজোড়ায় কঠোর চাহনি। আস্ত্রাখানের কোটিপতি সাপোজনিকোভ- সার্কাস দেখতে এসেছে সে।
অনেক উঁচুতে দড়ির উপর টাট্টু ঘোড়া। (চলবে)