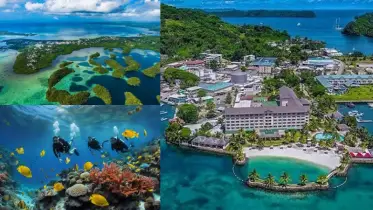ব্যক্তির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থক
ব্যক্তির স্বাধিকার ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থক হলেও এই দুটি বোধের ভিতর প্রকরণগত ও প্রায়োগিক পার্থক্য রয়েছে। যাপিতজীবনে বিভিন্ন স্তর সচেতনভাবে অতিক্রম করতে করতে একজন চেতনাজাগার মানুষ নিজে নিজেই এ দুইয়ের দূরত্ব ও নৈকট্য উপলব্ধি করে।
স্বাধিকার বলতে প্রাথমিকভাবে বোঝায় নিজের অধিকার। জন্মের পর থেকে একটি পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিমানুষ কিছু অধিকার লাভ করে। যেমন-আহার, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সদাচারী সুকৃতি ইত্যাদি। এই অধিকার মূলত দুই রকম। প্রথমত মূর্ত অধিকার ও দ্বিতীয়ত বিমূর্ত অধিকার। মূর্ত ও বিমূর্ত এই দুই ধরনের অধিকার ব্যক্তি যদি শৈশব থেকে বেড়ে ওঠার ধাপে ধাপে পেয়ে যায়, তাহলে মানুষ হিসেবে তার বেড়ে ওঠার পর্যায়গুলো সুষম হতে থাকে। কিন্তু যদি শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণের পূর্ব পর্যন্ত কোনো ব্যক্তিমানুষ একটি সমাজে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তার মধ্যে অন্তত দু’ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়।
একটি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে অধিকার না পাওয়ার বেদনা ও হতাশা; এবং অন্য প্রতিক্রিয়া হচ্ছে সে অধিকার অর্জন ও আদায়ের জন্য অঙ্গীকার। যে সমাজ বা রাষ্ট্রে ব্যক্তি শৈশব থেকে পরম্পরাগত অধিকার পেয়ে যায়, সেই সমাজে ব্যক্তি তার জীবনযাপনের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে তার করণীয়টুকুও বুঝে নেয়। এই বুঝে নেওয়ার ক্ষেত্রেও দুই ধরনের মানসিকতা কাজ করে। কেউ কেউ সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে এক ধরনের সমঝোতার মাধ্যমে এগিয়ে গিয়ে নিজের অধিকার ও স্বাধীনসত্তার বিষয়টি নিজেই লঙ্ঘন করে। এটা এক ধরনের নমনীয় মনোভাব। অন্যদিকে যারা অনমনীয়ভাবে নিজের অধিকার ও সমাজের সকল সুষম অধিকার ভারসাম্যভাবে অর্জন করতে চায়, তারা স্বাধীনসত্তা বিকাশের পথে পা বাড়ায়। নিজের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার মধ্যে এই সূক্ষ্ম সম্পর্কটি বুঝতে হলে ব্যক্তিকে সদাচারী সুকৃতি ও সংস্কৃতির বিষয়টিও সচেতনভাবে বুঝে নিতে হয়।
প্রায় দুশো বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হতে হতে বাঙালি সমাজের মধ্যেও স্বাধিকার ও স্বাধীনতার বোধ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রজন্মের বাঙালির মধ্যে আমরা এই সাংস্কৃতিক বোধ ও লড়াইয়ের বিভিন্ন রকম সূচনা হতে দেখি। এমনকি পলাশীর প্রাঙ্গণে ইংরেজদের হাতে বাঙালি তার ব্যক্তিস্বাধীনতা ও জাতিস্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর থেকে, এই অনমনীয় চেতনা, যার অন্য নাম বিদ্রোহ, তারও বিকাশ ঘটতে দেখি। এই স্বাধিকার স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের সঙ্গে সূচনা লগ্ন থেকে বাঙালির ভাষা আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত যারা নানাভাবে নিজের বোধ, উপলব্ধি ও কর্তব্যকে শনাক্ত করতে পেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাদের সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম।
॥ দুই ॥
উপমহাদেশের বিভক্তির মাধ্যমে যে দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তার একটি পাকিস্তান। এই রাষ্ট্রটি শুরু থেকে অবাস্তব রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এর মূল কারণ তৎকালীন পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষিক দূরত্ব, সাংস্কৃতিক দূরত্ব এবং পূর্ব অংশের ওপর পশ্চিমা অংশের প্রাধান্যকামিতার মনোভাব। তথাকথিত পাকিস্তানের স্বাধীনতার পরপরই, কিংবা তারও অব্যবহিত আগে, বঙ্গবন্ধু এই বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। কাজেই তাঁর সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের শুরু থেকে বাঙালি জাতি স্বাধিকার ও স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়েছে। ভাষিক লড়াই ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের মাধ্যমে তা পঞ্চাশের দশকের শুরুতেই, কিংবা তারও আগে, সুপ্রকাশিত।
স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও সাংস্কৃতিক লড়াইয়ের পথ ধরে বঙ্গবন্ধু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির দিকে এগিয়ে যান। তিনি তাঁর রাজনৈতিক অঙ্গীকার ও করণীয়কে শনাক্ত করেন। ফলে পঞ্চাশ থেকে ষাটের দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি ব্যক্তিবাঙালি ও জাতিবাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য যে লড়াই শুরু করেন তার স্তরসমূহ তাঁকে শনাক্ত করতে হয়। তিনি বুঝেছিলেন যে, এই স্তর শনাক্ত সম্পূর্ণ হলে বাঙালির স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে। এই তাত্ত্বিক পথে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এগিয়েছিলেন তিনি তাঁর মৌলিক বোধ থেকে। ফলে তাঁর সাংস্কৃতিক লড়াই শেষ পর্যন্ত অর্থনৈতিক লড়াইয়ে রূপান্তরিত হয়। এ পর্যায়ে তিনি সমন্বিতভাবে ছয়দফা আন্দোলন ঘোষণা করেন যা ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের পথ ও বিজয় সুনিশ্চিত করে। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনন্য ও শেষাবধি অনাপোষী।
রাজনীতির বাঁকে বাঁকে তিনি বাঙালির ব্যক্তিক অধিকার ও সামষ্টিক অধিকার অর্জনে সার্বভৌম মুক্তির দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন। এটি বাঙালির ইতিহাসে অভূতপূর্ব ও দৃষ্টান্তরহিত। এখানেই তার অনন্যতা।
॥ তিন ॥
ব্যক্তিতাবোধ কিংবা জাতীয়তাবোধ হঠাৎ কোনো ঘোষণা দিয়ে বা আধিপত্যবাদী নির্দেশনা বা হুকুমজারি করে সৃষ্টি হয় না। প্রাণের বিবর্তন তথা মানববিবর্তনের পথ ধরেই পৃথিবীর এক এক অঞ্চলে এক এক ধরনের জীবন প্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে এক এক ধরনের নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক, ব্যবহারিক, সামাজিক ও আচরণগত অনন্যতা ও বৈপরীত্যের বিকাশ হতে থাকে। ফলে উত্তরমেরুর মানুষের পরিচয় দক্ষিণমেরুর মানুষের প্রায়োগিক পরিচয় থেকে মেরুদূর, যদিও তাদের অভিন্ন পরিচয় তারা মানুষ। এই মানুষের মধ্যে উত্তরমেরু থেকে দক্ষিণমেরুর মধ্যে অন্য যে সব বিভিন্ন গোত্রীয় ও জাতিগত মানবস্বরূপ বিকশিত হয়েছে তাদের চলার ধরন, বলার ধরন, খাদ্যের ধরন, বাসস্থানের ধরন, আনন্দ-বেদনার ধরন ও অভিব্যক্তির ধরন এক নয়। এটাকেই বলা হয় খুব সহজ কথায় সাংস্কৃতিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষিক ও জাতিগত বৈচিত্র্য ইত্যাদি। এই জাতিগত বৈচিত্র্যের মধ্যেই এক ধরনের মানবিক ঐক্য আবিষ্কার করে পৃথিবীব্যাপী মানুষের নান্দনিক ঐক্য শনাক্ত করা হয়। ফলে একদিনে বা হঠাৎ আদেশ জারি করে জাতীয়তাকে বা ব্যক্তিতাকে তার নিজস্ব পরিচয় থেকে অন্য পরিচয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।
ব্যক্তিবাঙালি ও জাতিবাঙালি এই দুই পরিচয়ে বাংলাদেশ নামক বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের মানুষেরা ইতিহাস পূর্বকাল থেকে অভিন্ন বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এই জাতিসত্তাকে সংকীর্ণ অর্থে শুধু ভূমিকেন্দ্রিক জাতীয়তা নামে পরিচিত করা সংর্কীণতা ও কূপম-ূকতার পরিচায়ক। পৃথিবীতে এক জাতিসত্তার মধ্যেও অনেক রাষ্ট্রের উদ্ভব দেখা যায়। যেহেতু জাতিসত্তার পরিচয় মূলত ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক, সেহেতু পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলেও একই জাতীয়তার পরিচয় প্রসারিত রয়েছে। জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের জাতীয়তার পরিচয় ইতিহাস পূর্বকাল থেকে বেড়ে ওঠা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাহাত্তরের সংবিধানে এটি সঙ্গতভাবেই সমুচ্চারিত ও গৃহীত।
॥ চার ॥
পরিশেষে বলতে চাই, ‘জয় বাংলা’ ও ‘বাঙালির জয়’ এই উচ্চারণ নিয়ে জাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশে যে বাঙালি জাতীয়তাবোধ তার স্বাধীনসত্তার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে তা অনাগতকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। আমাদের অতীত ইতিহাসই তার প্রমাণ। আমরা দেখেছি ইতিহাস পূর্বকাল থেকে এই বাংলাদেশে বিভিন্ন হানাদার লুটেরা আধিপত্যবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শত্রুরা আঘাত হেনেছে। কেউ কেউ এই মাটি ও সংস্কৃতির সঙ্গে অভিন্নভাবে বিলীন হয়ে গেছে। বাংলা ও বাঙালির বহতা সংস্কৃতি এভাবে বৈশি^ক সংস্কৃতির রূপ ধারণ করেছে। কিন্তু বাঙালির স্বাতন্ত্র্যসূচক ব্যক্তি ও জাতি পরিচয়কে কেউ ধ্বংস করতে পারেনি। আগামীতেও পারবে না। আমাদের জাতীয়তার এই সদাচারীবোধ ও নান্দনিক বিবর্তনকে আমাদেরকেই অব্যাহত রাখতে হবে। এর মূল প্রেরণা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সাংবিধানিক দর্শন। এটাকে আমরা বলতে চাই ‘সংবিধান নান্দনিকতা’। আসলেজাতিরাষ্ট্র বাংলাদেশের সংবিধানে যে নান্দনিক ও মনোলীন মানব ঐক্যের ধারণা অন্তর্বয়িত, তা পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব।
লেখক : কবি, মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি