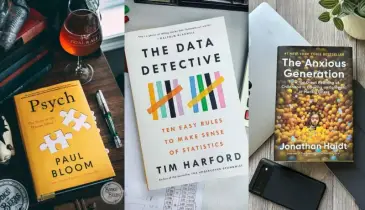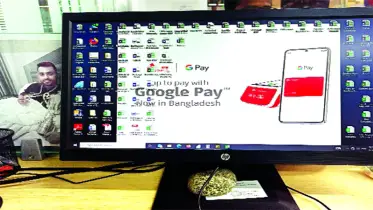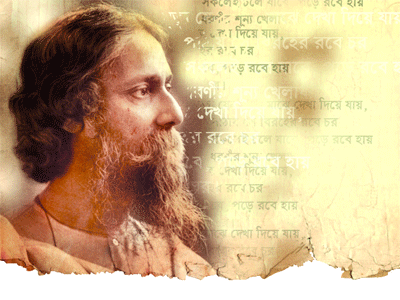
‘নদী যেমন কাটাখালের মতো সিধে চলে না’, তেমনি ছন্দ এঁকেবেঁকে নানা মূর্তি, নানা রূপ ধারণ করে থাকে। একটা শ্রুতিগ্রাহ্য ছন্দোস্পন্দ ভেদ করে কবিতা তার মর্মসত্যকে বয়ে নিয়ে যায় সুনির্দিষ্ট জায়গায়। চর্যাপদ থেকে শুরু করে একুশ শতকের কবিতার শিরা-উপশিরায় নিরন্তর বইছে কমবেশি ছন্দস্রোত। চর্যাপদে রয়েছে প্রতœ মাত্রাবৃত্তের আভাস। সংস্কৃত মাত্রাবৃত্ত রীতির পাদাকুলক [প্রাকৃত পদ্ধতির বা পজ্ঝটিকা] বন্ধের আশ্রয়েই চর্যাপদের ছন্দ নির্মিত হয়েছে। মধ্যযুগে, বড়ু চন্ডীদাসের [আনুমানিক ১৩৭০-১৪৩৩] ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে সর্বপ্রথম অক্ষরবৃত্ত পয়ারের উদ্ভব লক্ষণীয় :
১. লবঙ্গ দোলঙ্গ খোঁপা বান্ধিআঁ উল্লাসে।
গুলাল মালতী-মালে করিল বিলাসে ॥
[বৃন্দাবন খ-]
২. মঙ্গল পায়িলে হয়ে চিত্তের সো আথে।
তবে সি মেলিব এথাঁ প্রিয় জগন্নাথে ॥
[বংশী খ-]
৩. গঙ্গাজলে পৈস গলে কলসী বান্ধিআঁ।
[দানখ-]
বিজয়গুপ্ত, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, মুকুন্দরাম, আলাওল, ভারতচন্দ্র প্রমুখ কবিগণ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের শাসনেই শাসিত ছিলেন। তাঁদের ছন্দের কায়াকাঠামোতে কোথাও যেন ফাঁক ছিল। আর সেই ফাঁক পূরণে যাঁর অবদান অপরিসীম তিনি আধুনিক কবিতার জনক মাইকেল মধুসূদন দত্ত [১৮২৪-১৮৭৩]। তিনি তাঁর ‘পদ্মাবতী’ [১৯৬০] নাটকে ও ‘মেঘনাদ বধ’ মহাকাব্যে [১৮৬১] প্রয়োগ করলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত ছকবাঁধা পদান্তিক যতি ও মিলকে অগ্রাহ্য করে তিনি তাঁর কাব্যে, নাটকে আমন্ত্রণ জানালেন মিলহীনতা, যতির স্বাধীনতা ও প্রবহমানতা-কে। প্রথমবারের মতো ছন্দোমুক্তির দরোজা খুলে দিয়েছিলেন তিনিই। অমিত্রাক্ষর ছন্দ অক্ষরবৃত্তেরই আরেক রূপ। ‘অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে মাইকেল অমিত্রাক্ষরের নতুনরূপে ভূষিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাকেই দিলেন মুক্তকের নতুন পোশাক’। [ছন্দের ঘরবাড়ি, মুজিবুল হক কবীর, ভূমিকা- আবদুল মান্নান সৈয়দ-পৃ.১৬] রবীন্দ্র-প্রবর্তিত মুক্তক অক্ষরবৃত্তের নেপথ্যে হয়তোবা ক্রিয়াশীল ছিল ‘অমিত্রাক্ষর’ ও ‘গৈরিশ ছন্দ’। ‘অমিল মুক্তকের সঙ্গে সমিল মুক্তক ছন্দও তিনি সৃষ্টি করলেন।’ মধ্যযুগে অনেক কবিই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত রহস্য উন্মোচন করতে পারেননি। মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র [১৭১২-১৭৬০] ছন্দসচেতন কবি। দু’জনেই মাত্রাগত বিন্যাস, যতিস্থাপন ও পর্বগঠন নিয়ে নানা সমস্যায় ভুগেছেন। এমনকি আধুনিক যুগে মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাত্রাবিন্যাস ও যতিস্থাপনে ত্রুটির উর্ধে ছিলেন না। ভারতচন্দ্র তাঁর ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে সাত অক্ষরের পরে যতিস্থাপন করেছেন :
কান্দে রাণী মেনকা চক্ষুর জলে ভাসে।
নখে নখে বাজায়ে নারদমুনি হাসে ॥
দুটো পঙ্ক্তিতেই রয়েছে সাত অক্ষরের পরে যতি-যা এ ছন্দের স্বভাব-বিরুদ্ধ। মধুসূদন এ অসম সংখ্যক মাত্রার পরে যতিস্থাপন করতে দ্বিধাবোধ করেননি :
১. চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ, [মেঘনাদবধ কাব্য]
২. বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে, [মেঘনাদবধ কাব্য]
এখানে ত্রিমাত্রক ‘অনঙ্গ’, ‘অকালে’ শব্দের পরে যতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। মধুসূদনের আত্মবিলাপ [১২৬৮ আশ্বিন] কবিতায় রয়েছে তিন-দুই-তিন এ ধরনের মাত্রাবিন্যাস :
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁদিতে।
‘চার-চার কিংবা তিন-তিন-দুই- এই হচ্ছে মিশ্রবৃত্তরীতি [অক্ষরবৃত্তরীতি] সম্মত মাত্রা সমাবেশের সাধারণ বিধি।’ অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে এ বিধির ব্যতিক্রমও গ্রহণযোগ্য হয়। অক্ষর সংখ্যার সমতাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মূল ভিত্তি নয়। ধ্বনি পরিমাণগত বিষয়টিও প্রধান বিবেচ্য বিষয় :
হে ধরণী, কেন প্রতিদিন
তৃপ্তিহীন
একই লিপি পড়ো ফিরে ফিরে?
[পূরবী, লিপি, রবীন্দ্রনাথ]
“একই’ শব্দটি দেখতে তিন হলেও শুনতে দুই’। রবীন্দ্রনাথ শ্রুতির অনুসরণ করে একে দুই মাত্রার মর্যাদা দিয়েছেন। কেননা, তিনি জানতেন ছন্দ-শাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র নয়, ওটি হচ্ছে আসলে শ্রৌত-শাস্ত্র। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথই এই মিশ্রবৃত্ত রীতির ছন্দকে দৃশ্যমান অক্ষরসংখ্যার সংকীর্ণ খাঁচা থেকে শ্রুয়মান ধ্বনির আকাশে মুক্তি দিয়েছেন। [ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ-২৯]
বলা যায়, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম অক্ষরবৃত্ত ছন্দ-রীতির স্বরূপ উপলদ্ধি করেছিলেন- যদিও তাঁর শৈশব-রচনায় কিছুটা দুর্বলতার পরিচয় ছিল।
উন্মেষ পর্বে [১৮৭৫-১৮৮২] রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দোগত কোন উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টিপ্রদীপের নিচে ধরা পড়ে না। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুদ্রিত কবিতা ‘অভিলাষ’। ১৮৭৪ সালে এ কবিতাটি ‘তত্ত্ববোধিনী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর ছন্দ সম্পর্কে প্রবোধচন্দ্র সেন-এর মন্তব্য : ‘অভিলাষ রচনার সময়েও বালক রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ছন্দোবোধ যে নেহাত কাঁচা ছিল না, তা স্পষ্টই বোঝা যায়’। [শত বার্ষিক জয়ন্তী উৎসর্গ [১৯৬১]: ভোরের পাখি]
‘কবিতাটি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮৩৮-১৯০৩] আদর্শে মিশ্রকলাবৃত্তের অমিল পয়ার চতুষ্পঙ্ক্তিক শ্লোকে রচিত’। এ কবিতায় ঊনচল্লিশটি শ্লোক রয়েছে। প্রথম শ্লোকটি উদ্ধৃত করছি:
জনমনোমুগ্ধকর ক্ষ্ম উচ্চ অভিলাষ
তোমার বন্ধুর পথ ক্ষ্ম অনন্ত অপার।
অতিক্রম করা যায় ক্ষ্মযত পান্থশালা
তত যেন অগ্রসর ক্ষ্ম হতে ইচ্ছা হয়।
[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৭৪]
মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথ অমিল অক্ষরবৃত্ত পয়ারের অবয়ব নির্মাণ করেছিলেন। ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ পর্বে [১৮৮২-১৮৯০] তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নানা রকম শাখা-প্রশাখার কথা স্মরণ রেখে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য : ‘সন্ধ্যাসঙ্গীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে। সে সময়কার অন্য সমস্ত কবিতা থেকে আপন ছন্দের সাজ পরে এসেছিল। সে সাজ বাজারে চলিত ছিল না’। [সন্ধ্যাসঙ্গীত, সূচনা, রচনাবলী, প্রথম খ-]
‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’-এর [১৮৮২] প্রথম কবিতার শিরোনামই ‘সন্ধ্যা’। একটু অংশ উদ্ধৃত করছি:
অয়ি সন্ধ্যে
অনন্ত আকাশতলে বসি একাকিনী
কেশ এলাইয়া
মৃদু মৃদু ওকি কথা কহিস আপন মনে
গান গেয়ে গেয়ে
নিখিলের মুখপানে চেয়ে।
কবিতাটি শুরু হয়েছে অমিলের মধ্য দিয়ে, প্রথমেই অতিপর্ব ‘অয়ি সন্ধ্যে’ লক্ষণীয়। পঞ্চম পঙ্ক্তি থেকে শেষ পঙ্ক্তি পর্যন্ত অন্ত্য-মিলের ব্যবহার বজায় রয়েছে। প্রথমাংশের এই কয়েকটি পঙ্ক্তি বাদ দিলে কবিতাটি সমিল অক্ষরবৃত্ত রূপেই গণ্য হবে। কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের মতে- ‘মুক্তকের প্রবহমানতা এখানে নেই- কিন্তু তার প্রাথমিক পদক্ষেপ’।
তৃতীয় কবিতায় ‘তারকার আত্মহত্যা’য় সমিল মুক্তকের আভাস ফুটে উঠেছে। ছয়, আট ও দশ মাত্রার পদ নিয়ে খেলায় মেতে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলাতেই। ‘কড়ি ও কোমল’ [১৮৮৬] কাব্যগ্রন্থ থেকেই তাঁর হাত আরও অধিক মাত্রায় ছন্দসিদ্ধ হয়ে ওঠে। অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদীর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি : ১০+১০ মাত্রাÑ
সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায় ক্ষ্ম শিথিল কবরী পড়ে খুলে-
যেতে যেতে কনক-আঁচল ক্ষ্ম বেধে যায় বকুলকাননে
চরণের পরশরাঙিয়া ক্ষ্ম রেখে যায় যমুনার কূলে-
নীরবে বিদায়-চাওয়া চোখে, ক্ষ্ম গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে
আঁধারের ম্লানবধূ যায় ক্ষ্ম বিষাদের বাসরশয়নে।
[কড়ি ও কোমল, সন্ধ্যার বিদায়]
অক্ষরবৃত্ত দ্বিপদী নয়, ত্রিপদীর একটি দৃষ্টান্ত : ৮+৬+১০ মাত্রা-
মৃত্যু যেন মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যায়,
পাঠায় সে বিরহের রবে চর
সকলেই চলে যাবে, পড়ে রবে হায়
ধরণীর শূন্য খেলাঘর।
[কড়ি ও কোমল, বিরহীর পত্র]
‘সন্ধ্যাসংগীত’ পর্বে ১৬৩টি কবিতাই অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নির্মিত। ‘মানসী পর্বেই’ [১৮৯০-১৯০০] ‘ছন্দের নানা খেয়াল দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। কবির সঙ্গে যেন একজন শিল্পী এসে যোগ’ হয়েছে। [মানসী, সূচনা, রচনাবলী]
“মানসী’র পূর্ব পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের প্রধান বাহন ছিল মিশ্রকলাবৃত্ত [অক্ষরবৃত্ত] রীতির ছন্দ। কলাবৃত্তের [মাত্রাবৃত্ত] আভাস মাঝে মাঝে পাওয়া গেলেও মিশ্রকলাবৃত্তের [অক্ষরবৃত্তের] সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট ছিল না’। ‘মানসীর যুগে রুদ্ধদল-কে দুই মাত্রার গৌরব দেবার ফলে কলাবৃত্ত [মাত্রাবৃত্ত] এবং মিশ্র কলাবৃত্তের [অক্ষরবৃত্তের] পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল’। [রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ, রামবহাল তেওয়ারী, ৩৫ পৃ.]
‘সন্ধ্যাসংগীত’ পর্বে মুক্তক অক্ষরবৃত্তের যে, আভাস আমরা পেয়েছি তা ‘মানসী’ পর্বের ‘নিষ্ফল কামনায়’ [১৮৮৭] আরও পরিণত রূপ লাভ করে :
শতঋতু আবর্তনে
বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
শতদল উঠিতেছে ফুটি;
সুতীক্ষè বাসনা ছুরি দিয়ে
তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে।
[মানসী: নিষ্ফল কামনা]
এ কবিতাটি অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত। এ কবিতা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য : ‘মানসী’ কাব্যগ্রন্থের নিষ্ফল কামনা [১৮৮৭] কবিতাটি ঐ কাব্যগ্রন্থটির অনেকগুলি নতুনত্বের মধ্যে একটি নতুনত্ব যুক্ত করে’। [ছন্দ, পৃ. ৬৮]
এ পর্বে রয়েছে সমিল প্রবহমান পয়ারেরও কিছু কবিতা। ‘মানসী’র ‘মেঘদূত; ‘অহল্যার প্রতি’, ‘শেষ উপহার’ ও ‘মৌনভাষা’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ‘অহল্যার প্রতি’ ও ‘শেষ উপহার’ কবিতা থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি :
ক) যে শিশির পড়েছিল তোমার পাষাণে
রাত্রিবেলা, এখন সে কাঁপিছে উল্লাসে
আজানুচুম্বিত মুক্ত কৃষ্ণ কেশপাশে।
[মানসী, অহল্যার প্রতি, ১৮৯০]
খ) আমি রাত্রি, তুমি ফুল যতক্ষণ ছিলে কুঁড়ি
জাগিয়া চাহিয়া ছিনু আঁধার আকাশ জুড়ি
সমস্ত নক্ষত্র নিয়ে, তোমারে লুকায়ে বুকে।
[মানসী, শেষ উপহার, ১৮৯০]
“রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় [১৮২৭-১৮৮৭]-প্রবর্তিত আঠারো মাত্রার মহাপয়ারকে প্রবহমান করার পরীক্ষা চালিয়েছিলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের হাতে মহাপয়ার যথার্থই প্রবহমান হয়ে উঠল। সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের প্রথম প্রয়োগ হয়েছে ‘সোনারতরী’ কাব্যের [১৮৯৪], ‘সমুদ্রের প্রতি’ [১৮৯২] কবিতায়।” [রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দী ছন্দ, রামবহাল তেওয়ারী পৃ.৩৩] ‘চিত্রা’ [১৮৯৬] কাব্যের ‘এবার ফিরাও মোরে’ কবিতাও সমিল প্রবহমান মহাপয়ারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ :
সুচির সঞ্চিত আশা সম্মুখে করিয়া উদঘাটন
জীবনের অক্ষমতা কাঁদিয়া করিব নিবেদন,
মাগিব অনন্ত ক্ষমা। হয়তো ঘুচিবে দুঃখনিশা।
তপ্ত হবে এক প্রেমে জীবনের সর্বপ্রেম তৃষা।
[চিত্রা, এবার ফিরাও মোরে]
‘মানসী’ পর্বে [১৮৯০-১৯০০] অক্ষরবৃত্ত কবিতার সংখ্যা ৩০১। উন্মেষ পর্ব থেকে মানসী-পর্ব পর্যন্ত অক্ষরবৃত্তে পাঁচ মাত্রা পর্বের চৌপদী এবং সাত মাত্রা পর্বের চৌপদী পঙ্ক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়নি- পাওয়া যায়নি অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও।
‘ক্ষণিকা’ পর্বে [১৯০০-১৯১৬] অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ কম। ‘ক্ষণিকা’ [১৯০০], ‘খেয়া’, [১৯০৬], ‘গীতিমাল্য’ [১৯১৪] কাব্যে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কোনো প্রয়োগ নেই। এ পর্বে ৭৩৩টি কবিতার মধ্যে ৪৪১টি কবিতাই স্বরবৃত্তে রচিত। নৈবেদ্য [১৯০১] কাব্যে রয়েছে ১০০টি কবিতা। এর ৭৮টি কবিতাই সনেট। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে নির্মিত, অর্থাৎ সমিল প্রবহমান পয়ারবন্ধে বিরচিত। সমিল প্রবহমান মহাপয়ার সনেটও তিনি নির্মাণ করেছেন :
তোমার সহস্র শৃঙ্গ বাহু তুমি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী, শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি।
[উৎসর্গ-২৭]
‘রবীন্দ্রনাথ বাংলা সনেটকে পাশ্চাত্য সনেটের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বাভাবিক গতি দান করেছেন। অনুকরণের মোহ থেকে এই মুক্তিÑ রবীন্দ্রনাথের একটি স্মরণীয় কীর্তি বলা যায়। এই সনেটগুলি রাবীন্দ্রিক সনেট নামে অভিহিত হতে পারে’। [রবীন্দ্রনাথ ও হিন্দীছন্দ, রামবহাল তেওয়ারী, পৃ: ৩৯]
অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত পয়ারেও তিনি কবিতা নির্মাণ করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে পয়ারের রূপবৈচিত্র্য নিয়ে একটু কথার বিস্তার করা যেতে পারে। ‘পয়ার একটি ছন্দোবন্ধের [ছন্দ-আকৃতির] নাম, ছন্দোরীতির [ছন্দ-প্রকৃতির] নাম নয়।
যে ছন্দপঙ্ক্তি অর্ধযতির দ্বারা যথাক্রমে আট ও ছয় মাত্রার দুই ভাগে অর্থাৎ দুই পদে বিভক্ত, তারই নাম পয়ার। সেই জন্যই ছন্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথ বলেছেন :
আট-ছয় আট-ছয়
পয়ারের ছাঁদ কয়।
[ছন্দ সরস্বতী, ভারতী, ১৩২৫ বৈশাখ প্রথম প্রকাশ]
পয়ারের সংজ্ঞাসূত্র থেকেই বোঝা যায়, ‘পয়ার’ আসলে দ্বিপদী বন্ধের একটি বিশেষ রূপের রূঢ়ার্থক নাম। অর্থাৎ যে কোনো রকম দ্বিপদী বন্ধকেই পয়ার বলা যায় না। শুধু আট-ছয় মাত্রার দ্বিপদী বন্ধকেই পয়ার নামে আখ্যাত করা হয়। পরবর্তীকালে আট-দশ মাত্রার দ্বিপদী বন্ধও পয়ার নামে পরিচিত হয়েছে। এই বড় পয়ারকে বলা হয় দীর্ঘ পয়ার বা মহাপয়ার। [নতুন ছন্দ পরিক্রমা, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ. ১৭০-১৭১]
‘পয়ার’ ও ‘মহাপয়ার’- এর রয়েছে তিনটি রূপ :
ক) পয়ার-
১। স্বরবৃত্ত [দলবৃত্ত] পয়ার [৮+৬]
২। মাত্রাবৃত্ত [কলাবৃত্ত] পয়ার [৮+৬]
৩। অক্ষরবৃত্ত [মিশ্রবৃত্ত] পয়ার [৮+৬]
খ) মহাপয়ার-
১। স্বরবৃত্ত [দলবৃত্ত] মহাপয়ার [৮+১০]
২। মাত্রাবৃত্ত [কলাবৃত্ত] মহাপয়ার [৮+১০]
৩। অক্ষরবৃত্ত [মিশ্রবৃত্ত] মহাপয়ার [৮+১০]
স্বরবৃত্ত পয়ার ও মহাপয়ার-এর দৃষ্টান্ত আমরা লক্ষ্য করি রবীন্দ্রনাথের ‘খেয়া’, কাব্যের ‘কোকিল’ কবিতায়, ‘ক্ষণিকা’র ‘কল্যাণী’তে আর মহাপয়ারের রূপ দেখি তাঁর প্রান্তিক-১৩, ‘একদা পরমমূল্য’ কবিতায়।
মাত্রাবৃত্ত পয়ার ও মহাপয়ারের রূপ লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথের ‘চিত্র-বিচিত্র’-এর ‘উৎসব’ ও নবজাতকের ‘শেষবেলা’ কবিতায়। অক্ষরবৃত্ত পয়ার ও মহাপয়ারের নানারকম বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ রবীন্দ্রকাব্যে কম নয়। রবীন্দ্রনাথ ছন্দের সব শাখা-প্রশাখাতেই কম-বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। ‘পুরো পঙ্ক্তির গতিভঙ্গিভেদে পয়ার ও মহাপয়ার উভয়েরই তিন রূপ- অপ্রবহমান, প্রবহমান ও মুক্তক’। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের [১৮২৭-১৮৮৭] ‘পদ্মিনী উপাখ্যান’ কাব্যে [১৮৫৮] সমিল অপ্রবহমান অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারের প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করি:
১. দুর্গের দ্বিতীয় দ্বারে মহীপতি আসি দেন বার,
বসিল ঘেরিয়া তাঁরে তারাকারে এগার কুমার।
[পদ্মিনী উপাখ্যান, অরিসিংহের যুদ্ধ বর্ণনা]
২. কোটি কোটি তারা মাঝে মৃগাঙ্গের প্রভাব যেমন,
অস্থির শত্রুর দল চারিদিকে করে পলায়ন।
[পদ্মিনী উপাখ্যান, অরিসিংহের যুদ্ধ বর্ণনা]
অমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারের প্রবর্তক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর [১৮৪০-১৯২৬]। ‘দ্বিজেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত এই অমিল প্রবহমান মহাপয়ারই দীর্ঘকাল পরে সমিল রূপ লাভ করে রবীন্দ্রনাথের রচনায়’। ‘রবীন্দ্রনাথ পঙ্ক্তিপ্রান্তিক মিলের মাধুর্যটুকু বর্জন না করেও এই মুক্তগতি পয়ারকে এক নতুন রূপ দিলেন। এই নতুন পয়ারকে বলা যায় সমিল প্রবহমান পয়ার’। [নতুন ছন্দ পরিক্রমা, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ: ১৭৭] প্রবহমান পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘পঙ্ক্তিলঙ্ঘক’ পয়ার। সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত পয়ারের নিদর্শন আমরা পাই ‘মানসী’র’ ‘মেঘদূত’ [১৮৯০], ‘অহল্যার প্রতি’ [১৮৯০], ‘সোনারতরী’র ‘যেতে নাহি দিব’, ‘বসুন্ধরা’ প্রভৃতি কবিতায়। ‘মেঘদূত’ থেকে একটু অংশ উদ্ধৃত করছি :
কবিবর, কবে কোন্ বিস্মৃত বরষে
কোন পুণ্য আষাঢ়ের প্রথম দিবসে
লিখেছিল মেঘদূত।
[মেঘদূত, সমিল প্রবহমান পয়ার]
সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ারের প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি ‘সোনারতরী’র ‘সমুদ্রের প্রতি’ [১৮৯৩], ‘চিত্রা’র ‘এবার ফিরাও মোরে’ [১৮৯৪] প্রভৃতি কবিতায়। ‘সমুদ্রের প্রতি’ কবিতা থেকে কয়েকটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করছি:
তাই ঘুমন্ত পৃথ্বীরে
অসংখ্য চুম্বন কর আলিঙ্গনে সর্ব অঙ্গ ঘিরে
তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযতেœ বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার
সুকোমল সুকৌশলে।
[সমুদ্রের প্রতি, সমিল প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ার]
রবীন্দ্রনাথ সমিল অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ার বন্ধে সনেটও নির্মাণ করেছেন। [দ্রষ্টব্য ‘উৎসর্গ-২৭’ সনেটটি] ‘শুধু পয়ার, মহাপয়ার বা ভাবের প্রবহমানতাকেই নয়, তিনি গিরিশ-রাজকৃষ্ণ প্রবর্তিত মুক্তক বন্ধকে যথার্থভাবে’ কাজে লাগিয়েছিলেন তাঁর কবিতায়। মুক্তক পয়ারকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘বেড়াভাঙা পয়ার’। ‘যে প্রবহমান পয়ার বা মহাপয়ার বন্ধে চোদ্দ বা আঠার মাত্রাকে পঙ্ক্তি দৈর্ঘ্যরে শেষ সীমা বলে মেনে নিয়ে ভাবপ্রকাশের প্রয়োজন অনুসারে ছন্দপ্ক্তিকে ছোট-বড় নানা রূপে বিন্যস্ত করা হয় তাকে বলা যায় মুক্তক পয়ার বা মুক্তক মহাপয়ার। কেননা, তাতে যতিস্থাপনের নির্দিষ্ট নিয়ম এবং প্রতি পঙ্ক্তির দৈর্ঘসমতা মেনে চলতে হয় না। শুধু মাত্রা বিন্যাস ও পর্বরচনার নীতি নিয়ম মেনে চলাই যথেষ্ট’। [নতুন ছন্দ পরিক্রমা, প্রবোধচন্দ্র সেন, পৃ. ২৬৮] এক কথায় বলা যায়, ‘নির্দিষ্ট পঙ্ক্তিসীমার বাধাটুকু সরিয়ে ফেলে কবিভাবনাকে স্বাধীনভাবে স্তরে স্তরে সাজিয়ে গেলেই হয় মুক্তক পয়ার’। তবে মুক্তকেও রয়েছে চৌদ্দ বা আঠার মাত্রার ও স্বাধীন স্তবকসজ্জার বিষয়টি। যদি কোনো কবিতার পঙ্ক্তি আঠার মাত্রার সীমা ছাড়িয়ে যায়, হ্রস্ব-দীর্ঘ ও অতি দীর্ঘ পঙ্ক্তির সমবায়ে কবিতাটি নির্মিত হয় তবে তাকে ‘অতিমুক্তক’ বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘লাগামছেঁড়া’ ছন্দবন্ধ বলা যেতে পারে। এ ‘লাগামছেঁড়া’ ছন্দবন্ধের প্রচুর নিদর্শন রয়েছে রবীন্দ্রনাথের ‘সন্ধ্যাসংগীত’ [১৮৮২], ‘প্রভাতসঙ্গীত’ [১৮৮৩] এবং ‘ছবি ও গান’ [১৮৮৪] কাব্যে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম মুক্তক অক্ষরবৃত্ত কবিতা ‘মানসী’র [১৮৯০], ‘নিষ্ফল কামনা’ [১৮৮৭], সুদীর্ঘ সাতাশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ মুক্তক অক্ষরবৃত্তের প্রথম প্রয়োগ করেন ‘বলাকা’র ‘ছবি’ কবিতায় [১৯১৪]:
তোমায় চিকন
চিকুরের ছায়াখানি বিশ্ব হতে যদি মিলাইত
তবে
একদিন কবে
চঞ্চল পবনে লীলায়িত
মর্মর-মুখর ছায়া মাধবী-বনের
হত স্বপনের।
[‘বলাকা’-৬ (ছবি), সমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত]
‘বলাকা’ পর্বে [১৯১৬-১৯৩২] তাঁর কবিতায় ‘নতুন পর্ব এসেছে, ভাব-ভাষা ও ছন্দ নতুন পথে গেছে। [ছন্দ, তৃতীয় সং, রবীন্দ্রনাথ, আমার ছন্দের গতি, পৃ: ১৭৭]
‘বলাকা’ [১৯১৬] কাব্যে রয়েছে ২৩টি সমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত। ‘এ পর্বের ‘লেখন’ [১৯২৭] ও ‘বনবাণী’ [১৯৩১] ছাড়া প্রতিটি কাব্যেই মুক্তকের নিদর্শন রয়েছে’। “মানসী’তে অমিল মুক্তক রচনার [নিষ্ফল কামনা, ১৮৮৭] দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ আবার চোদ্দ মাত্রার দীর্ঘতম পঙ্ক্তির অমিল মুক্তক রচনা করলেন ‘পরিশেষ’ কাব্যে” [অগোচর, ১৯৩২]:
সে নিরালা ভবনের
কুলুপ তোমার কাছে নেই
যার কাছে আছে তবে।
[পরিশেষ, অগোচর]
এখানে দুটো উদ্ধৃৃতি লক্ষণীয়, মুক্তক পয়ারেরও দুই রূপ- সমিল ও অমিল। সমিল ও অমিল মুক্তকে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত কবিতাও আমরা লক্ষ্য করি। ‘বলাকা’ [১৯১৬] পর্বে রয়েছে ২৩৬টি অক্ষরবৃত্ত কবিতা। ‘পুনশ্চ’-পর্বে [১৯৩২-১৯৪১], ‘প্রান্তিক’ [১৯৩৮], থেকে ‘শেষলেখা’ [১৯৪১] পর্যন্ত ১৮১টি অক্ষরবৃত্ত রীতির কবিতার মধ্যে ৮১টি কবিতাই অমিল। [‘প্রান্তিক’-১৪, ‘রোগশয্যায়’-২৯, ‘আরোগ্য’-১৪, ‘জন্মদিনে’-১৬ এবং ‘শেষলেখা’-৮, মোট ৮১টি কবিতা অমিল]। এবার রবীন্দ্রনাথের সমিল ও অমিল মুক্তক পয়ার ও মহাপয়ারের আরও কিছু দৃষ্টান্ত বিভিন্ন কাব্যপর্ব থেকে তুলে ধরছি :
ক. সমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত পয়ার :
অল্পকিছু আলো থাক,
অল্পকিছু ছায়া,
আর কিছু মায়া।
ছায়াপথে লুপ্ত আলোকের পিছু
হয়তো কুড়ায়ে পাবে কিছু-
কণা মাত্র লেশ
তোমার ঋণের অবশেষ।
[রোগশয্যায়-৪, অজস্র দিনের আলো-১৯৪০]
খ. অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত পয়ার :
সে না হলে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
উঠত না শঙ্খধ্বনি,
মিলত না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সামমন্ত্র ভাষাহীন হয়ে
রইত নীরব।
[পরিশেষ, প্রাণ-১৯৩২]
গ. সমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ার :
প্রিয়া তারে রাখিল না, রাজ্য তারে ছেড়ে দিল পথ
রুধিল না সমুদ্র পর্বত।
আজি তার রথ
চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বার পানে
[বলাকা, শাজাহান]
ঘ. অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্ত মহাপয়ার :
চঞ্চলের অন্তরালে অচঞ্চল যে শান্ত মহিমা
চিরন্তন,
চরম প্রসাদ তার
নামিল তোমার নম্রশিরে
মানস-সরোবরের অগাধ সলিলে
অন্তর্গত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।
[পরিশেষ, জরতী, ১৯৩২]
রবীন্দ্রনাথের এই মুক্তক বন্ধকে ‘রাবীন্দ্রিক বন্ধ’ নামে চিহ্নিত করা যায়। প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে, ‘যতি ও পঙ্ক্তিসীমার বন্ধনহীনতাই মুক্তক’। মধুসূদন তাঁর কাব্যে, নাটকে, মিলহীনতা, প্রবহমানতা ও যতির স্বাধীনতাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু মান্য করেছেন চৌদ্দমাত্রার পঙ্ক্তিবিন্যাসকে। আর গিরিশচন্দ্র [১৮৪৪-১৯১২] তাঁর ‘রাবণবধ’ [১৮৮১] নাটকে প্রথম প্রয়োগ করেন স্বাধীন পঙ্ক্তিবিন্যস্ত অমিত্রাক্ষরÑ যা ‘গৈরিশ ছন্দোবন্ধ’ নামে পরিচিত। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন পঙ্ক্তি বিন্যাস-কে অবলম্বন করেই মুক্তক বন্ধকে [অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে] ‘সন্ধ্যাসঙ্গীত’ পর্ব [১৮৮২-১৮৯০] থেকে শুরু করে ‘পুনশ্চ’-পর্ব [১৯৩২-১৯৪১] পর্যন্ত অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ কবিতাটিও অমিল মুক্তক অক্ষরবৃত্তে রচিত :
তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
[শেষলেখা, ২৫ তোমার সৃষ্টির পথ, ১৯৪১, ৩০ জুলাই]
রবীন্দ্রনাথ ছন্দের দুর্গম পথের যাত্রিক। ‘তিনিই সর্বাগ্রে বাংলা ভাষার মর্মগত স্বাতন্ত্র্যকে অক্ষুণœ রেখে বাংলা ছন্দের মূলনীতিগুলো আবিষ্কার করেছেন’Ñ ভেঙে দিয়েছেন কৃত্রিমতা ও অপূর্ণতার বেড়াজাল, প্রচলিত, বহুল ব্যবহৃত ছন্দকে ভেঙেচুরে, নানা মাত্রায়, নতুন আঙ্গিকে কবিতায় প্রয়োগ করেছেনÑ। তিনিই ‘রুদ্ধদলের সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ রূপের যথাযোগ্য’ মর্যাদা দিয়ে অক্ষরবৃত্তের মর্মসত্যকে উপলব্ধি করে ‘সহস্রবছরের আক্ষরিক সংস্কারকে’ [হরফ বা অক্ষর-সমতা অক্ষরবৃত্ত রীতির যথার্থ ভিত্তি নয়- এমন সংস্কার] ভেঙে ধ্বনিভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে।