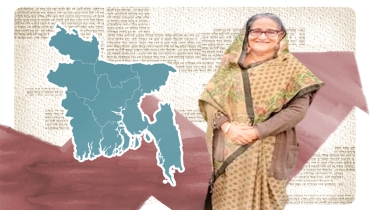বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছে। ধর্মের নামে সন্ত্রাসী কর্মকা- এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, অধিকাংশ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজমান। বাংলাদেশ ইতোপূর্বে অনেক কঠিন সময় অতিক্রম করেছে; কিন্তু গুলশানের হলি আর্টিজান রেস্তরাঁয় জঙ্গী আক্রমণে অতীতের সকল দুঃসময়কে ছাপিয়ে গেছে। সন্ত্রাসী জঙ্গীরা ১৭ বিদেশীসহ বিশজনকে বিধর্মী বলে হত্যা করায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র যেমন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অসাম্প্রদায়িক দেশের সুনাম হারিয়েছে, তেমনি শান্তির ধর্ম হিসেবে ইসলামকেও প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ‘ইসলাম শান্তির ধর্ম’ এই শাশ্বত বাক্যের বিপরীতে জঙ্গীদের অবস্থান। এজন্য পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মুসলমানরা সঙ্কটের মধ্যে পড়েছে। কিন্তু জঙ্গীরা যে ইসলামের কথা বলছে তা পবিত্র কোরআন বা মহানবীর ইসলাম নয়; এটি ইয়াজিদের ইসলাম। মুয়াবিয়া সিফ্ফিনের যুদ্ধে তদীয় পুত্র ইয়াজিদ কারবালার নৃশংসতা ঘটিয়ে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের বীজ রোপণ করেন। কারবালার নৃশংসতা ইসলামের মূল মর্মবাণীর বিপরীত বিধায় ইতিহাস ইয়াজিদকে ক্ষমা করেনি। আজ বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে আইএস নামধারী সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত যেসব তা-বলীলা চালাচ্ছে তার পেছনে বরং ইহুদীদের মদদ থাকতে পারে। আইএস বা তাদের বন্ধুপ্রতিম সন্ত্রাসী বিভিন্ন নামের যেসব সংগঠন তাদের কর্মকা-ে এটি স্পষ্ট যে, তারা প্রকৃতপক্ষে ইসলাম ধর্মের অনুসারী নয়। কারণ, কোরআন-হাদিসের কোথাও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা করার কথা নেই। এমনকি যদি কেউ ধর্মে বিশ্বাস নাও করে তাকেও হত্যার লাইসেন্স প্রদান করেনি পবিত্র কোরআন বা রাষ্ট্র। ইসলামের নামে সন্ত্রাস বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে; কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে যে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি তা অনেকটাই সাম্প্রতিক। ফলে এই সন্ত্রাসী কর্মকা-ের বিষয়টি শুধু বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক বিষয়। এই বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবেই মোকাবেলা করা প্রয়োজন। আর বাংলাদেশের যে চিরায়ত ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সংস্কৃতি তাতে উগ্রবাদী এই জঙ্গীদের টিকে থাকার কথা নয়। বিবেকবান মানুষের জেগে ওঠার ওপর সন্ত্রাসীদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। রাষ্ট্রের পাশাপাশি জনগণের জোরালো আওয়াজ সন্ত্রাসীদের নির্মূল করতে সহায়ক হবে।
বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ও বিস্তৃতিতে শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন পড়েনি। আফ্রিকা, স্পেন ও অন্যান্য অঞ্চলে মুসলমানদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় যেভাবে শক্তি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়, বাংলায় ইসলাম প্রচার ও প্রসারে সে পথ অবলম্বন করতে হয়নি। এর কারণ ইসলাম ধর্মের সাম্যের চেতনা ও হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা। এ অঞ্চলে হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণরা সমাজে এমন বিভাজন তৈরি করেন যে, বৈশ্য ও শূদ্রদেরকে তারা অস্পৃশ্য ও নিম্নবর্ণীয় মনে করত এবং নিম্নবর্গীয়রা শুধু উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণদের আদেশ পালন করবে এবং তাদের নৈবেদ্যে পূজার ফুল অর্পণ করবে এটাই ছিল নিয়ম। বখতিয়ার খলজি ও তার পরবর্তীতে আগত সুফী দরবেশগণ বাংলায় ঠিক এর বিপরীত ব্যবস্থা চালু করেন। এখানে উল্লেখ্য, বখতিয়ার খলজি ত্রয়োদশ শতকের ঊষালগ্নে বাংলা দখলের পর মুসলমান বিজয়ের স্মারক হিসেবে মসজিদ, মাদ্রাসা ও খানকা তৈরি করেন। মসজিদে নামাজ আদায়, মাদ্রাসায় নতুন ধর্ম শিক্ষা ও খানকায় সুফি দরবেশদের আবাস এবং ইসলাম প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হয়। পরবর্তীতে দেখা যায় যে, ৩টি প্রতিষ্ঠানই, বিশেষত খানকা নিম্নবর্গীয় হিন্দুদের আকৃষ্ট করে। খানকায় অবস্থানরত সুফিরা এটাকে মানুষের মিলনের স্থানে পরিণত করেন। তারা মানুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির পরিবর্তে ঐক্যের আহ্বান জানান এবং ধনী-গরিব, উঁচু-নিচু, সাদা-কালোর পার্থক্য না করে একই থালায় খাবার আয়োজন করেন। মসজিদে আমীর-ওমরাহ বা সাধারণ মানুষ একই কাতারে নামাজ আদায় করেন। এ সকল ব্যবস্থা নিম্নবর্গের হিন্দুদের আকৃষ্ট করে এবং তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। এই সাম্যের চেতনাই এ অঞ্চলে ইসলামের প্রসার ঘটায়। ইসলাম প্রতিষ্ঠায় এখানে জঙ্গী কর্মকা-ের আশ্রয় নিতে হয়নি।
পুরো সুলতানী ও মোগল আমলে সুফিদের আগমন অব্যাহত ছিল এবং খানকাভিত্তিক ইসলাম প্রচারের কাজ তারা করেছেন নির্বিঘেœ, শান্তির মাধ্যমে, মানুষকে বুঝিয়ে। সুলতানী আমলে শায়খ নূর কুতুব উল আলম, শায়খ মোজাফ্ফর শামস্ খলজী, শায়খ আনোয়ার, শায়খ জাহিদ প্রমুখ সুফি মানুষকে আধ্যাত্মিক বিষয়ে শিক্ষা দেন। পরবর্তীকালে খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তি, নিজামউদ্দীন আউলিয়াসহ বহু সুফি ভারতবর্ষে এসেছেন। তাদের অনুসারীরা বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে খানকা স্থাপন করে মানুষকে ভ্রাতৃত্বের ও সাম্যের পথে আনার চেষ্টা করেছেন। বাংলাদেশে এখনও অনেক পীর-দরবেশ রয়েছেন যারা বর্বরতা ও শক্তি প্রয়োগের বিরুদ্ধে। তাদের অনুসারীদের তারা শান্তির পথে থাকার জন্য সর্বদা নির্দেশ দেন।
ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখলের পর সমাজে বিভাজন তৈরির উদ্যোগ নেয়। সকল ঔপনিবেশিক শক্তিই ‘ভাঙ্গ এবং শাসন কর’ নীতির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে পার্থক্য তৈরি করেছে এবং প্রতিটি ঔপনিবেশিক শক্তিই নিজেদের সীমানায় এই গর্হিত কাজ থেকে বিরত থেকেছে। ভারতে ইংরেজ, লিবিয়ায় ইতালি, আলজেরিয়া-তিউনিসিয়া, মরক্কো ও সিরিয়া-লেবাননে ফ্রান্স এবং ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজরা এই বিভাজনের নীতি অনুসরণ করে। আরব-অনারব, শিয়া-সুন্নী, সুন্নী-আলাবী, হিন্দু-মুসলমান, সাদা-কালো বিভিন্নভাবে তারা মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। ভারতবর্ষে ক্ষমতা দখলের কিছু দিনের মধ্যেই তারা হিন্দু উচ্চবর্গীয়দের বিভিন্নভাবে সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকে। এতে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হয়। এরই প্রকাশ ঘটে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গে। বঙ্গভঙ্গকে অধিকাংশ মুসলমান সমর্থন করে এবং অধিকাংশ হিন্দু বিরোধিতা করে। ফলে সমাজে সাম্প্রদায়িক সঙ্কটের সৃষ্টি হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারত এবং পাকিস্তান নামে দুটো রাষ্ট্রের পত্তন হয়। ভারতে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং পাকিস্তানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। ব্রিটিশরা উপমহাদেশে স্থায়ীভাবে সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দেবার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে। তৎকালীন নেতৃবৃন্দ এটা অনুধাবন করা সত্ত্বেও পরিস্থিতি এমন এক জটিল জায়গায় পৌঁছে যে, তখন কারোরই কিছু করার ছিল না। এমনকি ভারত বিভাগের সময় সীমানা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রেও কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়, যাতে এ অঞ্চলে স্থায়ীভাবে অশান্তি বিরাজমান থাকে। আবার পাকিস্তান রাষ্ট্র তৈরি করা হয় ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, ভৌগোলিক অবস্থান আলাদা হওয়া সত্ত্বেও দুই অঞ্চলকে একই রাষ্ট্রের পতাকাতলে একই জাতীয় সঙ্গীতের আওতায় আনা হয়। ফলে সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ শুরু হয়।
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গণপরিষদে যে ভাষণ দেন তাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষ সমানাধিকার ভোগ করবে। কিন্তু তিনি তার এই বক্তব্যে অটল থাকতে পারেননি। বাংলা ভাষার দাবিতে বাঙালীদের আন্দোলনে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি ভাষা বিতর্কে সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে অবস্থান নেন। বাংলাকে হিন্দুদের ভাষা হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তার মৃত্যুর পরে তার অনুসারীরা একই নীতি অবলম্বন করেন। লিয়াকত আলী খান বা খাজা নাজিমুদ্দীন কেউই বাংলার পক্ষে ছিলেন না। বরং ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানে পূর্ব বাংলার প্রতি যেসব বৈষম্য নেমে আসে তা কোনভাবেই ইসলামের সাম্যের চেতনার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। রাষ্ট্র এক্ষেত্রে সরাসরি বিভাজনের নীতি শুরু করে। পাকিস্তান ইসলামী রাষ্ট্র এই অজুহাতে রবীন্দ্রনাথকে প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ করা হয়। কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা থেকে বাংলা শব্দ বাদ দিয়ে উর্দু বা ফার্সী শব্দ লাগিয়ে দেয়া হয়। মানবতার কবি নজরুলকে ইসলামের ধারক-বাহক হিসেবে প্রচার শুরু হয়। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ এই সাম্প্রদায়িক কর্মকা-ে সরকারকে সহযোগিতা দেয়। আইয়ুব খান রাষ্ট্রপতি থাকাকালে এক বুদ্ধিজীবীকে ডেকে বলেন, ‘আপনারা রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না?’ এভাবে সমাজের সকল স্তরে সাম্প্রদায়িকতার বীজ উপ্ত হতে থাকে। বাঙালী মুসলমানদের মধ্যেও বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। সমাজের উচ্চবিত্ত বা ভূস্বামীদের বেশিরভাগই পাকিস্তানের এব মানবতাবাদবিরোধী কর্মকা-কে সমর্থন করে। তবে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায় উদার ও প্রগতিবাদ আঁকড়ে ধরে। কিন্তু এরই মধ্যে উগ্র সাম্প্রদায়িকতার এক নতুন দর্শন সামনে নিয়ে আসেন মাওলানা আবুল আলা মওদুদী। তিনি জামায়াতে ইসলামী নামক এক উগ্র ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের পত্তন করেন। বলা যায়, জঙ্গীবাদের বিস্তার এই সময় থেকে ও তার অনুসারীদের মাধ্যমে শুরু হয়।
মওদুদী মূলত তুরস্কের জামালউদ্দীন আফগানীর অনুসারী। বিশ্ব ইসলামীবাদ ছিল আফগানীর দর্শন। যে কোন পন্থায় পুরো পৃথিবীতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কেমন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা ছিল না। আরবের গোত্র-বিভক্তি মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন মহানবী (সা)। তিনি অন্য ধর্মাবলম্বীদের জীবন ও সম্পদকে নিরাপত্তা দিয়েছেন, তাদের ধর্ম পালনের অবাধ অধিকার প্রদান করেছেন। মহানবী (সা) সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করেননি। মওদুদীবাদ শুধু সমাজে নয়, এ অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইসলামের নামে যেভাবে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে ইসলামের ভাবাদর্শ পরিপন্থী এবং মওদুদীবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ।
আবুল আলা মওদুদী তার দর্শনে মিসরের ‘ইখওয়ান উল মুসলিমীন’ ও তুরস্কের ‘মুসলিম ব্রাদারহুড’ এবং মক্কার ইবনে সৌদের ‘ইখওয়ানে’র নীতি-আদর্শকে অনুসরণ করেন। উভয় ইখওয়ানেরই মূল উদ্দেশ্য ছিল শক্তি প্রয়োগ করে হলেও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। সেক্ষেত্রে যুব সমাজ বিশেষ করে মাদ্রাসার ছাত্রদের তারা টার্গেট করেন। তারা এমনভাবে তাদের অনুসারীদের শিক্ষাদান করেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিলে তার জন্য শহীদের মর্যাদা পাওয়া যাবে। আর এই শহীদ হবার জন্য বেহেস্ত নিশ্চিত। এভাবে যুবকদের কট্টর পন্থার দিকে নিয়ে যাবার প্রয়াস পান মওদুদী ও তার দর্শনের অনুসারীরা। মিসরের ইখওয়ানের সদস্যদের যেমন চূড়ান্ত সমর্থকে পরিণত হবার পর্যায়ে পবিত্র কোরআন হাতে শপথ গ্রহণ করানো হয়, ঠিক জামায়াতে ইসলামীও তাদের অনুসারীদের একইভাবে শপথ করায়। এজন্য বিভিন্ন সময়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে শিবিরের সংঘর্ষ হয়েছে, তখন পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার উদ্যোগ নিলে তারা পুলিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ে। ১৯৯২ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সোহরাওয়ার্দী ও মাদার বখ্শ হলের মধ্যবর্তী স্থানে পুলিশ-শিবির সংঘর্ষ হয়। তখন পুলিশই শিবিরের ভয়ে পিছু হটে। এটা লক্ষণীয় যে, পুলিশের জীবনের মায়া আছে; কিন্তু শিবিরের ক্যাডারদের জীবনের কোন মায়া নেই। কারণ তারা ‘মরলে শহীদ’ হবে- এই চেতনায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে চ্যালেঞ্জ করে। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মওদুদীর কোন সন্তান মাদ্রাসায় পড়েননি। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং কেউ জামায়াতে ইসলামীর অনুসারী হননি।
১৯৮০’র দশকের গোড়ার দিকে দেখা যায় যে, ইসলামী ছাত্রশিবিরের অনেক সাথী রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান যুদ্ধে যোগ দেয় এবং কেউ কেউ ৮০’র দশকের মাঝামাঝি ফিরে আসে। তাদের বিভিন্ন মসজিদে অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হতো। এই সকল সাথীই পরবর্তীতে তাদের অনুসারীদের অস্ত্রের প্রশিক্ষণ দেয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন পাহাড়ের ওপরে এ ধরনের প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছে এমন কারও কারও সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ছাত্রশিবিরের একটা পর্যায়ে পৌঁছে সবাই ভাতা পায়। তারা কাজ করে অর্থের বিনিময়ে। উপর পর্যায়ের সবাই বেতনভোগী। এই বেতন বা অর্থের উৎস মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ এবং বাংলাদেশের বিত্তবান জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। পূর্বতন শিবিরের অনেক নেতা, যারা বিভিন্ন কারণে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে এখন যুক্ত নেই তাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, জামায়াত বা ছাত্রশিবিরের একটা বিশেষ অংশ রয়েছে যাদের সামরিক প্রশিক্ষণ রয়েছে এবং তারা আত্মঘাতী। আফগান ফেরত প্রশিক্ষিত শিবিরের নেতা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বাহিনীতে তাদের অবসরপ্রাপ্ত অনুসারীদের মাধ্যমে এই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য ঐ সময়ে জামায়াতের সেøাগান ছিল ‘মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী’। পরবর্তীকালে আফগানিস্তানে যখন তালেবানরা ক্ষমতা দখল করে তখন জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে তাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তৈরি হয় এবং বাংলাদেশে ছাত্রশিবির তখন স্লোগান দেয় ‘আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান’। এ সময় জামায়াত-শিবিরের মূল মুখপত্র ছিল দৈনিক ইনকিলাব। পরবর্তীকালে সংগ্রাম ও নয়াদিগন্ত তাদের আদর্শ প্রচার করে। এমনকি আমার দেশ পত্রিকাটিও পরোক্ষভাবে জামায়াত-শিবিরের পক্ষে অবস্থান নেয়। জামায়াতে ইসলামীর অর্থ অঢেল। তাদের ব্যাংক, বীমা, পরিবহন, প্রিন্টিং প্রেস, বিভিন্ন মিডিয়াসহ অন্য অনেক ক্ষেত্রে বিপুল অর্থের বিনিয়োগ রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে তাদের দলীয় আদর্শের অনুসারীরাই চাকরি পায়। অর্থাৎ ছাত্রজীবন শেষ করে শিবিরের নেতাকর্মীকে বেকার জীবন কাটাতে হয় না। তারা সঙ্গে সঙ্গে কাজ পায়। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, শিবিরের উঁচুপদে পদার্পণ করলে তারা ভাতা পায়, আবার লেখাপড়া শেষ করার পর সঙ্গে সঙ্গেই চাকরি পায়। সেজন্য তাদের কোন অর্থাভাব নেই। বরং চাকরি পাবার পর বেতনের একটা নির্দিষ্ট অংশ দলীয় তহবিলে জমা দিতে হয়। এভাবে তাদের দলীয় তহবিলে সর্বদা বিপুল অংকের অর্থ থাকে। সেজন্য তাদের প্রচার-প্রচারণায় অন্য যে কোন রাজনৈতিক দলের চেয়ে তারা বেশি খরচ করে।
আফগান যুদ্ধের পর তালেবানদের সঙ্গে যেমন জামায়াত-শিবিরের যোগাযোগ তৈরি হয়, ঠিক আইএসের সঙ্গেও তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে বলে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থার ধারণা। তবে তালেবানদের প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করে যেভাবে তারা মিছিল করেছে, এখন আইএসের বিষয়ে তারা প্রকাশ্য নয়। কারণ তাদের দলীয় হাইকমান্ডের অনেকেই যুদ্ধাপরাধের মামলায় অভিযুক্ত হয়েছেন, কারও কারও দ-ও ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। এজন্য তারা রাজনৈতিকভাবে চাপের মুখে রয়েছে। তবে জামায়াত-শিবিরের তৎপরতা থেমে নেই। রাষ্ট্র বা সরকারের প্রতিটি অঙ্গে তাদের অনুসারী রয়েছে। প্রত্যেকের জায়গায় তারা দলীয় কাজ করে। এছাড়া ৫ জানুয়ারি ২০১৪-এর নির্বাচন পূর্ব সময়ে তাদের বর্বরতা এবং ২০১৫ সালের ৫ জানুয়ারির পর টানা ৯২ দিন তাদের যে তা-ব চলে, তখন তাদের শক্তির বিষয়ে একটা ধারণা পাওয়া যায়। ঐ সময় তারা টিভি ক্যামেরা ডেকে নিয়ে বোমাবাজির ছবি তোলে এবং তা অনেক চ্যানেল প্রচারও করে। ঐ সময় তাদের নামে দায়েরকৃত মামলাগুলোর বিচারের প্রক্রিয়া এখনও সম্পন্ন হয়নি।
রাজনৈতিক চাপে থাকার কারণে সাম্প্রতিককালে তাদের কোন সমাবেশ পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু এক বছর আগেও ঢাকায় সরাসরি তারা পুলিশের ওপর হামলা করেছে। ২০১৪ পূর্ববর্তী সময়ে বাংলাদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে কোন দল সরকারী বাহিনীকে টার্গেট করে আক্রমণ করেনি। কিন্তু ২০১৪ এবং অতঃপর দেখা যায় যে, তারা সরকারী বাহিনীর ওপর হামলা চালাচ্ছে। বর্তমানে আইএসের নামে যে মানবতাবিরোধী কর্মকা- চলছে, ইসলামী ছাত্রশিবির এদেশে তা আগেই শুরু করেছে। ছাত্র-রাজনীতি সম্পর্কে যারা খোঁজ-খবর রাখেন তারা জানেন যে, ছাত্রশিবিরেরও আত্মঘাতী হামলাকারী রয়েছে। যারা জীবন দেবার জন্য প্রস্তুত তাদের আলাদা তালিকাও রয়েছে। বিপরীতপক্ষের আক্রমণে মৃত্যু হলে বেহেস্তের সার্টিফিকেট প্রদান করার বাইরেও জামায়াত তাদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। তাই ধর্মীয় উন্মাদনার পাশাপাশি অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা তাদের রয়েছে। এজন্য শিবিরের একটা বিশেষ অংশ জীবন দেবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। প্রায় দশ বছর পূর্ব থেকে ছাত্রশিবির তার রাজনৈতিক কৌশল পাল্টেছে বা বলা যায় নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে। তা হলো তাদের কর্মী-সমর্থকদের তারা ইংরেজী শেখাবার উদ্যোগ নেয়। প্রতি শুক্রবার নির্দিষ্ট কোন জায়গায় তাদের কমিউনিকেটিভ ইংরেজী শেখানো হয়। কর্মীরা অন্য দেশের মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারে সেজন্যই এই ব্যবস্থা। তাদের শারীরিক ফিটনেস ঠিক রাখার প্রশিক্ষণ হয় প্রকাশ্যে। ক্রিকেট খেলা, ফুটবল খেলা বা ব্যায়াম করার নামে তাদের শরীর চর্চা চলে। এই গ্রুপটিও বিভিন্ন সময় সশস্ত্র তা-বে অংশ নেয়। তাদের আক্রমণের ধরন ভিন্ন। বেশিরভাগ সময়ই তারা ঘুমন্ত মানুষের ওপর অতর্কিত হামলা চালায় এবং সুস্থির ও ঠা-া মাথায় মানুষকে হত্যা করে।
আইএসের বিভিন্ন কর্মকা- পর্যালোচনা করলে এটা প্রতীয়মান হয় যে, ছাত্রশিবিরের কর্মকা-ের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য রয়েছে। তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কাউকে মুসলমান মনে করে না। সেজন্য অন্য মুসলমানকে হত্যার সময় তারা বিধর্মীকে হত্যা করছে বলে মনে করে। আইএসের নামে ১ জুলাই গুলশানের রেস্তরাঁয় হামলা করে বলা হয়েছে যে, বিধর্মীদের হত্যা করা হলো। কিন্তু মসজিদে হামলা, শোলাকিয়ায় ঈদের জামাতে হামলা, বিভিন্ন মন্দিরের পুরোহিতকে হত্যায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, তারা বিধর্মী নয়, মানুষ হত্যায় মেতে উঠেছে। তদুপরি ইসলাম ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের হত্যা যে অনুমোদন করে না তা পূর্বেই বলা হয়েছে।
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে অনেকবার বলা হয়েছে যে, এদেশে আইএস নেই। এটা হয়ত সঠিক যে, সরকারের গোয়েন্দাদের হাতে বাংলাদেশে আইএস নামক কোন সংগঠন আছে- এরকম তথ্য নেই। কিন্তু আইএস তাদের অনুসারী ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের মাধ্যমে তা-বলীলা চালাচ্ছে বলে অনেকেরই ধারণা। অতএব আইএস নেই; কিন্তু আইএসের ভাই আছে। জেএমবি বা হিযবুত তাহ্রীর যেমন জামায়াত-শিবিরের ভাই, ঠিক তেমনি জামায়াত-শিবির আইএসের ভাই। বিষয়টাকে দেখা প্রয়োজন এই দৃষ্টিকোণ থেকে। কারণ হঠাৎ করে একজন যুবক হারিয়ে গিয়ে আইএস হতে পারে না। এর পেছনে কোন সংগঠন ক্রিয়াশীল। সেই সংগঠন জামায়াত-শিবির ছাড়া অন্য কারও নেই। পাকিস্তানের লস্কর-ই তৈয়্যেবা, জয়সই মোহাম্মদ, আফগানিস্তানের তালেবান ও সাম্প্রতিককালের আইএস সবই ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন। বেশ কয়েক বছর ধরে মাদ্রাসার ছাত্র ছাড়াও পোশাক-পরিচ্ছদে আধুনিক- এমন মেধাবী ছাত্রদের শিবির দলে টানছে এবং তাদের প্রশিক্ষিত করে তুলছে তথাকথিত জেহাদের জন্য। লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই কোন যুদ্ধাপরাধীর দ- কার্যকর সমাগত হয়, তখনই কোন না কোন তা-ব চলে। অদূর ভবিষ্যতে জামায়াতের সবচেয়ে বড় অর্থদাতা মীর কাশেম আলীর আপীলের রিভিউ রয়েছে। এটাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য বর্তমান অবস্থা তৈরি করা হতে পারে। পাঠকদের মনে থাকতে পারে, কোন এক যুদ্ধাপরাধীর মামলার বিচার চলাকালে একটা তুর্কি পর্যবেক্ষকদল হঠাৎ করে ট্রাইব্যুনালে ঢুকে যায় এবং বিচারকদের সঙ্গে আদালতের রীতি পরিপন্থী আচরণ করে। তখন এ ধরনের সংবাদ প্রকাশ হয় যে, তাদের ভিসাও যথাযথ ছিল না। জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে তুরস্কের মৌলবাদীদের এই যে যোগাযোগ এতে স্পষ্ট হয় যে, আইএসের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া এখানে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়, ২০০০ সালের পর এ পর্যন্ত যত বড় বড় বোমা বা গ্রেনেড হামলা হয়েছে তা উদারপন্থী, মুক্তচিন্তার অধিকারী গণতন্ত্রমনা মানুষের ওপরই হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে বলতে হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনার অধিকারী মানুষই বরাবর আক্রান্ত হয়েছে। এমনকি বিএনপির কোন উদারপন্থী নেতাকর্মীর ওপর এসব পৈশাচিক তা-ব চলেনি। উদীচী, সিপিবি, একুশে আগস্ট, আহসানউল্লাহ্ মাস্টার, মঞ্জুরুল ইমাম, হুমায়ুন আজাদ, মমতাজউদ্দিন ও এসএএমএস কিবরিয়ার কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।
২০০৯-এর পর থেকে এ পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসহ সাধারণ মানুষের ওপর যেসব আক্রমণ হয়েছে এর কোনটির বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবির নিন্দা জানায়নি। ব্লগে যেসব লেখক লেখালেখি করেন তাদের হত্যাকা-গুলোও একই চক্রের। উদারপন্থী অনলাইন লেখকদের ব্লগার বলে সাধারণ মানুষের কাছে তাদের বিতর্কিত করার চেষ্টা করা হয়েছে বারবার। কিন্তু জামায়াত-শিবিরের ‘বাঁশের কেল্লা’র সদস্যরা যে ব্লগে লেখে তাদের ব্লগার বলা হয়নি। অথচ ব্লগার যেন একটা গালিতে পরিণত হয়েছে এবং ব্লগার হত্যার ধারাবাহিকতায় আজ গুলশান ও শোলাকিয়ার ট্র্যাজেডি। এর সবগুলো ঘটনাই একই সুতোয় গাঁথা। (চলবে)
লেখক : উপাচার্য, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা, বাংলাদেশ শনিবার ২৭ এপ্রিল ২০২৪, ১৩ বৈশাখ ১৪৩১