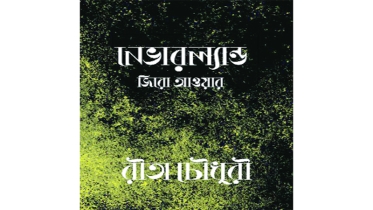টনি মরিসন মার্কিন ঔপন্যাসিক, সম্পাদক এবং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক। পেয়েছেন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার। অর্জনের খাতায় আরও যোগ করেছেন ন্যাশনাল হিউম্যানিটিজ পদক, প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব ফ্রিডম। টনি মরিসন এর জন্ম আমেরিকার ওহাইও অঙ্গরাজ্যের লরেইন-এ ১৯৩১ সালে। এরি লেইকের নিকটে উত্তরাঞ্চলের ছোট্ট এই শিল্প শহরটিতে তখন মূলত ইউরোপিয়ান, মেক্সিকান ও কৃষ্ণাঙ্গদের বসবাস ছিল। টনির বাবা জর্জ ওফোর্ড ও মা সারাহ উইলিস ওহাইওর দক্ষিণাঞ্চল থেকে বর্ণবাদ এড়াতে এবং অধিকতর সুবিধার আশায় উত্তরে চলে আসেন। ছোটবেলা থেকেই টনি অত্যন্ত মেধাবী। শৈশবে তাঁর নাম ছিল ক্লোয়ি এ্যান্তনি ওফোর্ড। ক্লাসের মধ্যে তিনিই শুধু প্রথম গ্রেডে পড়তে পারতেন। ১৯৪৯-এ ভর্তি হন ওয়াশিংটনের হাওয়ার্ড ইউনিভার্সিটিতে। ইংরেজী সাহিত্যে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন ১৯৫৩ সালে। অনেকেই তাঁর প্রথম-নাম ‘ক্লোয়ি’ ঠিকমতো উচ্চারণ করতে না পারায় মধ্যনামের সংক্ষেপ ‘টনি’কেই প্রথম-নাম হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৫৫‘তে স্নাতকোত্তর পাস করেন নিউইয়র্কের ইথাকার কর্নেল ইউনিভার্সিটি থেকে। এরপর চাকরি নেন হিউস্টনের টেক্সাস সাউদার্ন ইউনিভার্সিটিতে। ১৯৫৭ সালে ফিরে আসেন হাওয়ার্ডে ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে। এখানে দেখা হয় জ্যামাইকান প্রকৌশলী হ্যারল্ড মরিসনের সঙ্গে। পরের বছর বিয়ে করেন তারা। নামের শেষ অংশে যোগ হয় স্বামীর নাম। শিক্ষকতা ও পরিবারের দেখাশোনার পাশাপাশি ছোট এক লেখক দলে যোগ দেন। টনির প্রথম গল্প একটি কালো মেয়েকে নিয়ে, ¯্রষ্টার কাছে যে প্রার্থনা করত নীল চোখের জন্য, কারণ তার ধারণা সাদা মেয়েদের মতো নীল চোখই শুধু সুন্দর।
শিক্ষকতা ছেড়ে ‘র্যানডম হাউস’ প্রকাশনার সম্পাদক হলেন, নিউইয়র্কের সিরাকুজে, পরে নিউইয়র্ক সিটিতে। তারপর চাকরি ছেড়ে আবারও লেখায় মন দিলেন। কালো মেয়েটিকে নিয়ে লেখা ছোট গল্পটিকে উপন্যাসে পরিণত করলেন। লেখালেখিকে নিলেন ‘এক্সাইটিং’ ও ‘চ্যালেঞ্জিং’ হিসেবে। গল্পটি ব্লুয়েস্ট আই (১৯৭০) নামে উপন্যাস হিসেবে প্রকাশ করলেন। এরপরের উপন্যাসগুলো হলো : সুলা (১৯৭৩), সংস অব সলোমন (১৯৭৭), বেবি টার (১৯৮১) ও বিলাভ্ড (১৯৮৭)। বিলাভ্ড উপন্যাসটি পরের বছর পুলিৎজার পুরস্কার পায়। আমেরিকার বর্ণবৈষম্যের এক হৃদয়বিদীর্ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই উপন্যাসে। ১৮৫১ সালের একটি ঘটনা। ক্রীতদাসী মার্গারেট গার্নার তার কেন্টাকির মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে আসেন ওহাইওতে। ধরা পড়ার আগে তিনি তার সন্তানদের হত্যা করতে চান, দাসত্বের জীবনে ফিরিয়ে দেবার পরিবর্তে। একটি সন্তানকে হত্যাও করেন। মার্গারেট এজন্যে অনুতপ্ত নন, কারণ তিনি চান তার মতো দাসত্বের জীবন যেন সন্তানদেরকে স্পর্শ না করে। পরবর্তী উপন্যাসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, জাজ (১৯৯২) ও প্যারাডাইস (১৯৯৭)। টনি মরিসন সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান ১৯৯৩ সালে। তিনিই নোবেল বিজয়ী একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ নারী। তাঁর লেখায় বর্ণবাদী সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতা, আফ্রিকান-আমেরিকান নারীদের জীবন এবং বৈরী সমাজে তাদের শক্তি ও সংগ্রাম, পৌরণিক উপাদান, সুগভীর পর্যবেক্ষণ, সমবেদনা এবং ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক এসেছে অত্যন্ত কাব্যময় গীতলতায়। নানা বিষয়ে লেখা তাঁর গল্প, কবিতা ও আলোচনায় মূর্ত হয়েছে আফ্রিকান-আমেরিকান সংস্কৃতি, বর্ণবাদ, যৌনতা ও শ্রেণীবৈষম্যের কথা। ছোটবেলায় শোনা দক্ষিণাঞ্চলীয় আমেরিকানদের লোকগাথা সঙ্গীতের অনুরণনের অনুভব নিয়েই তিনি পাঠ করেন তলস্তয়, দস্তয়ভস্কি, ফ্লবেয়ার থেকে শুরু করে জেন অস্টেন পর্যন্ত।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েলসলি কলেজের সমাবর্তনে তাঁর দেয়া ভাষণটি চির-অমলিন হয়ে থাকবে। ভাষণে তিনি বলেন, ‘আজ তোমরা সাফল্যের সঙ্গে এক মহৎ, সম্মানজনক ও তাৎপর্যময় ডিগ্রী অর্জন করলে, তাই শুরুতেই তোমাদের ধন্যবাদ। এখন শুধু সামনে এগিয়ে যাওয়ার পালা। পৃথিবীর অনেক অবদান, অগণিত অর্জন শেষাবধি টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি শুধুমাত্র ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে না যাওয়ার কারণে। তোমরা এখন মুক্ত, স্বাধীন। তোমাদের আর পরীক্ষার চাপ নেই। তোমাদের সামনে এখন অবারিত জীবনের নতুন যাত্রাপথ। শিক্ষাজীবনের যত ঋণ, যত দায়Ñ সেসব শোধরানোর সময় এখন। যাত্রা শুরুর পর আগের গৎবাঁধা সব রোডম্যাপ ছুড়ে ফেলতে হবে। নতুনভাবে পথচলার পরিকল্পনা নিতে হবে তোমাদের নিজেকেই। পৃথিবীকে দেখার ভঙ্গিটা হতে হবে অভিনব, চিরসতেজ, নান্দনিক। অবাঞ্ছিত বিষয় বর্জন করে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছুকে পর্যবেক্ষণ কর। পথচলার সময় অবশ্যই মনে রাখবে, তুমি কোথা থেকে এসেছ। যে জায়গায় আমাদের জন্ম, সেখানকার ধুলোবালি আর স্বপ্ন আমাদের লালন করতে হবে। পুরো পথেই নিজেকে প্রশ্ন করবে, ‘আমি কেন এই পথে?’ এর একটা উত্তর আমি তোমাদের বলতে পারি। সেটা হলো, জিততে। তুমি জিততেই এ পথে নেমেছ। এ জেতাটা হচ্ছে নিজের সম্ভাবনাময় শক্তির জয়। এ জেতাটা হলো শ্রেষ্ঠ হিসাবরক্ষক, প্রকৌশলী, শিক্ষক কিংবা তুমি যা হতে চাও, তা হওয়ার। যে সম্ভাবনা তোমার মধ্যে আছে, সেটার জন্য নিজেকে বিশ্বাস কর। অন্য কারও সাফল্য দেখে নিজের সফলতাকে বিচার করিও না। অন্য কারও সফলতার গল্প পড়ার দরকার নেই, তুমি নিজেই নিজের গল্প হও। কোন বিষয়ে তোমার আগ্রহ বেশিÑ এটা তুমি জেনে যাবে একদিন। আবার কেউ কেউ আছে, যারা নিজের আগ্রহের জায়গাটা কখনোই জানতে পারে না। এরই মধ্যে তুমি যদি তোমার লক্ষ্যটাকে স্থির করে থাক, অথবা যদি এমন হয় তুমি তোমার লক্ষ্যকে সন্ধান করছ, তবে মনে রেখ, কৌতূহলই একদিন তোমার জীবনের সফলতা এনে দেবে। অন্যদিকে স্বপ্ন সত্যি করতে হলে তোমার ভেতরে যে ‘তুমি’ আছে, তার কথা শুনতে হবে। ইচ্ছে যদি বিস্তৃত হয়, বিশাল হয়, তোমার স্বপ্ন সত্যি হবেই। সততা, নৈতিকতা ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করে যাও। যদি তোমার স্বপ্নের সঙ্গে আপস না কর, তুমি সফল হবে, হবেই। পথ বেছে নিতে তুমি যেমন স্বাধীন, সফল হওয়াটাও তোমার জন্য উন্মুক্ত। দরকার শুধু কঠোর পরিশ্রম এবং একটি স্বপ্ন। আজ যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করলে, তাদের অনেকেই জান না, তোমরা পৃথিবীটাই বদলে দিতে যাচ্ছ। আমি জানি, সত্যিই তোমরা পৃথিবীটা বদলে দেবে। কিভাবে বদলাবে, সে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তোমাদেরকেই। আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ আদর্শের জন্য সংগ্রাম করি। জীবনে সংগ্রাম করাটাই তো চিরসত্য। দরিদ্র দেশের ছোট্ট কোন গাঁয়ে নাকি উন্নত দেশের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে একটি শিশু জন্ম নিল, সেটি মুখ্য বিষয় নয়। সব মানুষের আত্মমর্যাদা ও মৌলিক সাম্যতায় আমরা বিশ্বাস করি। আমরা আরও বিশ্বাস করি, সব মানুষ শান্তি চায়। আমরা অসাধারণ সুন্দর এক পৃথিবীর বাসিন্দা। যদিও তা বিভক্ত বিভিন্ন দলে, তবু আমরা একই মানব সম্প্রদায়ের অংশ। সমতার পৃথিবী গড়তে হলে এখন তোমাদের সহযোগিতা দরকার। তোমরা যে যেখানেই যাও, ভবিষ্যতে যে যা-ই কর না কেন, তোমরা সেই পৃথিবীতে যোগ দিতে যাচ্ছ, উত্তরোত্তর যার বিশ্বায়ন ঘটছে। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেখানে তোমরা সবাই এক হয়ে কাজ করতে হবে। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ছিলাম, তখন আমার একটা অভ্যাস ছিল এমন, আমি হঠাৎ করে অধ্যাপকদের কক্ষে হানা দিতাম। তাদের প্রশ্ন করতামÑ জীবনের অর্থ কী? অধ্যাপকরা ঘাবড়ে যেতেন, ভাবতেন আমার ‘নিওরোলজিক্যাল ডিজঅর্ডার’ হয়েছে। সবাই যে এমনটা ভাবতেন, তা কিন্তু নয়। অনেকেই উত্তর দেয়ার চেষ্টা করতেন। কেউ কেউ বলতেন, ‘সুখ’। আবার কেউবা বলতেন, ‘জ্ঞান’। আমার কাছে জীবনের অর্থ হলো, আমার কাছের মানুষকে সুখী করার জন্য কাজ করা। তোমাদের কাছেও জীবনের আলাদা আলাদা অর্থ থাকতে পারে। আর যদি না থাকে, তাহলে এ পথে ট্রাই করে দেখতে পার। অন্যের জন্য কিছু করার মধ্য দিয়ে নিজের আনন্দ খুঁজে নাও। তাহলে পৃথিবীটা আরও সুন্দর হয়ে উঠবে।
‘ইন্টারভিউ’ নামে একটি ম্যাগাজিনে ১ মে, ২০১২ সালে সাক্ষাতকারটি প্রকাশিত হয়। ম্যাগাজিনের পক্ষে সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেন ক্রিস্টোফার বোলেন। ফটোগ্রাফিতে ছিলেন বিখ্যাত সাংবাদিক ড্যামন উইন্টার।
আপনি তো ভার্জিননিয়া উলফ-এর আত্মহত্যা বিষয়ক বিষয়বস্তু নিয়ে গ্রাজুয়েশনের থিসিস করেছিলেন, তাই না?
আমি উলফ ও ফকনারকে নিয়ে থিসিস লিখেছিলাম। আমি তখন ফকনারের অনেক লেখা পড়েছি। আপনার হয়ত একটা বিষয় জানা না-ও থাকতে পারে। পঞ্চাশের দশকে আমেরিকান সাহিত্য একেবারেই নতুন ছিল। এটি ছিল একেবারেই বিচ্যুত ও আনকোরা। ইংরেজী সাহিত্য বলতে তা মূলত ইংরেজীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। আমেরিকান সাহিত্যকে বেশিকিছু করার জন্য এই উঁচুমাপের অধ্যাপকগণই ভরসা ছিলেন। তাদের সেসব কাজ এখন আমাকে নাড়া দিচ্ছে।
এই অধ্যাপকগণ কি তখন আফ্রিকান-আমেরিকান লেখকদের সাহিত্যকর্ম পড়াতেন?
তারা আফ্রিকান-আমেরিকান স্কুলেও তো সেসব লেখকদের সহিত্যকর্ম পড়াতেন না। আমি হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। আমার মনে পড়ে, আমি জানতে চেয়েছিলাম আমি শেক্সপিয়ারের সাহিত্যকর্মে কৃষাঙ্গ চরিত্রসমূহ নিয়ে একটা থিসিস লিখবো কি-না (তিনি হাসলেন)। শিক্ষক খুব বিরক্ত হলেন। তিনি বললেন,‘কী?’ তিনি এটিকে একটি নিচু শ্রেণীর বিষয় ভাবলেন। তিনি বললেন, ‘না, না, আমরা এসব করছি না। এটা খুবই ক্ষুদ্র বিষয়Ñএটা কিছুই না।’
আপনার শিরোনামগুলো অসাধারণ। এগুলোতে অকৃত্রিম বিশুদ্ধতা, অবিচ্ছিন্নতা এবং চেতনার বিস্তৃতি রয়েছে। একটা উপন্যাসের নাম ‘হোম’ রাখার ক্ষেত্রে তো যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিশীল হতেই হয়।
আমি যখন এই বইটি নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন এটার নাম রেখেছিলাম ‘ফ্রাঙ্ক মানি’। আমার সম্পাদকই আমাকে নাম পরিবর্তনের কথা বললেন। আমি যখন ‘সং অব সলোমন’ নিয়ে কাজ করছিলাম, তখন সেটিরও অন্য একটি নাম রেখেছিলাম। ঔপন্যাসিক জোনাথন গার্ডনার এটির নাম ‘সং অব সলোমন’ রাখতে প্রভাবিত করলেন। কেউ একজন বলল ‘সং অব সলোমন’ রাখা হোক। আমি বললাম, এটা ভয়ঙ্কর নাম। আমি তখন নফের অফিসে। জন গার্ডনারও সেখানে ছিলেন। তিনি বললেন, ‘সং অব সলোমন’ তো মিষ্টি একটা নাম। এইটা রাইখা দাও।’ আমি বললাম, ‘আপনি নিশ্চিতভাবেই রাখতে বলছেন?’ তিনি বললেন, ‘হ্যাঁ’। আমি বললাম, ‘আচ্ছা’। তারপর তিনি চলে গেলেন। আমি ভাবলাম, ‘আমি তার কথায় মনোযোগ দিচ্ছি কেন? সে নিজেই তো ‘সুর্যাস্তের সংলাপ’ নামে একটা একটা বই লিখেছেন। তার লেখালেখির শুরু থেকেই তো তিনি কোন ভাল নাম রাখতে পারেননি নিজের বইয়ের (হাসলেন)! কিন্তু ততক্ষণে বড্ড দেরি হয়ে গেছে।
‘সুলা’ বইটির পুনর্মুদ্রণে একটি ভূমিকা লিখেছিলেন। ভূমিকায় দুটি সন্তানের লালনপালন ও র্যানডম হাউসে ফুল-টাইম চাকুরির অতিরিক্ত চাপ নিয়ে এই বইটি লেখার কথা জানিয়েছেন। আপনি সে সময় কুইন্সে থাকতেন। আমার কাছে যেমনটা মনে হয়, আমরা তরুণ বয়সে লিখতে শুরু করা লেখকদের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিই। কিন্তু মধ্য বয়সে লেখালেখি শুরু করাটা তো অধিকতর কঠিন, বিশেষ করে ফুল-টাইম চাকরি ও সন্তান লালনের পর।
আমি তো ঊনচল্লিশ বছর বয়সে শুরু করেছিলাম।
ব্যাপক জনশ্রুতি আছে, আপনি সূর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠে লেখালেখি শুরু করেন।
সকালে আমি খুব প্রাণবন্ত থাকি। এই সময়টা গ্রাম্য কৃষকদের সময়। আমি সুর্যোদয়ের আগে ঘুম থেকে উঠতে পছন্দ করি। যাই হোক, আমি আমার ‘দ্য ব্লুয়েস্ট আই’ শেষ করার পর এটি অনেকের কাছে পাঠাই। তারপর অনেকের কাছ থেকেই আমি ফেরত চিঠি পাই। তারা অধিকাংশই এটিকে মানোত্তীর্ণ বলে জানায়। তবে একটি চিঠি পাই যেটিতে দেখা যায় কেউ একজন বইটিকে অন্যভাবে নিয়েছেন এবং এটিকে ভাল বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। সেই সম্পাদক একজন নারী ছিলেন। তিনি অবশ্য ভাষাশৈলী নিয়ে প্রশংসা করেছিলেন। তারপর লিখেছিলেন, ‘কিন্তু এটির কোন শুরু নেই, মধ্যভাগ নেই এবং সমাপ্তি নেই।’ আমার মনে হয়েছিল তিনি ভুল করেছেন। কিন্তু এটি আমাকে শিহরণ দিয়ে গিয়েছিল। তারপর ক্লদ ব্রাউন আমার কাছে কয়েকজনকে পাঠালেন। এদের মধ্যে হল্ট, রাইনহার্ট এবং উইনস্টন ছিলেন। ‘স্ক্রু হোয়াইটি’ বইটির লেখার পরের দিনগুলোর কথা। বইটির মধ্যে ‘স্ক্রু হোয়াইটি’ আন্দোলনের যে কয়েকটি আগ্রাসী বিষয়বস্তু ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল ‘কালোই নান্দনিক।’ আমি ভাবলাম, ‘এটি আসলে কী সম্পর্কে? তারা কী নিয়ে কথা বলছে? আমাকে নিয়ে? তারা বলতে চাচ্ছে, আমি সুন্দরী?’ তারপর ভাবলাম, ‘এক মিনিট অপেক্ষা করুন। এরা আমার দর্শনীয় কৃষ্ণাঙ্গ বগিতে আরোহণের আগে আমাকে এ নিয়ে বলতে দিন।’ (তিনি হাসলেন)। তুমি জান, বর্ণবাদ যা করতে পারে তা হচ্ছে আত্মবিতৃষ্ণা সৃষ্টি। এটি আমাদের আঘাত দেয়। এটি এমনকি ধ্বংসও করে দিতে পারে।
একজন বালিকা যে কি-না নিজেকে কুৎসিত ভাবত এবং সে নীল চোখ প্রত্যাশা করত। এমন একটি গল্প বলার মধ্য দিয়েই আপনার প্রথম উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন। এটিই মূলত পরিপূর্ণভাবেই ‘কালোই নান্দনিক’ আন্দোলনের বিপরীত। আপনার শুরুর দিনগুলোর কিছু সমালোচক যারা কি-না কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়েরই ছিল, এই উপন্যাসটি দ্বারা কি আপনি তাদেরকে ইঙ্গিত করেছিলেন? হ্যাঁ, তারা এটার নিন্দা করেছিল। সবচেয়ে চমৎকার যে জিনিসটি, সেটি আমি কোন সমালোচকের কাছ থেকে পাইনি। সেটি পেয়েছিলাম আমার এক ছাত্রীর কাছ থেকে। সে বলেছিল, ‘আমি ব্লুয়েস্ট আই পছন্দ করি, কিন্তু এমন একটি বই লেখায় আমি আপনার প্রতি উম্মাদনা বোধ করি।’ আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘কেন?’ সে জবাব দেয়, ‘কারণ এখন তারা আমাদের আকাক্সক্ষার বিষয়টি জেনে যাবে।’ বেশিরভাগ সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিই ছিল উড়িয়ে দেবার মতো। ঐ পারিপাশ্বিক অবস্থায় আমার মনে হয়েছিল বইটি কেউ পড়বে না। দেড় হাজার কপি ছাপা হওয়ার কথা থাকলেও ছাপা হয়েছে মাত্র ১২০০ কপি। আমার মনে হয় ওরা ৪০০ কপির বেশি ছাপেনি। বানতাম নরম মলাটের একটা বই কিনেছিল। এটা ছুড়ে ফেলে দেয়ার মতো ছিল। তারপর অসাধারণ কিছু একটা ঘটল। আমি মনে করি এই অসাধারণ ঘটনাটির পেছনে সিটি কলেজের ভূমিকা রয়েছে। বইটি ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সিটি কলেজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, প্রতিটি কারিকুলামে ভর্তি হওয়া নবাগতদের জন্য নারী এবং আফ্রিকান-আমেরিকান লেখকদের বই থাকবে। আমার বইও সে তালিকায় ছিল। তার মানে এই নয় যে বইটি শুধুমাত্র নবাগতদের শ্রেণীতেই পাঠ্য থাকছে, সেটি আরও অনেক ক্লাসেই পাঠের সুযোগ উন্মোচিত হয়ে যায়।
আপনাকে আমেরিকার ‘জাতীয় ঔপন্যাসিক’ বলা হয়। আপনাকে ‘আমেরিকার বিবেক’ও বলা হয়। মূলত ওয়াল্ট হুইটম্যান ছাড়া আরেকজন লেখককে চিন্তা করা কঠিন যার নাম জাতীয়ভাবে এত উচ্চকিত স্বরে উচ্চারিত হয়। আপনার কি কখনো মনে হয়েছে, এটি আপনাকে লেখার জগত হতে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে? এরকম বিরাট সাফল্য কি একদিক থেকে পায়রার খোপের জীবনে পরিণত করে না?
নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর আমি কিছুটা বিরূপ পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম। কিন্তু ¯্রষ্টাকে ধন্যবাদ, সে সময়ে আমি ‘প্যারাডাইস’ লিখছিলাম। এই পুরস্কারের জন্য আমাকে আহামরি কিছু করতে হয়নি। এখন আমি শুধু ভাল জিনিসগুলো গ্রহণ করি। আমার একটা ফরমায়েশি কাজের কথা মনে পড়ে। তবে আমি শুধু ভালগুলোই গ্রহণ করি। (তিনি হাসলেন)
নোবেল কমিটির একটি ভাবপ্রবণ ব্যাপার আছে। ওরা সকালে আমেরিকান নোবেল বিজয়ীকে ফোন দিয়ে ঘুম ভাঙায়। আপনার ক্ষেত্রেও কি তেমনটা হয়েছিল?
না, এই রীতি পরিবর্তন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নোবেল কমিটি এখন অনেক বেশি সুসভ্য। যখন থেকে তারা এই ব্যাপারটি অনুধাবন করতে পেরেছে, তখন থেকেই তারা সুবিধাজনক সময়ে পুরস্কার ঘোষণা করে। তারা মানুষকে অস্থির না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা এখন রাতেই ফোন করে এবং সে যে দেশেরই হোক, তার সুবিধা অনুযায়ী স্বাভাবিক সময়ে ফোন করে। আমার ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল, রুথ সিমন্স নামে আমার এক বান্ধুবী আছে। সে এখন ব্রাউনের প্রেসিডেন্ট। সিমন্সও তখন প্রিন্সটনে থাকত। সে আমাকে সকাল সাতটায় ফোন করে বলল, ‘তুমি নোবেল পেয়েছ। আমি ভাবলাম, কী? আমার মনে হয়েছিল সিমন্স ভুল দেখেছে।
নোবেল পুরস্কারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন এমনটা কি আপনি কি জানতেন?
সত্যি বলতে আমি এমনটা কখনো ভাবিইনি। সুতরাং আমি আমি তার উপর চড়াও হলাম। আমি তাকে বললাম, ‘তুমি আসলে কী বলছ?’ কারণ আমি ভেবেছিলাম, আমি যা জানি না, তা সে কী করে জানবে? সে আমকে আবার ফোন করল। আমি বললাম, ‘তোমার আসলে কী হয়েছে? কোথায় এসব শুনেছ তুমি?’ সে বলল, ‘আমি ব্রায়ান্ট গাম্বেলের টুডে শোতে শুনেছি। তখন আমি ভাবলাম, বেশ...এমনটা হতে পারে? কিন্তু আমি পরে জানতে পেরেছি, এরকম অনেক মুহূর্ত আছে যা আমার ভাবনারও অতীত। অনেকে শুনে বিশ্বাস করেছেন তারা পুরস্কার পেতে যাচ্ছেন, সাংবাদিকরা তাকে চারপাশে জটলা পাকিয়েছে, অথচ তারা পরে পুরস্কার পায়নি।
আমার মনে হয় বেচারা নরম্যান মেইলারের ক্ষেত্রে এমনটা হয়েছিল। এমনকি বন্ধুরাও তাকে বলেছিল সে নোবেল পেয়েছে এবং তাকে সাক্ষাতকার দিতে হবে। কিন্তু সে কোনদিনই নোবেল পায়নি।
আমি জানি। এটা জয়েস ক্যারোল ওটসের ক্ষেত্রেও একবার ঘটেছিল। সাংবাদিকরা বাইরে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু আমার জানা ছিল না আমাকে কী করতে হবে। আমি সোজা ক্লাস নিতে চলে গিয়েছিলাম, তাই না? এবং তারপর আমি সাড়ে বারোটায় সুইডিশ এ্যাকাডেমির ফোন পাই। তারা জানায় আমি নোবেল পেয়েছি। ফোন দেয়ার জন্য এটা দিনের একটা স্বাভাবিক সময়ই ছিল। আমি তখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত হতে পারিনি। আমি বললাম, ‘ঘোষণাটা কি ফ্যাক্স করে দেবেন?’
আপনি লিখিতভাবে চাচ্ছিলেন? (হাসি)
এটা ঠিক ধরেছেন। কিন্তু সেই ব্যাপারটিই একটা দারুণ ব্যাপার। লিখিতভাবে ঘোষণা দেখতে পাওয়াটা সবচেয়ে বড় নিশ্চয়তা ছিল।
আপনি ১৯৮৩ সালে চূড়ান্তভাবে সম্পাদনার চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছিলেন লেখালেখিতে মনোনিবেশ করার জন্য। সেক্ষেত্রে আপনি কি চাকরিটা ছেড়ে আসার পর এমনটা বোধ করেছেন, ঠিক আছে, আর ফিরে না যাওয়াই ভাল?
এটা একটু ভিন্ন রকম ব্যাপার। আমি তখন চাকরি ছেড়ে এসে করিডরে বসেছিলাম। (তিনি তাঁর করিডরের জানালার দিকে ইঙ্গিত করেন) এখানে যে হাডসন নদীটা, এটা তখন এতটা সুন্দর ছিল না। আমি সেখানেই বসে ছিলাম এবং কিছুটা ভীতও ছিলাম। ভীত না বলে উদ্বিগ্নও বলা যেতে পারে। আমার কোন চাকরি ছিল না। তখনও বাচ্চারা আমার সঙ্গে। এটা এক বিচিত্র রকমের অনুভূতি। এরপর মনে হলো, আমি আসলে উদ্বিগ্ন নই, এটা এক ধরনের সুখ, সুখের অনুভূতি।
এটাকে মুক্তি বলছেন?
মুক্তির চেয়েও বেশি কিছু। আমি সত্যিই সুখী ছিলাম। যা বলা দরকার, আমার মনে হয় আমি তা বলতে পারিনি। আমি ঠিক তেমনটাও অনুভব করিনি। এটা মূলত সুখ এবং অন্য কোন একটা অনুভূতির সংমিশ্রণ ছিল। তারপরই আমি ‘বিলাভ্ড’ লিখেছিলাম। এই বইটি লেখার সময় আমার কাছে আবেগে প্লাবিত হওয়ার মতো বোধ হয়েছিল।
২০০৮ সালে ফিরে আসি। বারাক ওবামা ২০০৮ সালের নির্বাচনের সময় আপনার সমর্থন চেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আপনি তাকে সমর্থন দিয়েছিলেনও। আপনি বলেছিলেন, তাকে ক্ষমতায় বসানোটা তার কর্মেরই প্রতিদান হতে পারে। আপনি এটিকে বিপ্লবের পরিবর্তে আবশ্যক পরিবর্তন বলেছিলেন।
আমি এটা বলেছিলাম? এটা খুবই ভাল কথা। (তিনি হাসলেন)
আপনি বলেছিলেন। এখন তার পুনর্নির্বাচনের আগমুহূর্তে এসে কি আপনার মনে হচ্ছে ওবামা তার ইশতেহার বাস্তবায়ন করতে পেরেছেন?
অনেক। অনেক। আমি যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়েও অনেক বেশি ভাল করেছেন।
আমারও সর্বোপরি তেমনটাই মনে হয়। তবে কিছু মুহূর্তে আমি সংশয়ে পড়ে যাই। একজন প্রেসিডেন্টের ওপর কোন কোন সময়ে আস্থা হারানোর ব্যাপারটি তো স্বাভাবিক।
অবশ্য এমনটা হতেই পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমি তার প্রতি বৈরিতা পোষণ প্রত্যাশা করি না। আমি জানি কিছু ভুল হয়ত রয়েছে, কিংবা বেশি সংখ্যক ভুলও থাকতে পারে। কিন্তু বৈরিতা পোষণ করাটা সত্যিই এক ধরনের উন্মাদনা। যারা ওবামাকে ঘৃণা করে, তাদের কাছে ওবামার কাজের কোনো মূল্যই নেই, তা সে যা-ই করুক। একেবারেই মূল্যহীন। তারা যা বলে তা একেবারেই স্ববিরোধী।
ঢাকা, বাংলাদেশ শনিবার ২৭ এপ্রিল ২০২৪, ১৪ বৈশাখ ১৪৩১