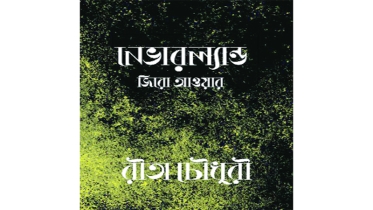সাহিত্যের বহুমাত্রিক আঙিনায় যার যুগান্তকারী অবদান আজও অম্লান, সেই রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান মনস্কতাও ছিল তেমনি অসাধারণ। মননশীলতায় ভাবনা এবং বস্তু দুটোই কবিকে সমানভাবে আকৃষ্ট করে, প্রাণিত করে। বিজ্ঞান চেতনা তাঁর এসব চিন্তার সম্পূরক। আর সেই কারণে বোধহয় ভারত উপমহাদেশ তথা এশিয়া মহাদেশের তিন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে কবির অকৃত্রিম ঘনিষ্ঠতা, বন্ধুত্বও নিরবচ্ছিন্ন হৃদ্যতা বরাবরই বজায় ছিল। শুধু হৃদয়ের সম্পর্কেই নয়, বিষয়গতভাবে ও তিনি বিজ্ঞানের এই তিন দিকপালের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে বাঁধা ছিলেন। কবির নোবেল প্রাপ্তির প্রায়ই এক দশক আগে জগদীশচন্দ্রের বিশ্বজোড়া খ্যাতি কবিকে উৎসাহিত, মুগ্ধ ও আকৃষ্ট করে রাখে বিজ্ঞানের এই নিরন্তন সাধকের নিবেদিত গবেষণার প্রতি। দুই বন্ধুর প্রচুর পত্রে এর প্রমাণ মেলে। শুধু তাই নয়, জীবনব্যাপী চিন্তায়, অর্থে, সাহচর্যে যেভাবে জগদীশকে ঘিরে রাখেন তা থেকেও অনুমেয় বিশ্ববরেণ্য এই কবির বিজ্ঞানপ্রীতি। তেমনি বলা যায় প্রফুল্ল চন্দ্র ছিলেন তার অকৃত্রিম বন্ধু, আজীবন সুহৃদ। আর তার ‘বিশ্বপরিচয়’ গ্রন্থটি তো দিয়েই দিলেন আর এক সমাদৃত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। যশস্বী পরিসংখ্যানবিদ প্রশান্ত মহালনবিসের সঙ্গেও ছিল তার গভীর সখ্য। কৃতী এই বিজ্ঞানী কবির ভ্রমণে ও তার সফরসঙ্গী হতেন। প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানের যে নিগূঢ় সম্পর্ক, অচ্ছেদ্য মেলবন্ধন সেটা তিনি অনুভব করতেন কিশোর বয়স থেকেই। ঠাকুর বাড়িতে নিয়মিত আসা সীতানাথ দত্তই ছিলেন তার বিজ্ঞানের আদিগুরু। পিতা মহর্ষিও তাকে ডালহৌসির পাহাড়ের ডাকবাংলোর আঙিনায় বসিয়ে তারা-গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে পরিচয় করাতেন। ‘বিশ্ব পরিচয়’ গ্রন্থের ভূমিকায় তা স্মরণ করে কবি লেখেন- ‘সন্ধ্যাবেলায় গিরিশৃঙ্গের বেড়া দেয়া নিবিড় নীল আকাশের স্বচ্ছ অন্ধকারে তারাগুলো যেন কাছে নেমে আসত। তিনি আমাকে নক্ষত্র চিনিয়ে দিতেন। তারা চিনিয়ে দিতেন। শুধু চিনিয়ে দেয়া নয়, সূর্য থেকে তাদের কক্ষচক্রের দূরত্বমাত্রা, প্রদক্ষিণের সময় এবং অন্যান্য বিবরণ আমাকে শুনিয়ে যেতেন। তিনি যা বলে যেতেন তাই মনে করে তখনকার কাঁচা হাতে আমি একটি বড় প্রবন্ধ লিখেছি। জীবনে এই আমার প্রথম ধারাবাহিক রচনা, আর সেটা বৈজ্ঞানিক সংবাদ নিয়ে।’ তার বিশ্ব পরিচয় বইটি পরমাণুলোক, নক্ষত্রলোক, সৌরজগৎ, ভূলোক বিশ্ব জগতের এই বৈজ্ঞানিক আবর্তনের মধ্যেই আবর্তিত।
বিজ্ঞান শুধু জানার, বোঝার কিংবা দেখার বিষয় নয়, তাকে নিজের আয়ত্তে এনে প্রতিদিনের কর্মকা-ের সঙ্গে যুক্ত করাটাই সত্যিকারের বিজ্ঞান ভাবনা এবং চর্চা, শিক্ষার মাধ্যমে এই বিজ্ঞানকে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে মেলাতে হবে। সেই যৌক্তিক বাণী বের হয়ে আসে আলোচিত গ্রন্থের ভূমিকার শুরুতে, ‘শিক্ষা যারা আরম্ভ করেছে গোড়া থেকেই বিজ্ঞানের ভা-ারে না হোক, বিজ্ঞানের আঙিনায় তাদের প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক। এই জায়গায় বিজ্ঞানের সেই প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার কাজে সাহিত্যের সহযোগিতা স্বীকার করলে তাতে অগৌরব নেই। সেই দায়িত্ব নিয়েই আমি এই কাজ শুরু করেছি। কিন্তু এর জবাবদিহি একা কেবল সাহিত্যের কাছেই নয়, বিজ্ঞানের কাছেও বটে।’ শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক প্রমথ নাথ সেনগুপ্তের লেখা পা-ুলিপিটি ভাষায়, বর্ণনায় আমূল পরিবর্তন করে বিশ্ব পরিচয় প্রন্থটি কবি নিজের ভাবনা আর অনুভূতিতে সাজান। জ্যোতিবির্র্দ্যার ওপরও রবীন্দ্রনাথের অগাধ পা-িত্য ছিল।
১৯৩৭ সালে লেখা এই বইটি সারাজীবনের বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনা, চিন্তা-চেতনার অনবদ্য স্বাক্ষর। পরিণত বয়সে শুদ্ধ বিজ্ঞানচর্চা, তারও বহু আগে কৈশোর থেকে বিজ্ঞানের প্রতি দরদ, বৈজ্ঞানিক মুক্তজ্ঞানের প্রতি অতিমাত্রায় আগ্রহ তাকে এমন একটি বিজ্ঞান সমৃদ্ধ বই লিখতে অনুপ্রাণিত করে। তার ভাষায়- ‘আজ বয়সের শেষ পর্বে মন অভিভূত নব্যপ্রাকৃতত্ত্বে-বৈজ্ঞানিক মায়াবাদে। তখন যা পড়েছিলুম তার সব বুঝিনি। কিন্তু পড়ে চলে ছিলুম। আজও যা পড়ি তার সবটা বোঝা আমার পক্ষে অসম্ভব’, অনেক বিশেষজ্ঞ প-িতের পক্ষেও তাই। বিজ্ঞান থেকে যারা চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করেন তারা তপস্বীমিষ্টান্নমিতরে জানা : আমি রস পাইমাত্র। সেটা গর্ব করার মতো কিছু নয়, কিন্তু মন খুশি হয় বলে যথা লাভ। এই বইখানা সেই যথা লাভের ঝুলি, মাধুকরী বৃত্তি নিয়ে পাঁচ দরজা থেকে এর সংগ্রহ।
মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার গুরুত্ব অনুভব করেন যখন তিনি নিজ উদ্যোগে গ্রামে-গঞ্জে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নানাবিধ উন্নয়ন কাজ হাতে নেন। সঙ্গে থাকে তার বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশ ভ্রমণের বাস্তব অভিজ্ঞতা। ১৬-১৭ বয়সে যখন তিনি বিলেত যান সেখানকার নতুন সভ্যতার অনেক কিছু তাকে মুগ্ধ করলেও বৈজ্ঞানিক শক্তিটি তার মনে তেমন সাড়া জাগায়নি। তার ‘য়ুরোপ প্রবাসী পত্র’ থেকে সে রকম কোন আলোচনা বের হয়ে আসে না। বরং আশি বছর বয়সে ‘সভ্যতার সঙ্কট’ প্রবন্ধে তাকে বলতে শুনি, ‘আমি যখন অল্প বয়সে ইংল্যান্ডে গিয়েছিলুম, সেই সময় জন ব্রাইটের মুখ থেকে পার্লামেন্ট এবং তার বাইরে কোন কোন সভায় যে বক্তৃতা শুনেছিলুম তাতে শুনেছি ইংরেজদের বাণী। সেই বক্তৃতায় হৃদয়ের ব্যাপ্তি জাগতিক সকল সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে আমার আজ পর্যন্ত মনে আছে এবং আজকের এই শ্রীভ্রষ্টের দিনেও আমার পূর্ব স্মৃতিকে রক্ষা করছে।’ ১৮৯৩ সালে লেখ পঞ্চভূত প্রবন্ধে ইউরোপীয় সভ্যতা নিয়ে কবির আপেক্ষ, ‘য়ুরোপে সম্প্রতি যে এক নব সভ্যতার যুগ আবির্ভূত হইয়াছে এ যুগে ক্রমাগতই নব নব জ্ঞান বিজ্ঞান মতামত স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে?’ যন্ত্রতন্ত্র উপকরণ সামগ্রীতেও একেবারে স্থানাভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবিশ্রাম চাঞ্চল্যে কিছুই পুরাতন হইতে পারিতেছে না।’
কিন্তু ৫৫ বছর বয়সে ১৯১৬ সালে যখন তিনি জাপান ভ্রমণে যান তখন শিল্পোন্নত জাপান তাকে মুগ্ধ করে, অনাবিল আনন্দ দেয় এবং অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতাও তিনি সঞ্চয় করেন। ‘জাপান-যাত্রী’ প্রবন্ধে বলেন, ‘কাজের শক্তি, কাজের নৈপুণ্য এবং কাজের আনন্দকে এমন পুঞ্জীভূতভাবে একত্র দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে বুঝতে পারলুম, এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা আছে। এই এতবড় একটা শক্তি যখন আপনার আধুনিক কালের বাহনকে পাবে অর্থাৎ বিজ্ঞান যখন তার আয়ত্ত হবে, তখন পৃথিবীতে তাকে বাধা দিতে পারে এমন কোন শক্তি আছে? তখন তার কর্মের প্রতিভার সঙ্গে তার উপকরণের যোগসাধন হবে।’
অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে যন্ত্রশক্তির সফল মিলনই একটি দেশকে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবে। জাপানীরা মাতৃভাষায় শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেখে তিনি আনন্দিত হন। প্রত্যাশিত ফলও তারা পাচ্ছেন। কবি মনে করতেন নিজস্ব ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে আধুনিক সভ্যতাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। ইউরোপীয় সভ্যতার যা কিছু কল্যাণকর, মাঙ্গলিক তার সঙ্গে মিলাতে হবে আমাদের নিজস্বতাকে। আমাদের ঐতিহ্যিক অস্বিত্ব যা যুগ যুগ ধরে আবহমান বাঙালীকে সমৃদ্ধির পথ দেখায় সেখানে থেকে কোনভাবেই সরা যাবে না। নব নব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে প্রতিদিনের কর্মযজ্ঞের সেতুবন্ধন তৈরি না হলে জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে পড়ব এবং পড়েছিও।
তার জমিদারি এলাকায় তিনি চেষ্টা করেন কৃষিনির্ভর গ্রামগুলোর কৃষির আধুনিকায়ন। পুত্র রবীন্দ্রনাথকে কৃষি অর্থনীতির ওপর নতুন জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর আমেরিকাতে পাঠান। চাষাবাদে উন্নত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে এর সফলতাকে সর্বস্তরের জনগণের দ্বারে পৌঁছে দিতে তিনি কার্পণ্য করেননি। এর সঙ্গে মাতৃভাষায় শিক্ষার বিষয়টিও বিশেষ গুরুত্ব পায়। তার মতে চাষের লাঙ্গল সেও এক প্রকার যন্ত্র, কিন্তু বহু পুরনো। আধুনিক উদ্ভাবনী শক্তি এই গতানুগতিক শ্রমের উপকরণকে পরাভূত করে পুরো কৃষি ব্যবস্থাকে যন্ত্র সভ্যতার ওপর দাঁড় করাবে। ব্যক্তিগত উদ্যোগ আর উদ্যমে হতদরিদ্র প্রজাদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যা করেন তা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।
আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে তার ধারণা যখন বদ্ধমূল তখন তিনি যান বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায়। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার শুধু যান্ত্রিক বিকাশই নয় সম্পদের সুষমবণ্টনও তাকে মুগ্ধ করে। বার বার উপলব্ধিতে আসে শিক্ষাই মূল শক্তি এবং অবশ্যই তা সকলের জন্য। তার মতে, ‘আমাদের সকল সমস্যার সবচেয়ে বড় রাস্তা হচ্ছে শিক্ষা। এতকাল সমাজের অধিকাংশ লোক শিক্ষার পূর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত- ভারতবর্ষ তো প্রায়ই সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এখানে সেই শিক্ষা যে কি আশ্চর্য উদ্যমে সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হচ্ছে তা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষার পরিমাণ শুধু সংখ্যায় নয়, তার সম্পূর্ণতায়, তার প্রবলতায়। কোন মানুষই যাতে নিঃসহায় ও নিষ্কর্মা না থাকে এ জন্য কি প্রচুর আয়োজন, ও কী বিপুল উদ্যম। শুধু শ্বেত রাশিয়ার জন্য নয়, মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্য জাতের মধ্যেও এরা বন্যার মতো বেড়ে শিক্ষা বিস্তার করে চলেছে। সায়েন্সের শেষ ফসল পর্যন্ত যাতে তারা পায় এই জন্য প্রয়াসের অন্ত নেই।’
কৃষিনির্ভর গ্রাম বাংলার সিংহভাগ অর্থনীতি চাষাবাদকে কেন্দ্র করে। জাতীয় আয় থেকে শুরু করে জনগোষ্ঠীর অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসার যোগান দেয়া সবই কৃষির ওপর নির্ভরশীল। মান্ধাতা আমলের কৃষি যন্ত্রপাতি নতুন সভ্যতায় একেবারেই অচল। তাই পরিবর্তিত রাশিয়ার কৃষি অর্থনীতির নবযুগ তাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। রূপান্তরিত রাশিয়ার সঙ্গে তুলনা করেন নিজ দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে। তিনি বলেন, ‘নিজের দেশের চাষীদের কথা মনে পড়ল। মনে হলো আরব্য উপন্যাসের জাদুকরের কীর্তি। বছর দশেক আগে এর ঠিক আমাদেরই দেশের জনমজুরদের মতোই নিরক্ষর, নিঃসহায়, নিরন্ন ছিল, তাদেরই মতো অন্ধ সংস্কার, মূঢ় ধার্মিকতা, দুঃখে, বিপদে এরা দেবতার দ্বারে মাথা খুঁড়েছে, পরলোকের ভয়ে পান্ডা পুরুতদের হাতে তাদের বুদ্ধি ছিল বাঁধা, আর ইহলোকের ভয়ে রাজপুরুষ, মহাজন ও জমিদারের হাতে। যারা এদের জুতাপেটা করত, তাদের সেই জুতা সাফ করা এদের কাজ ছিল। হাজার বছর এদের প্রথা পদ্ধতির বদল হয়নি। যানবাহন, চরকা ঘানি সমস্ত প্রপিতামহের আমলের, হালের হাতিয়ারে হাত লাগাতে বললে বেঁকে বসত। আমাদের দেশের ত্রিশ কোটির পিঠের ওপর চেপে বসেছে ভূতকালের ভূত, চেপে ধরেছে তাদের দু’চোখ-এদেরও ঠিক তেমনই ছিল। ক’টা বছরের মধ্যে এই মূঢ়তার অক্ষমতার অভ্রভেদী পাহাড় নড়িয়ে দিলে যে কী করে, সে কথা এই হতভাগ্য ভারতবাসীকে যেমন একান্ত বিস্মিত করেছে এমন আর কাকে করবে বল।’
ভাবুক, রোমান্টিক কবির কি অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সমাজ বিশ্লেষণ। আর তাই বিশ্বব্রহ্মা-ের সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা এসব বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ কিংবা শুধু বিজ্ঞান চেতনাই নয়, সমাজ নিরীক্ষণের ভূমিকায়ও নামেন একজন দক্ষ সমাজ বিজ্ঞানীর মতো।
বিদেশী অভিজ্ঞতালব্ধ ধ্যান-ধারণা, সম্পদ, জনবল, সার্বজনীন শিক্ষা সর্বোপরি কর্মশক্তিকে অপরিহার্য করে দেশের মঙ্গল, জনসাধারণের কল্যাণ সাধনে আজীবন নিজেকে সম্পৃক্ত রাখেন। তার শান্তি নিকেতনে বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা কর্মসূচী, শ্রী নিকেতনের কৃষি অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ সর্বোপরি সমবায় ব্যবস্থার প্রচলন করে প্রজামঙ্গলের যে দৃষ্টান্ত তৈরি করেন তা আজও অনুকরণীয়। শুধু চিন্তায় কিংবা সৃজনে নয় ব্যবহারিক জীবনেও বিজ্ঞাননির্ভর কর্মযোগ কবিকে যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার স্বাক্ষর বিভিন্ন জনহিতকর কাজে দীপ্ত হয়ে আছে।
নিত্য নতুন আবিষ্কার যেমন সভ্যতাকে চরম উৎকর্ষের দিকে নিয়ে যায় তেমনি এর অশুভ প্রয়োগগুলোও পুরো সমাজকে হানাহানি, বিপর্যয় এবং অবক্ষয়ের শেষ পর্যায়ে নামিয়ে দেয়। বিজ্ঞানের বিপরীত প্রতিক্রিয়াগুলোও তাকে আহত করে, চিন্তিত করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত দেখার দুর্ভাগ্য তার হয়নি। যে জাপানের নতুন সমাজ শক্তি, বিজ্ঞান চেতনা তাকে মুগ্ধ করেছিল সেই জাপানের দুটো প্রধান শহর হিরোশিমা, নাগাসাকি বিজ্ঞানের অপশক্তির কাছে পর্যুদস্ত, ক্ষতবিক্ষত হয়। যুদ্ধের বীভৎসতা আজও তারা বয়ে বেড়াচ্ছে। জানি না কবি এটা সহ্য করতে পারতেন কিনা। মনুষ্যত্বের সমাধিস্থলে তাকে দাঁড়াতে হলো না। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকা-ের প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ কর্তৃক পুরস্কৃত ‘নাইট’ উপাধি তিনি বর্জন করেছিলেন। তবে তার সামনে ঘটে যাওয়া ১ম বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ এবং পরিণতি তাকে মর্মাহত এবং ক্ষুব্ধ করেছিল। সেই সময়কার মনন এবং সৃজনে সেই বিষণœ অনুভব আজও স্পষ্ট হয়ে আছে। এ ছাড়াও এক প্রাকৃতিক দুর্যোগে (সম্ভবত ভূমিকম্প) অনেক লোকের প্রাণহানিতে মহাত্মা গান্ধী বলে ছিলেন বিধাতার অভিশাপ। গান্ধীকে পরম শ্রদ্ধা করেও বিজ্ঞানসচেতন কবি বলেছিলেন ঈশ্বর মানুষের জন্য। তাই এটা কখনও তার বিধান হতে পারে না। এটা প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়ম।
শীর্ষ সংবাদ: