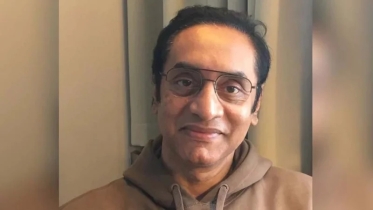আদিম শস্য গবেষণার মাধ্যমে একটি দুর্লভ ডাটাব্যাংক পেতে পারে বাংলাদেশ
আদিম শস্য গবেষণার মাধ্যমে একটি দুর্লভ ডাটাব্যাংক পেতে পারে বাংলাদেশ। অতীতের অমূল্য ডাটা কাজে লাগিয়ে বর্তমান প্রকৃতি পরিবেশের উন্নতি, উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তা বাড়ানো সম্ভব। শস্য আবাদের ইতিহাস জানা গেলে জানা যাবে এ অঞ্চলের মানুষের নির্ভুল ইতিহাসও। এভাবে কৃষি এবং মানুষের ইতিহাসÑ দুটোরই পুনর্গঠনে ভূমিকা রাখতে পারবে সদ্য শুরু হওয়া গবেষণা।
প্রত্নউদ্ভিদ বিজ্ঞানী মিজানুর রহমানসহ কৃষি ও ইতিহাস গবেষণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।
প্রত্নশস্য গবেষণার মূল বৈশিষ্ট্যগুলোর খোঁজ করতে গিয়ে জানা যায়, এ গবেষণার জন্য আদি ঐতিহাসিক যুগে ফিরে যাওয়া আবশ্যক। তবে এই ফিরে যাওয়া পেছনে পড়ে থাকার জন্য নয়। বর্তমানকে এগিয়ে নেওয়া, ভবিষ্যৎকে মজবুত ভিত্তি দেওয়ার জরুরি প্রয়োজনে। অভিন্ন চাওয়া থেকে এ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন মিজানুর রহমানও। জনকণ্ঠকে তিনি বলেন, ‘এটি মৌলিক গবেষণা। গবেষকরা প্রতœস্থান থেকে মাটির নমুনা নিয়ে শ্যস্যের অরিজিন রিসার্চ করেন। জিওগ্রাফিক্যাল অরিজিন খুঁজে বের করেন। এখানে হাইপোথিসিস গুরুত্ব পায় না। যে কোনো বিষয়ে হাইপোথিসিস হতে পারে। তবে বিজ্ঞাননির্ভর প্রত্নউদ্ভিদ গবেষণায় প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত সেটিকে নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া যায় না।
এ কারণে আদিম শস্য গবেষণার সুফলও বেশি।’ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সুফলগুলো কী হতে পারে? জানতে চাইলে গবেষক বলেন, ‘আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান। কিন্তু ভবিষ্যতের কৃষিকে এগিয়ে নিতে পারে এমন অনেক জরুরি তথ্য আমাদের হাতে এখনো নেই। এই যেমন, প্রাগৈতিহাসিক যুগে এ অঞ্চলের প্রকৃতি পরিবেশ জলবায়ু কেমন ছিল? কীভাবে কোন অবস্থায় এর বিবর্তন ঘটেছে? কী কী গাছ হতো এখানে? পানি কত ছিল? কেমন ছিল? কতবার বন্যা বা খরা হয়েছে? আরও অনেক প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর আমাদের জানা নেই। আবহাওয়া অফিস ছিল না তখন। জলবায়ু সম্পর্কে কোনো ডাটাবেজ ছিল না। কিন্তু প্রত্নশস্য গবেষণার মাধ্যমে এসব প্রশ্নের উত্তর বের করা যাবে।’ এভাবে বাংলাদেশের প্রকৃতি পরিবেশ প্রতিবেশ ও কৃষি সংক্রান্ত একটি সমৃদ্ধ ডাটাব্যাংক তৈরি করা যাবে বলে জানান মিজানুর।
অভিন্ন ব্যাখ্যায় বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘আমরা লক্ষ্য করছি এখন ক্লাইমেট চেঞ্জ ও এর প্রভাব নিয়ে বিশ্ববাসী উদ্বিগ্ন। দিন দিন পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে। অভাব দেখা দিচ্ছে পানির। বৃষ্টির সময় খরা। শীতের সময় গরম। দুই মাসের জায়গায় এক মাসে শেষ হয়ে যাচ্ছে শীতকাল। তাপমাত্রা বাড়ছে। এসবের প্রভাবে ফসল উৎপাদন হুমকির মুখে পড়ে যাচ্ছে।’
তিনি বলেন, আমরা অনুমান করতে পারি, অতীতেও ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে। কেন হয়েছে? কৃষকরা কী ধরনের পলিসি অ্যাপলাই করেছেন তখন? অনাবৃষ্টি বা খরার সময় আদিতে কী ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়েছিল? মাটি খুঁড়ে পাওয়া প্রতœশস্যের মাধ্যমেই উত্তরগুলো জানা যাবে।’
তিনি বলেন, ‘প্রত্নশস্য গবেষণার মাধ্যমে পাওয়া তথ্য সরকারের ধান গবেষণা বা কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ অনেকেই কাজে লাগাতে পারবেন। এমনভাবে কাজে লাগাতে পারবেন যে, জলবায়ু পরিবর্তন হলেও ফসল উৎপাদন হ্রাস পাবে না। বরং চাষাবাদে বৈচিত্র্য আসবে।’ এভাবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রত্নউদ্ভিদ গবেষণা বড় ভূমিকা রাখবে বলে মনে করেন সুফি মোস্তাফিজ।
তিনি জানান, নিজেদের কৃষি পণ্যের জি আই (ভৌগোলিক উৎস নির্দেশক) স্বীকৃতি আদায়েও ভূমিকা রাখবে প্রত্নউদ্ভিদ গবেষণা। উদাহরণ দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের এই শিক্ষক বলেন, ‘ধরা যাক, আমাদের এখানে বহুকাল আগে একটা ফসল উৎপন্ন হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি সে তথ্য না জানি, বিশ্বের কাছে এর উৎস প্রমাণ করতে না পারি, তা হলে অনেক পরে চাষ করেও ওই ফসলের জিআই স্বীকৃতি অন্য কোন দেশ আদায় করে নিতে পারে। এমনটি হয়েছেও।’ প্রত্নশস্য গবেষণার সহায়তা নিলে এই ক্ষতিতে পড়তে হবে না বলে জানান তিনি।
এদিকে, প্রত্নউদ্ভিদ গবেষণার তথ্য উপাত্ত বাংলাদেশের কৃষির ইতিহাস এবং সেই সূত্রে এ অঞ্চলের মানুষর ইতিহাস পুনর্গঠনেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আশা করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, জীবন ধারণের জন্য মানুষ প্রথমে শিকার ও সংগ্রহে মনোযোগী হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে বিরাট অগ্রগতি সাধিত হয় কৃষি আয়ত্তে আসার পর। ইতিহাসবিদদের মতে, আজকের আধুনিক মানুষের আবির্ভাবের পর আরও ১০ থেকে ১২ হাজার বছর সময় লেগেছিল কৃষি আয়ত্তে আনতে। কৃষি সভ্যতার মধ্য দিয়েই প্রি-আরবান সিভিলাইজেশন ও পরে আরবান সিভিলাইজেশন বা নগর সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। তাই আজকের ইতিহাস জানতে অতীত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
এ প্রসঙ্গে ফারটাইল ক্রিসেন্ট অঞ্চলের ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে মিজান বলেন, ‘গম ও বার্লির ইতিহাস উদঘাটনের মাধ্যমে ওই অঞ্চলের মানুষের আদিম ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে। একইভাবে উত্তর-পূর্ব ভারত থেকে মধ্য-গাঙ্গেয় উপত্যকার মানুষের প্রধান খাদ্যশস্য যেহেতু ধান, ধানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানা গেলে এ অঞ্চলের আধুনিক মানব বসতি, সমাজ বিকাশের ধারা ও তাদের মোবিলিটি সম্পর্কে জানা যাবে।’
গবেষণার আলোকে মিজান বলেন, ‘পৃথিবীতে সভ্যতার অনেকগুলো কেন্দ্র ছিল। একটির সঙ্গে অন্যটির যোগাযোগ স্থাপন হয়েছিল ফসলের মাধ্যমে। একেকটি ফসলের উৎপত্তি একেক জায়গায়। পরে সেই ফসল বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যেমন, জাপোনিকা ধান বাংলাদেশে এসেছে পূর্ব দিক থেকে। চীন থাইল্যান্ড বার্মা ও উত্তর-পূর্ব ভারত হয়ে এ দেশে ঢুকেছিল। খাদ্য বা ধান তো মানুষই বহন করে নিয়ে এসেছে। এই সূত্রে বাংলাদেশ অঞ্চলের মানুষের বসতি স্থাপনের ইতিহাসটিও আমরা পেয়ে যাচ্ছি। একইভাবে উয়ারী-বটেশ^র থেকে অনেক প্রাগৈতিহাসিক হাতিয়ার পাওয়া গেছে। সেগুলোর সঙ্গেও, দেখা যাচ্ছে, বার্মা এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের সমাজ সংস্কৃতির যথেষ্ট মিল। এসব কিছু প্রমাণ করে আদিম বসতি ওই অঞ্চল হতেই বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়েছিল।’
ইন্ডিকা ধানের প্রসঙ্গ তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘এ ধান বাংলাদেশ অংশে ঢুকেছিল পশ্চিম দিক থেকে। তার মানে, ইন্দো ইউরোপিয়ানদের সংশ্লিষ্টতা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।’ অবশ্য এ বিষয়গুলো নিশ্চিত হতে আরও গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন মিজান।
তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশ অঞ্চলে প্রথম যখন বসতি স্থাপন করা হয় তখন থেকেই মানুষ ধান চাষের ওপর নির্ভরশীল ছিল কি না তা একটি বড় প্রশ্ন। এ প্রশ্ন সামনে রেখেও গবেষণা হচ্ছে। আবার প্রত্নস্থানে উৎখননে বিভিন্ন সময় ভবনের ধ্বংসাবশেষ, ভাঙা পাত্র, ঘটি বাটি ইত্যাদিও পাওয়া যাচ্ছে। প্রাচীন এসব নিদর্শন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি, এসব তৈরির টেকনিক রপ্ত করার আগেও মানুষের অস্তিত্ব ছিল। কারা ছিল তারা?’ এমন আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে প্রত্নশস্য গবেষণার প্রয়োজন আছে বলে মত দেন তিনি। তার মতে, গবেষণা সফল হলে সত্যি সত্যি জানা যাবে বাংলাদেশে কারা কখন প্রথম বসতি স্থাপন করেছিল। তাদের আদি পরচয় কী? এখন যারা বসবাস করছে তারা আসলে কারা? বাঙালির ইতিহাসইবা কত পুরনো?
মিজানের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কথা হয় বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ শরীফ উদ্দিন আহমেদের সঙ্গে। জনকণ্ঠকে তিনি বলেন, ‘আমাদের ফল ফসল কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে কীভাবে হারিয়ে গেছে অনেক ফসল প্রত্নউদ্ভিদ গবেষণার মাধ্যমে হয়ত সে সম্পর্কে জানা যাবে।’ তবে এ জন্য আরও অপেক্ষা করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।
অন্য প্রসঙ্গ তুলে ধরে কৃষি বিজ্ঞানী জীবন কৃষ্ণ বিশ্বাস বলেন, ‘বাংলাদেশের কৃষকও অনেক বড় গবেষক। অনেক বড় বিজ্ঞানী। তাদের কাছেও অনেক তথ্য থাকে। গবেষকদের গবেষণার সঙ্গে তাদের চেনা জানা তথ্য-উপাত্তের সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাহলেই মূলত কাজে আসবে গবেষণা।’
এদিকে, প্রত্নশস্য নিয়ে গবেষণা দেশে নতুন হওয়ায় অনেকেই এ সম্পর্কে এখনো অবগত নন। এর সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতেও ছাড়ছেন না কেউ কেউ। কারও কারও মতে, আগুনে পুড়ে অঙ্গার শস্যদানায় কোনো বায়োলজিক্যাল উপাদান থাকে না। এ ধরনের উপাদান নিয়ে গবেষণায় সীমাবদ্ধতা থেকে যেতে পারে। তবে সব ধরনের মূল্যায়নকে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে চান গবেষক মিজানুর রহমান। জবাবে তিনি বলেন, ‘আমার গবেষণার কোথাও ত্রুটি থাকলে, যে কেউ ধরিয়ে দিতে পারেন। আমি তাকে স্বাগত জানাব। কারণ সিরিয়াস সব গবেষণাই এভাবে নানা ক্রিটিকের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। সফল পরিণতির এটাও এক শর্ত।’
একই প্রসঙ্গে সুফি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘অতীত কৃষি বা মানুষ সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা আগেও জানতাম। বা অনুমান করতে পারছিলাম। কিন্তু মিজানুর রহমানের গবেষণা তথ্যগুলোর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দিচ্ছে। এটা অনেক বড় ব্যাপার।’ অক্সফোর্ডের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেণাটি এখন চলছে জানিয়ে তিনি বলেন, গবেষণার কদর করতে হবে।’ অন্যথায় গল্পগাথার মধ্যেই বাঙালির ইতিহাস আটকে থাকবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।