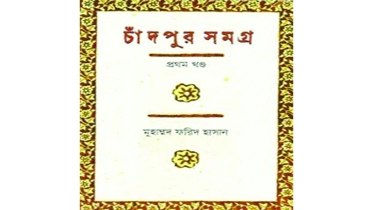শওকত ওসমানের জন্ম ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ২ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার সবলসিংহপুর গ্রামের মেহেদি মহল্লায়। সে হিসেবে ২০১৭’র ২ জানুয়ারি, তাঁর জন্মশতবর্ষ। তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা এবং এক ধরনের পরিণতি ঘটে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায়। যখন তিনি ভারত ও বঙ্গ বিভাগের মধ্যদিয়ে পাকিস্তানের পূর্বাংশ তথা পূর্ববঙ্গে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন তা ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিচিত্র রূপকেই প্রকাশ করে। এ সময় তাঁর বয়স তিরিশ। কর্মজীবন শুরু করেছেন, লেখক ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। ‘বনী আদম’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ‘জননী’ লেখার প্রস্তুতি চলেছে এবং তার পটভূমি পশ্চিমবঙ্গ।
কিন্তু তারপরেও এটা বিশেষভাবে উল্লেখ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ যেÑ তিনি নিজেই বলেছেন, ‘দেশবিভাগের পর শুধু পূর্ববঙ্গ নিয়ে কারবার আমার। পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ পর্যন্ত।’ এই বিশেষ দায়িত্বই তিনি পালন করতে চেয়েছেন, তবে এক্ষেত্রে তিনি যেমন বলেন, ‘১৯৩৮-এর পটভূমি থেকেই উপন্যাস আরম্ভ করে ধীরে ধীরে এগোতে হবে’ তাতে বোঝা যায়, এই উপমহাদেশের বৃহত্তর পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁর বিকাশ ও বিস্তৃতি।
এই তথ্যগুলো আমরা পাই তাঁর গ্রন্থ ‘উত্তরপর্ব : মুজিবনগর’ থেকে। বঙ্গবন্ধুর হত্যাকা-ের পরবর্তী সময়ে কয়েক বছরের জন্য তিনি পশ্চিমবঙ্গে চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা যে তাঁর বসবাস, চিত্তন, সৃজন ও মননভূমি ছিল না তা বোঝা যায় সে সময়ে, লেখা তাঁর দিনপঞ্জি থেকে। উনিশশ’ সাতাত্তরের ৫ ফেব্রুয়ারির দিনপঞ্জিতে তিনি নিজেকেই প্রশ্ন করেন ‘মনে হয় না নির্বাসনে আছি?’ তখন তাঁর অস্থিরতা বেশ ভালই বোঝা যায়। ছিয়াত্তরের নবেম্বরে দুবার লিখেছেন, ‘আমি বিদেশী’। ‘ইতিহাসের চোখে আমি বিদেশী।’ ঐ বছরেরই ফেব্রুয়ারির একদিন তখন জানান ‘গত পাঁচ মাস এক লাইনও লিখতে পারিনি’ তখন সঙ্কটটা বেশ বোঝা যায়। শেক্সপিয়ারের মতো ‘কাব্য-ঔষধ’ও তখন তাঁকে সুস্থির করতে পারেনি। তাঁর তখনকার বাস্তবতা এই উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়েছে, ‘কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তো আমার মানস-জন্মভূমি। আমি সেখান থেকে বঞ্চিত যেমন তেমনি রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশ থেকে নির্বাসিত?’
একটি বিশেষ প্রসঙ্গ থেকে বিষয়টিকে অধিকতর স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। ‘কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা’র ‘শেষ কয়েকটি কথা’য় মুজফফর আহমেদ বলেছেন, কবিকে বুঝতে হলে ‘শুধু নজরুলের রচনা পড়লেই চলবে না, আমার মতে, নজরুলকে অধ্যয়ন করাও আবশ্যক।’ এ কথা শওকত ওসমান সম্পর্কেও কমবেশি প্রযোজ্য। তাঁর বস্তু ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কেই শুধু নয়, তিনি মানুষকে যেভাবে দেখেছেন তা থেকেও বিষয়টিকে বুঝতে হবে।
দুটি উদাহরণ দেয়া যাক। প্রথম উদাহরণ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের। ১৯৭১-এ তাঁকে কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট নিয়ে যাওয়া-পরবর্তী প্রসঙ্গে শওকত ওসমান লিখেছেন, ‘তবে অপরাধ তিনি করেছিলেন বৈকি। তাঁর অপরাধ : কৈশোর কাল থেকে দেশবাসীর সুখে-দুঃখে একাত্ম শরিক হওয়ার ব্রত গ্রহণ শপথবদ্ধ অঙ্গীকারে।’ ‘কাল : এপ্রিল, ১৯৭১।’ মুক্তিযুদ্ধের শহীদ সম্পর্কে শওকত ওসমান লিখেছেন, ‘বর্তমান প্রজন্মের কাছে এই নাম তেমন পরিচিত নয়।’ নতুন প্রজন্মের ভাই-বোনদের আহ্বান জানিয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮। যে পারে ভুলুক, আমি কোনদিন এই তারিখ ভুলব না। সেদিন পূর্ব পাকিস্তানের কোন মুসলমান সদস্য নয়, বিধর্মীরূপে উপহাসিত এই মাটিরই সন্তান বাংলা ভাষার দাবি উত্থাপন করেন। মানুষের পরিচয় তার মনুষ্যত্ব।’
(মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি/শহীদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মারকগ্রন্থ)।
আর দ্বিতীয় উদাহরণ অজিত কুমার গুহের। ‘মদীর অগ্রজ’ স্মৃতিচারণে শওকত ওসমান শিল্পী কামরুল হাসানের বরাত দিয়ে ১৯৫২ সালের ঘটনার কথা লিখেছেন। শিল্পীর সঙ্গে গোয়েন্দার কথোপকথন :
Ñআপনার নাম তো কামরুল হাসান।
Ñজী।
Ñকিন্তু প্রফেসর গুহ তো হিন্দু।
Ñনিশ্চয়।
Ñআপনি মুসলমান?
Ñনিশ্চয়।
Ñআপনি মুসলমান। হিন্দু কী করে আপনার দাদা হয়?
Ñহয়। সকলে তা বুঝতে পারে না।
(অজিত গুহ স্মারকগ্রন্থ। উভয় স্মারকগ্রন্থের সম্পাদক আনিসুজ্জামান)।
যিনি এ কথা নিজে বুঝবেন ও অন্যকে বোঝাতে চাইতেন এবং মনুষ্যত্বের ওপর প্রধান জোর দিতেন তিনিই শওকত ওসমান।
এই লেখক ও কথাসাহিত্যিক নিজেকের গ্রামের আরেকটি নাম উল্লেখ করেছেন, ‘হুড়কো।’ বলেছেন, গ্রামের সীমানা নিয়ে বিরোধ বাধলে তার গ্রামের লোক হুড়োহুড়ি করে গিয়ে সেই সীমানা রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের ছিল ‘হামা’ তথা বন্যাপ্রবণ এলাকা। বৈরী, অন্যায় ও বিরুদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে গিয়ে লড়ার যে উত্তরাধিকার পূর্বজদের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন তাই হয়ে উঠেছিল তার জীবন ও সাহিত্যের অন্বিষ্ট ও বৈশিষ্ট্য। ছাত্রজীবনের দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা বোঝা যায়; ‘ধর্মতলা স্ট্রিট থেকে লেয়ার সার্কুলার রোড ধরে মল্লিকবাজার। তারপর ডাইনে পার্ক স্ট্রিট ধরে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ। পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগত, তিন মাইলের মতো রাস্তা অনুমানে। সকালে নাস্তা করে বেরিয়ে পড়তাম সকালের টিউশনি ধরতে। বিকেলে কলেজ শেষে সন্ধ্যার টিউশনি। ক্লান্ত লাগলেও পরিস্থিতি আরাম-আয়েশের কোন সুযোগ দিত না।’ উত্তরকালে কর্মজীবনে বাংলা একাডেমিকে সাক্ষী রেখে চলেছেন, এখানে তিনি প্রচুর অনুবাদ করেছেন। শুধু সাহিত্য নয়, অন্যান্য বিষয়েও। ‘হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিÑ তাঁতশিল্পের রিপোর্ট নিশ্চয়ই সাহিত্য নয়, কিন্তু উপার্জনের উৎস তো বটে।’
ফলে জীবনকে তিনি দেখেছেন একদম কংক্রিট টার্মসে। স্নাতক হওয়ার সাংস্কৃতিক তাৎপর্যের আগে তার মনে পড়েছে এর অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলায় এমএ করলেও শওকত ওসমান অর্থনীতিতে অনার্স করেছিলেন। তখনকার লেখার, ডিভিশন ক্লার্কের মাসিক ৪৫ টাকা বেতনের অন্তত পনেরো টাকা সঞ্চয় হওয়ার কথা এবং দুই মাসের সঞ্চয় থেকে দেড় বিঘা জমি কেনা সম্ভব ছিল। কবিতা লেখার সম্মানী বাবদ পাঁচ টাকা পেলে তাঁর মনে হয়, এ দিয়ে দুই মন মোটা চাল কেনা যায়।
এভাবে তিনি গদ্য লেখার অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেন। ‘অতীত দিনের স্মৃতি’তে আবুল কালাম শামসুদ্দীন লিখেছেন, ‘আমরা সেদিন একদিনের জন্য হুগলি পান্ডুয়া ভ্রমণে গিয়েছিলাম। বাহার মিয়া, আয়নুল হক খাঁ, নাগির আলী, মুজিবুর রহমান খাঁ, মঈনুদ্দীন প্রমুখ সাহিত্যিক বন্ধুরা মিলে আমরা প্রায় জনাদশেক ছিলাম সে দলে, তরুণ সাহিত্যিক শওকত ওসমান আমাদের সহযাত্রী হন। হুগলি ও পান্ডুয়ার দ্রষ্টব্যগুলো দেখে সে-রাতেই আমরা আবার কলকাতায় ফিরে আসি। দিনদশেক পরেই শওকত ওসমান তার ভ্রমণ বিবরণ লিখে ‘মাসিক মোহাম্মদী’ অফিসে আসেন। তার লেখাটি পড়ে একেবারে বিস্মিত-চমৎকৃত হয়ে গেলাম। লেখাটির ভাষাই শুধু সুন্দর ছিল না, দ্রষ্টব্য বিষয়গুলোর বিচরণ ছিল এতই সজীব এবং তাঁর তীক্ষè পর্যবেক্ষণ এতই পরিস্ফুট ছিল যে তাঁর বর্ণনায় মুগ্ধ হয়ে বলে ফেললাম, আপনি গল্প লেখেন না কেন? আপনি তো জাত গল্প-লেখক।’ এরপর তিনি তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে এক্ষেত্রে তাঁর অধিকারের বিষয়টি বোঝা যায়, ‘আমরাও তো এই ভ্রমণে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এমন বহু জিনিস আপনি দেখতে পেয়েছেন। এমন পর্যবেক্ষণ শক্তি যার, গল্প লেখায় তাঁরই তো অধিকার।’
কিন্তু জীবন তাঁর কাছে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবেও ধরা দিয়েছিল। ষোল বছরের ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী পুত্র রেলগাড়ির নিচে বীভৎস মৃত্যুবরণ করে। রাত সাড়ে তিনটা উন্মাদপ্রায় পিতা-সন্তানের গলাকাটা লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি ‘প্রস্তরফলক’ গল্পগ্রন্থ উৎসর্গ করতে গিয়ে লেখক লিখেছেনÑ
‘তোমায় বাবা বলে আর ডাকিব না
আমায় দিতেছ কত যন্ত্রণা।’
এতকিছুর পরে এবং তা সত্ত্বেও শওকত ওসমান ছিলেন জীবনবাদী লেখক। শামসুর রাহমানের কবিতার ভাষায়Ñ
আপনার জীবন এক অবিরাম সংগ্রাম বাঁচবার
ক্লান্তি আর হতাশা যাদের কুঁজো করে ফেলেছে তাদের
বাঁচিয়ে তুলবার।
সে কারণে
এদেশের প্রতিটি বিবেকী মানুষ আপনার
রচনাসমূহের পক্ষে, হে প্রেরণাসঞ্চারী অগ্রজ,
এদেশের প্রতিটি সাহসী, অগ্রসর মানুষ
আপনার সুদীর্ঘ জীবনের পক্ষে
(শওকত ওসমানের জন্য = উজাড় বাগানে)
পশ্চিমবঙ্গে জন্মগ্রহণ করে সেখানে তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব কাটালেও তাই তিনি আমাদের লেখক। ১৯৭৬-এর ২৫ জুলাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে সে কারণে তিনি লিখেছেনÑ ‘কোথাও মন বসছে না।’ দুই মহানগর ঢাকা ও কলকাতা বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সকলেও তাই তিনি উত্তর প্রজন্মের লেখকদের আহ্বান জানিয়েছেন, ‘আগামীকালের লেখক বন্ধুগণ, তোমরা দুই মহানগরীর উপাখ্যান লিখিও।’
ফলে ঐ পর্বেই তিনি বাংলাদেশের খুঁটিনাটি খবর রেখেছেন। তাঁর দিনপঞ্জিতে যেমন উনিশশ’ একাত্তরের ২৪ সেপ্টেম্বরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর শিক্ষক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সাতাত্তরের ২১ মে পরলোকগমনের সংবাদ পাওয়া যায় তেমনি ছিয়াত্তরের ১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকায় যে আবদুল গণি হাজারী মারা গেছেন সে সংবাদও তাঁর দিনপঞ্জিতে উল্লেখ করতে ভোলেননি।
একাত্তরেও বাংলাদেশ ছিল তাঁর মর্মমূলে একটি ‘অসাহিত্যিক’ ও আরেকটি ‘সাহিত্যিক’ উদাহরণ থেকে তাঁর সামগ্রিক মনোযোগের বিষয়টি বোঝা যাবে। ১৯৭১-এর ৯ অক্টোবরের দিনপঞ্জিতে শওকত ওসমান লিখেছেন, ‘চাঁদপুরের ছেলে অরুণ কুমার নন্দী গতকাল থেকে কলকাতার কলেজ স্কয়ার ট্যাঙ্কে সাঁতার কাটছে। বিশ্বরেকর্ড করার প্রত্যাশা বেজায় ভিড় জমে যায় চারদিকের পাড়ে। অনেকে উৎসাহ জোগাচ্ছে ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি দিয়ে। দেখা যাক কী হয়।’ আর ১২ অক্টোবর এর পরিণতি সম্পর্কে লিখেছেন, ‘জয় বাংলা। সাঁতারু অরুণকুমার নন্দী বিশ্বরেকর্ড করে বসে আছে। কাছে গিয়ে এই বীরকে অভিনন্দন জানাতে হয়। তাঁর কৃতিত্ব স্বাধীনতা সংগ্রামে এক অমূল্য অবদান। একটানা লাগাতার সাঁতারে বিশ্বরেকর্ড ছিল ৮৯ ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট। অরুণ নন্দী ৯০ ঘণ্টা ৫ মিনিট সাঁতরে এই রেকর্ড চুরমার করে দিয়েছে। আর এক ব্রজেন দাসকে পাওয়া গেল। বাংলাদেশের অধিবাসীর টাক লাগানো এই ম্যাজিক বিশ্ববাসীকে দুর্দিনে আরও আমাদের কাছে টেনে আনবে। জয় বাংলা।’ এর আগে ১৯৭১-এর ১০ অক্টোবর শওকত ওসমানের বন্ধু ও দেশের বিশিষ্ট লেখক ও কথাসাহিত্যিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন, যদিও শওকত ওসমান তখনও তা জানতেন না। জানার পর ১৩ অক্টোবরের দিনপঞ্জিতে তিনি লিখেছেন, ‘না না না...তা হতে পারে না।’ প্রবাসে থেকেই ওয়ালীউল্লাহ তখন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও সক্রিয় সহযোগিতা করছিলেন। তাঁর এই ভূমিকার জন্য পাকিস্তানের প্ররোচনায় তিনি ইউনেস্কোর চাকরি করান। ২০ অক্টোবর কলকাতার তাদের আবার সার্কুলার রোডের বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির দফতরে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে শওকত ওসমান ওয়ালীউল্লাহর ওপর প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধ পরে ‘দেশ’-এ ছাপা ছয়।
ফলে বাংলাদেশের বাইরে, কলকাতা থেকেও শওকত ওসমান বাংলাদেশকে অনুভবই শুধু করেননি। যেন সেখানে সশরীরে বসবাস করছিলেন। ৮ ডিসেম্বরের দিনপঞ্জিতে তা অধিকতর প্রাঞ্জল হয় :
‘বিবিসির খবর, কুমিল্লা বিমানবন্দর মুক্তিবাহিনীর দখলে। পূর্ব রণাঙ্গনে সর্বত্র জয়রস ঘর্ঘর-রবে গড়িয়ে চলেছে।’ ‘বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি, বুঝে নিক্্ দুর্বৃত্ত!’
॥ দুই ॥
শওকত ওসমান নিজেকে বলেছেন ‘ঝাড়ুদার গ্রন্থকার।’ লেখালেখির জন্য তিনি পথ পরিষ্কার ও প্রস্তুত করছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর মতো লেখকদের কথা মনে রেখে এ কথা বললেও স্বয়ং ওয়ালীউল্লাহ স্ত্রী এ্যানমারিকে তাঁর সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছেন, ‘ও যধাব শহড়হি যরস ভড়ৎ ুবংি রহ পধষপঁঃঃধ...ঐব রং ষরশব ধ পযরষফ, ুবঃ বীঃুবৎহবষু বিষষ ৎবধফ, ারবংি াবৎু পষবধৎ. ও যধাব হড়ঃ ংববহ ধহুড়হব ষরশব যরস. ঐব রং ংড় মড়ড়ফ, ধনংড়ষঁঃবষু রিঃযড়ঁঃ ধহু সধঃপব, ধহু ঔবধষড়ঁংু, মৎববফ. ঐব রং ঃযব ড়হষু ৎিরঃবৎ যিড় ঢ়ৎরংবং ধহুনড়ফু ধসড়হম যরং পড়হঃবসঢ়ড়ৎধৎরবং.’
(জীবনবৃত্তান্ত : সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর জীবন ও সাহিত্য/সৈয়দ আবুল মকসুদ)। সে কারণে নিজের লেখা বাদ দিয়ে তিনি বিস্মৃতপ্রায় লেখক ফজলুল হকের তিনটি গল্প খুঁজে বের করে সেগুলো গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। শামসুর রাহমানের ভাষায় যিনি ‘সর্বক্ষণ লেখার চিন্তায় বিভোর ছিলেন’ তিনি এ রকম কাজেও সময়কে ব্যয় করেছেন।
সকলেই জানেন, শওকত ওসমান ইহলৌকিক চিন্তা ও চেতনার অগ্রসর লেখক ছিলেন। ধর্ম ও রাষ্ট্র যে এক নয় এবং হতে পারে নাÑ সেটা তিনি তাঁর সৃজন ও মননশীল লেখায় বহুবার বলেছেন। ১৯৪৭-এ মুসলিম লীগারদের হাতে মার খেয়েছেন। বিয়াল্লিসে কলকাতার ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রিটে ফ্যাসিবাদবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। এ বছরই চট্টগ্রামে ছাত্র ফেডারেশনের সম্মেলনে মুনীর চৌধুরীর সঙ্গে শওকত ওসমানের যোগাযোগ ঘটে।
কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ করে পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসতে হয়। গোলাম কুদ্দুস ছাড়া তাঁর সাহিত্যিক সতীর্থ প্রায় সকলেই পাকিস্তান চলে আসেন অথবা তার সিদ্ধান্ত নেন। ‘আবু রুশদ, আবুল হোসেন, আহসান হাবীব নেই, এমন দুনিয়ায় বাস করা কঠিন।’ অমুসলমান সম্পাদিত পত্রিকায় তাঁর লেখা ছাপা হলেও বেশিরভাগ লেখাই বেরুত মুসলিম সম্পাদিত ‘আজাদ’, ‘মোহাম্মদী’ ও ‘সওগাত’-এ। শওকত ওসমান ভেবে দেখেন, এদের সবাই মুসলিম-লীগার ছিলেন না।
বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং বাংলা ভাষার প্রতি অবিচল আস্থা থাকা সত্ত্বেও শওকত ওসমান মানবতাকে প্রথম গুরুত্ব দেন। পাকিস্তানোত্তরকালে তিনি যে বিহারী সম্প্রদায়কে নিয়ে ‘গেঁহু’র মতো গল্প লেখেন তাতেই বিষয়টি বোঝা যায়। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ভাষায়, ‘ঘোরতর সমকাল সচেতন’ লেখক বলেই যে তিনি এ গল্পটি লেখেন তা নয়। ইলিয়াস যে বলেছেন ‘বাংলাদেশের বিহারী সম্প্রদায়ের সীমাহীন দুর্দশার কথা মনে হলে আমার চোখে কিন্তু জেনেভা ক্যাম্পের ছবি ভাসে না। বরং যখনি জেনেভা ক্যাম্পের ওদিকটায় যাই, গোটা এলাকার ওপর ক্রেন ছাড়াই আকাশ থেকে ঝুলতে থাকে একটা মালগাড়ির অন্ধকার ওয়াগন’ তা শওকত ওসমান ও তাঁর মনুষ্যহৃদয়টিকে শনাক্ত করে। ইলিয়াসের মন্তব্য লেখকের চেতনাকেও স্পষ্ট করে, ‘এক প্রজন্মে দুইবার বাস্তুচ্যুত এই সম্প্রদায়কে নিয়ে আরও গল্প এখানে লেখা হয়েছে। কিন্তু নিজের মাটি থেকে ওপড়ানো মানুষের শেকড়টি ‘গেঁহু’ গল্পে যেমন প্রকট, অন্য কোথাও তার ছায়াও দেখেছি বলে মনে পড়ে না।’ ইলিয়াস যে আরও বলেছেন, ‘বয়স তাঁকে ভোঁতা করে না, বরং বযসের সঙ্গে তাঁর অনুভূতি আরও ধারাল। আরও তীক্ষè হয়ে উঠেছে (শওকত ওসমানের প্রভাব ও প্রস্তুতি/ নিসর্গ, শওকত ওসমান সংখ্যা : সম্পাদক : সরকার আশরাফ, বগুড়া তা তাঁর কথিত মৃত্যুপূর্ব উচ্চারণ ‘একাশি, নট আউট’-এর তাৎপর্যকে তুলে ধরে। সাতাত্তর বছর বয়সে নিজের সম্পর্কে তিনি যথার্থই বলেছেন :
বন্ধুগণ, আমার বয়স মাত্তর
এখন প্রায় নয়, ছুঁই হোলো সাতাত্তর।
ঈর্ষার নিশ্চিত জ্বলছে, দ্যাখো পুড়ছে
মানবতার দুশমনদের গাত্তর।
ওরা বলে, “ হালা মরেনা ক্যান,
মইরব কবে?
ও অক্ষয় যেন, পাহাড়ের পাত্তর।”
বন্ধুগণ, স্বচ্ছন্দে ওদের জানিয়ে দাও,
কেতাব না, জীবন-পাঠশালার ছাত্তর;
ওদের ধর্ম-ব্যবসা, ভ-ামি ছুটাতে
আমি এ্যাসিড খুব বড় এক পাত্তর
............
বয়স শুরু এই মোটে সাতাত্তর
॥ তিন ॥
শওকত ওসমানের নানা অঙ্গিকে লেখা সমগ্র সাহিত্যকর্মকে একটা ঐক্যবদ্ধ দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে। প্রবন্ধের কথা কথাসাহিত্যে, কথাসাহিত্যের প্রসঙ্গ প্রবন্ধে, নাটকের বিষয় ছোটগল্পে এভাবে নানা মাত্রা তাঁর মনন, চিন্তা, ভাবনা, এমনকি ভালোবাসাকেও বিন্যস্ত করেছে। কিশোরদের জন্য লেখা তাঁর সাহিত্য ‘প্রাইজ’ ‘আব্বাস’ প্রথবা ‘ক্ষুদে সোশ্যালিস্ট’ কি তাঁর মূল সাহিত্যেরই অংশ নয়? তাঁর প্রবন্ধের বইয়ের নাম যখন হয় ‘সমুদ্রনদী সমর্পিত’ তখন কি তা অঙ্গিকের সীমাবদ্ধতাকেই অতিক্রম করে না?
একটি উদাহরণ থেকে তাঁর সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য অথবা স্বদর্থক অহংকারের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর উপন্যাস ‘জননী’র ইংরেজি নামের জন্য কোনো পরিভাষা পছন্দ না হওয়ায় তিনি বললেন, ‘ঔধহধহর’ ই ‘জননী’র ইংরেজি। ওদের ভাষা এত শিখেছি, ওরা কেন আমাদের একটি শব্দ ভালো করে শিখবে না? মাদার নয়, মম, নয়, মামী নয়, জননী। কবিকে তিনি বলেন, ‘শোনো শামসুর রাহমান, আমি পাশ্চাত্যকে অন্তত একটি বাংলা শব্দ উপহার দিয়েছি।’ আর এর কাছাকাছি সময়ে একদিন যখন মতিঝিলের মধ্য দিয়ে হাঁটছি, তখন তিনি আমাকে বলেন,‘কেমন প্রতিশোধ নিলাম!’
শওকত ওসমান সারাজীবন ধরে তাঁর লেখার যে পুনর্লিখন ও পরিমার্জন করেছেন তা থেকে বোঝা যায়, লেখক ক্রমাগত নিজেকে অতিক্রম করতে চেয়েছেন। ১৯৪৩-এ তাঁর উপন্যাস ‘বনী আদম’ তিনি পুনর্লিখন করেন ১৯৯০-এ। ‘জন্ম-জন্মান্তর’ নাটকের লেখা শুরু ১৯৪৮-এ, শেষ ’৪৯-র মার্চে। সাহিত্যপত্রে প্রকাশ পায় মধ্যষাটে এবং গ্রন্থাকারে ১৯৮৬তে। তাঁর ‘নন-ফিকশন’ রাইটিং-এর মধ্যে ‘মুসলিম মানসের রূপান্তর’-এর খসড়া তিনি করেছিলেন ১৯৪০-এ। তাকে গ্রন্থের রূপ দিতে নেন চার দশকেরও বেশি সময়।
শওকত ওসমানের রচনা বা তাঁর কথা সাহিত্য বাংলাদেশকে শনাক্ত করতে সাহায্য করে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন তিনি চট্টগ্রামে। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সংকলনে তিনি যে গল্প ‘মৌন নয়’ লেখেন তা-ই পরবর্তীকালে ‘আর্তনাদ’ উপন্যাসে রূপ পায়। এই উপন্যাসে পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যে দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটে এতে তার ঘনীভূত প্রকাশ দেখি। ‘ক্রীতদাসের হাসি’ তিনি লেখেন ১৯৬২-তে। এটি ঐ সালেই আদমজী পুরস্কার পান এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান লেখকের হাতে তা তুলে দেন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, এটি তাঁর স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধেই লেখা। তাঁর তথাকথিত উন্নয়ন এবং এদেশের জনগণের ‘প্রতিভার উপযুক্ত’ ‘মৌলিক গণতন্ত্র’- কিছুই তাঁকে রক্ষা করতে পারে না। ‘উন্নয়ন দশকে’র খাদেই তিনি শেষ পর্যন্ত পতিত হন। তার উত্থানেই স্বৈরশাসনের পতনের শব্দ শুনেছিলেন লেখক। উপন্যাসে তিনি আগেই বার্তা দিয়েছেন। হাসি মানুষের প্রাণের সম্পদ-কোনো লোভ অথবা প্রলোভন দিয়ে তাকে জেতা যায় না। বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশীদের জাংসী বিদ্রোহের পতনের শক্ত আমরা পাকিস্তানী স্বৈরশাসনে তার প্রকৃত ও প্রাসঙ্গিক প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে শুনি। সকল স্বৈরশাসকই মানুষের হাসিকে দখল অথবা ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়।
‘চৈৗরসন্ধি’র নাম একটু কম উচ্চারিত হলেও এই উপন্যাস ছিল পশ্চিমের বড় ও পূর্বের ছোট চোরের কাহিনী। উপন্যাসের শেষে দেখা যায় ছোট ভাই বড় ভাইকে বলছে,‘বড় ভাই থাকতে ছোট ভাই মুখ খোলে না, পূর্বদিক আমাদের আর পশ্চিম আপনাদের। আইয়ুব ও ইয়াহিয়া কেবিনেটের সদস্য রাঙালি জি ডব্লিউ চৌধুরী ‘দ্য লাস্ট ডেইজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান’- এর একটি হাস্যকর উদাহরণ দিয়েছেন। পূর্ব বাংলা ও তার নেতা শেখ মুজিব যখন প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন দাবি করছিলেন তখন জি ডব্লিউ চৌধুরীর কাছে আইয়ুব খান জানতে চেয়েছিলেন, ‘ঞবষষ সব যিধঃ বিৎব ঃযবু ধংশরহম ঃড়ৎ? উরফ হড়ঃ সু চৎড়ারহপরধষ এড়াবৎহড়ৎ গড়হবস বহলড়ু ধষষ ঃযব চড়বিৎং ভড়ৎ ৎঁহহরহম ঃযব চৎড়ারহপরধষ এড়াবৎহসবহঃ রহ ঊধংঃ চধশরংঃধহ? যিধঃ সড়ৎব পড়ঁষফ ও মৎধহঃ?’ পাকিস্তানপন্থী ও তার সমর্থক হয়েও চৌধুরী এর হাস্যকর দিকটিকে এভাবে তুলে ধরেছেন, অভঃবৎ সধহু ুবধৎং ড়ভ বীঢ়বৎরবহপব, অুঁনব বয়ঁধঃবফ ঃযব ফবষবমধঃবফ ঢ়ড়বিৎং ড়ভ যরং হড়সরঃবফ ধহফ ঁহঢ়ড়ঢ়ঁষধৎ মড়াবৎহড়ৎ রিঃয ঃযব ষবমরঃরসধঃব ফবসধহফং ড়ভ ঃযব ংবাবহঃু ভরাব সরষষরড়হ ঢ়বড়ঢ়ষব ড়ভ যরং পড়ঁহঃৎু!’
এভাবে উপন্যাসে পশ্চিমে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান আইয়ুব আর পূর্বে তার গোলাম মোনায়েম, ফলে চোরেরা যা বলে তাকে ভিন্নার্থে লেখকের কৌশলের প্রতি সাধুবাদ জানিয়ে আমারাও বলতে পারি, সোবহান আল্লা, সোবহান আল্লা। ১৯৬৮তে তিনি লেখেন ‘সমাগম’। এখানে বহু বিচিত্র চরিত্রের সমাবেশ ঘটে, তর্ক লাগে নানা মূল্যবোধের মধ্যে। লেখকের সঙ্গে পাঠকেরও নানা উপলব্ধি ঘটে। উপন্যাসের শেষে মানুষের বিশ্বভ্রাতৃত্বের জয় ঘোষণা করা হয়।
মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শওকত ওসমান বেশ কয়েকটি উপন্যাস লেখেন। ‘নেকড়ে অরণ্য’ সম্ভ্রমহারা নারীদের আত্মকথা ‘দুই সৈনিক’ মুসলিম লীগের ভ্রান্ত রাজনীতির প্রকাশ। মুসলিম লীগপন্থী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মখদুম মৃধা আগ বাড়িয়ে পাকিস্তানী দুই সেনা অফিসারকে সাদর আমন্ত্রণ ও আপ্যায়ন করে। পরে তাদের লালসার শিকার হয় তার নিজেরই দুই কন্যা। মকদুমের মা উচ্চরণ করেন প্রকৃত সত্য, ‘কথা কস না ক্যান... পাকিস্তান বানাইছিলি না? তখন হিন্দু মাইয়াদের উপর জুলুম অইলে কইতি না, অমন দুএকডা হয়। অহন দ্যাখ আল্লার ইনসাফ আছে কিনা’ মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস ‘রাজস্বাক্ষী।’ কিন্তু দ্রুত ও অনুরুদ্ধ হয়ে লেখা হলেও ‘জাহান্নাম হইতে বিদায়’-এ মুক্তিযুদ্ধের একটি আন্তরিক ও যথার্থ পরিচয় রয়েছে। অস্থির সময়ের মধ্যেও গাজী রহমান, বত্রিশ বছর তাতে কাটানো বিদ্যালয়-শিক্ষক স্থিতধী বুদ্ধির পরিচয় দেন। ‘তবে অপমৃত্যুর যেখানে ভয়, সেখানে হুঁশিয়ার হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। খামোখা মরে লাভ নেই। মাঝে মাঝে অতিসচেতন মুহূর্তে গাজী রহমান তা উপলব্ধি করেছে বৈকি। কিন্তু পরিত্রাণের আশায় হলেও হন্যে হওয়া এক ধরনের কাপুরুষতা। কোটি কোটি নর-নারী, শিশু-কিশোর বৃদ্ধ আছে না বাংলাদেশে? সকলে যদি নিরাপত্তার খোঁজে বিবাগী হয়, জালেমের মুখোমুখি কে রুখে উঠবে? অবশ্যি সংসারে আবার সকলে যোদ্ধা নয়। তা হওয়াও উচিত নয়। লাঙল ছেড়ে দিলে বিনা আহারে কী দিয়ে গেরিলারা লড়বে? নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়ে তার আরও উপলব্ধি হয়, ‘যুদ্ধ তো শুধু যোদ্ধার কাজ নয়। কেন লড়ছি, কিসের জন্য লড়ছি, তার সঠিক হদিস যদি জানা থাকে, তাগদ বেড়ে যায়।’ গাজী রহমানের মতো সকলের মনে এই প্রশ্ন, কবে তারা এই নরক থেকে মুক্তি পাবে? ‘মুক্তি পাবে বাংলাদেশ?’ অবরুদ্ধ স্বদেশ যে কারণে জাহান্নাম গাজী রহমানের কাছে তার ব্যাখ্যা এরকম- ‘আমার অর্ধভুক্ত দেশবাসী তোমাদের হাতে অস্ত্র সাজিয়ে দিয়েছিল দেশরক্ষার জন্য। আজ কৃতঘেœর মতো তাদের ধ্বংস করছ ছলনার পাশা খেলে। যা তোমাদের স্বার্থরক্ষী তা-ই ইসলাম, যা করাচী ইসলামাবাদকে ঝকমকে রাখবে তা-ই পাকিস্তানের সংহতি, অখ-তা...। বেঈমানের দল দূর হও অথবা ধ্বংস হও।’
সেজন্য মুক্তিযোদ্ধারা গোলামির কোনো পরিচয়, রাখতে চায় না। স্বাধীন বাংলাদেশকেই তারা তাদের পরিচয়ের ভিত্তি হিসেবে গড়ে তুলতে চায়। এ কারণে ১৯৭১-এ অসহযোগ আন্দোলন চলবার সময় দৈনিক ‘পাকিস্তান’-এ ‘স্বাধীনতার চিহ্ন’ শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে তিনি জানিয়ে দেন, কী করে স্বাধীন হতে থাকতে হয়: ‘এ্যাকেমেনীয় সম্রাটদের আমলে এক প্রাদেশিক গভর্নর (হারভারনিস) গ্রীক বন্দীদের উপদেশ দেন তার অধীনে চাকরি নিতে।
তখন গ্রীকরা জবাবে বলেছিল, জনাব, আপনি আমাদের যে পরামর্শ দিলেন তা কোন দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নয়। আপনি যা জানেন না তা নিয়ে উপদেশ দিতে পারেন না। আপনি জানেন কিভাবে গোলাম হওয়া যায়। স্বাধীনতা সম্পর্কে আপনি কিছুই জানেন না। আপনি একবার যদি তার স্বাদ পেতেন তাহলে বর্শা বল্লম নয়, দা-কুড়ুল নিয়েই আমাদের লড়তে উপদেশ দিতেন।’
॥ চার ॥
শওকত ওসমান সর্বদাই একজন অসন্তুষ্ট লেখক ছিলেন। তাই তিনি লেখার শেষ পর্ব পর্যন্ত ছিলেন নিরীক্ষাপ্রবণ। ফলে তাঁর রচনার যেমন বৈচিত্র্য এসেছে তেমনি তা হয়েছে বহুমাত্রিক। এক্ষেত্রে অন্যদের সাহায্য করতেও তিনি এগিয়ে এসেছেন। আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ’ সে সময়ের হিসেবে কম বয়সে প্রকাশিত কবিতাগুলো সব টানা গদ্যে লেখা হওয়ায় ‘কারো কারো কাছে’ ‘বেয়াদবি’ বলে মনে হয়েছিল। (প্রথম নির্জন বইগুলো/স্মৃতির নোটবুক)। প্রীতিভাজন ছাত্র বলেই নয়, তাঁর নিরীক্ষাপ্রবণ মনোভঙ্গির প্রতি সম্মান জানাতেও শওকত ওসমান ঐ ধরনের কবিতাকে সমর্থন করে সাহিত্য-সংস্কৃতিপত্র ‘সমকাল’-এ লেখেন দীর্ঘ প্রবন্ধ ‘নতুন কবিতা।’
অনুজ-আত্মজ এবং এ ধরনের বয়োকনিষ্ঠদের প্রতি সম্মান জানানো ছিল শওকত ওসমানের জীবনবৈশিষ্ট্য। ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে দেখেছি তিনি ছাত্রদের ‘আপনি’ ও ‘স্যার’ বলতেন। আরেকটি কাজ তিনি করতেন। চাকুরি-রক্ষার জন্য ক্লাসে রেজিস্টার আনলেও রোল কল করতেন না। একবার সতীর্থ-বন্ধুরা আমাকে উসকে দিয়েছিল তাঁকে এসব বিষয়ে প্রশ্ন করতে। আমিও রাজি হয়ে যাই। সেভাবে ক্লাসে একদিন দাঁড়াই, ‘কোন প্রশ্ন?’ স্যার খুব খুশি হন। কারণ, সক্রেটিসের এই উক্তি তাঁর খুব প্রিয় ছিল: অ ষরভব ঁহবীধসরহবফ রং হড়ঃ ড়িৎঃয ষরারহম. সেটা যেমন তাঁর লেখায় উদ্ধৃত হয়েছে তেমনি ক্লাসেও তিনি বহুবার বলেছেন।
প্রশ্নগুলো আমি বলে ফেলি। কেন ক্লাসে আপনি রোলকল করেন না। কেন ছাত্রদের ‘স্যার’ ও আপনি’ বলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ছাত্র- শিক্ষকের সম্পর্ক হচ্ছে বিশ্বাসের সম্পর্ক। রোল কল করে তিনি সেই বিশ্বাস ভাঙ্গতে কিংবা তাতে ফাটল ধরাতে চান না। বরং তিনি ছাত্রদের ক্লাস থেকে পালাবার ও সেই স্বাধীনতা দেবার পক্ষপাতী। সেজন্য তিনি প্রায়ই বলতেন য পলায়তি স জীবতি। যে পালায় সে বাঁচে।
কেন তিনি ছাত্রদের ‘স্যার’ ও ‘আপনি’ বলেন সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার আগে জানতে চান, আপনারা কেন আমাকে ‘স্যার’ ও আপনি’ বলেন। স্বভাবতই আমরা বলি, অপনাকে শ্রদ্ধা করি। সেই কারণে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি বললেন, আমিও একই কারণে আপনাদের ‘আপনি’ ও ‘স্যার’ বলি। আমাদের কেউ কেউ জানতে চায় আপনি কি আমাদের শ্রদ্ধা করেন? হ্যাঁ। কারণ, ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, বিদ্যার আদান-প্রদানে উভয়ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন। শুধু এক পাক্ষিক শ্রদ্ধা কোনো কাজের কাজ হতে পারে না। প্রথমে ধাক্কা লাগলেও আমরা ভেবে দেখি, তাইতো। ব্যাপারটা এক পাক্ষিক হওয়াই তো অনুচিত। তবে এর মধ্যে স্বাভাবিকতা আনার জন্য আমরা শেষ পর্যন্ত তাঁকে আমাদের ‘তুমি’ বলতে রাজী করাই। কিন্তু ‘স্যার’ বলা থেকে তিনি সরে আসেননি।
আরেকটি বিষয় তাঁর প্রত্যক্ষ ছাত্ররা জানান, তিনি পাঠ্যবই বা ঞবীঃ পড়াননি প্রচলিক অর্থে তাঁর বিষয় বাংলাও পড়াননি। চতুর্থ বিষয় ‘অতিরিক্ত বাংলা’য় আমাদের পাঠ্যসূচিতে ছিল কাজী ইমদাদুল হকের উপন্যাস ‘আবদুল্লাহ।’ এ প্রসঙ্গে একদিন শুধু তিনি আমাকে বলেছিলেন, বরিহাটি মসজিদের ইমাম জোলা বলে সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস তাঁর পছনে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অস্বীকার করেন। অথচ ইসলামে আশরাফ- আতরাফের কোনো ভেদাভেদ থাকার কথা নয়, স্যার।
পাঠ্য বিষয় কেন পড়াননি, সেটা ভাবতে গিয়ে আমার মনে হয়, ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধের সেই পর্বে কিংবা তার আগে থেকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পরিস্থিতির মোড় ঘুরছে। দেশের, অন্তত আমাদের অংশের রাজনীতি-সংস্কৃতি ও দর্শনগত পরিবর্তন দরকার। কিন্তু ঢাকা কলেজের ছাত্ররা বুদ্ধিদীপ্ত হলেও এখানে পড়তে আসে। কেরিয়ার গড়তে ও তথাকথিতভাবে বড় হতে। ফলে তিনি ন্যূনতমভাবে তাদের ধাক্কা দিতে চেয়েছিলেন। হটকারী কিছু তিনি করতে চাননি। কিন্তু টিপিক্যাল অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষার্থীদের কেবল ‘পড়িয়ে’ যাবেন তাও তাঁর কাছে সঠিক বলে মনে হয়নি। অতএব তিনি ছাত্রদের চেতনা বিকাশের একটা ন্যূনতম পথ অবলম্বন করছিলেন।
এখানে আরেকটি বিয়ষেরও উল্লেখ করা যেতে পারে। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর বিশাল শিক্ষার্থীদের বোঝাতে তিনি বলতেন ‘উত্তমকুমার থেকে শান্তনু কায়সার।’ উত্তমকুমার অর্থাৎ অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর অধ্যাপনা জীবনের প্রথম পর্ব কলকাতা সরকারি কমার্স কলেজের ছাত্র আর আমি তাঁর শেষ পর্বের ঢাকা কলেজের ছাত্র। আমাকে মনে রাখবার বিশেষ কারণ হয়তো এই, ১৯৬৬-৬৮ পর্বে অতিরিক্ত বাংলার ছাত্র হিসেবে দশ বারোজন তালিকাভুক্ত হলেও আমার বন্ধু ও সতীর্থ আতাউর রহমান বেশ কিছুদিন তাঁর ক্লাস করলেও শেষ পর্যন্ত আমরা মাত্র অধ্যাপক-শিক্ষার্থী দুজনই টিকে যাই। পড়ন্ত বিকেলে ঢাকা কলেজ যখন প্রায় নির্জন হয়ে যেত তখন তাঁর পাঠে পাঠ্যবিষয়ের চেয়ে অপাঠ্য বিষয় অর্থাৎ আসন্ন বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও তার রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কাঠামো প্রাধান্য পেত।
॥ পাঁচ ॥
শওকত ওসমান নতুন প্রজাতন্ত্রে স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে ছিলেন। পাকিস্তানী অপশাসনে আইয়ুব আমলের বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশেও এর দূষণ বিষয়ে তিনি অন্ধ ছিলেন না। ‘ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী’ গল্পে লেখক দেখিয়েছেন। মূর্খ ঐ স্বৈরশাসক কীভাবে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে বন্যার পানিতে হেঁটে হেঁটে নিজেকে জনদরদী প্রমাণ করতেও সর্বক্ষমতার অধিকারী হিসেবে দেখাতে চান। কিন্তু লেখকের কাছে কোনোকিছুই গোপন থাকে না। ‘বিবস্ত্র সত্য ও তা দেখার জন্য চোখ লাগে এবং সুস্থ চোখ, যা সুস্থ মগজ দ্বারা পরিচালিত।’
প্রত্যক্ষভাবে যাঁরা তাঁকে চিনতেন এবং যাঁরা তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে যেমন আখতারুজ্জামান ইলিয়াস তাঁর জীবদ্দশায় প্রয়াত হয়েছিলেন এবং তাঁর মৃত্যু পরবর্তীকালে আবদুল মান্নান সৈয়দ তেমনি তাঁরা ছাড়া আমরা যাঁরা তাঁর নিকট সান্নিধ্য পেয়েছি তাঁরাও যখন থাকবো না তখন জন্মশতবর্ষউত্তর বাস্তবতায় উত্তরপ্রজন্মরা তাঁর সাহিত্য ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে শওকত ওসমানকে খুঁজে পাবে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে নবীন পাঠকদের তাঁকেও পড়তে ইচ্ছে হবে। এই উভয় পাঠ ও যুগলবন্দী থেকে তারা আবিষ্কার করবে নতুন এক শওকত ওসমানকে।
তাঁর মৃত্যুর পরদিন ১৯৯৮’র ১৫ মে ‘দৈনিক জনকণ্ঠ’ তার সম্পাদকীয়তে বলে ‘শওকত ওসমান শুধু সাহিত্যিক বা ঔপন্যাসিক ছিলেন না।’ ‘গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের তিনি একজন বিশিষ্ট অভিভাবক হয়ে উঠেছিলেন।’ দৈনিকটি আরও বলে, ‘সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি তাঁর আদর্শিক সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন শয্যাশায়ী হওয়ার আগ পর্যন্ত।’ আজ যখন শারীরিকভাবে তিনি অনুপস্থিত তখন তাঁর চেতনা শতবর্ষউত্তর বাস্তবতায় আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।
শীর্ষ সংবাদ: