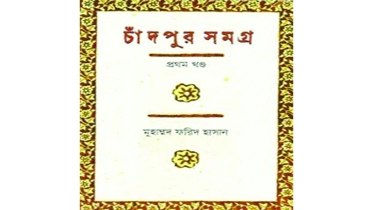বাড়ি ফিরতে-ফিরতে মাগরিবের আজান পড়ে গেল। আমাদের মতো আরো অনেক পরিবার পালিয়েছিল। তাদের অনেকে ইতোমধ্যে ফিরে এসেছে, কেউ কেউ ফিরছে এখনও আমাদের মতো। আজ আমরা এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলাম। পাকিস্তানী আর্মি আমাদের গ্রামে ঢুকেছিল। শুনলাম আমাদের পাশের পাড়া থেকে ফিরে গেছে। কিছু গরু-ছাগল আর মুরগি ধরে নিয়ে গেছে। মারধর করেছে কয়েকজনকে। হিন্দু আর আওয়ামী লীগের লোকদের খোঁজ করেছে। অবশ্য পেয়েছে খুব কম লোককেই, কারণ তাদের আসার খবর শুনে আগে-ভাগেই পালিয়েছে সব মানুষ।
আমাদের পাড়ার সব পশ্চিমে আমাদের বাড়ি। তার পেছনে একটা ছোট মাঠ। তারপরে পশ্চিমপাড়া। পালানোর আগে আমাদের বাড়ির পেছনের আমবাগানে দাঁড়িয়ে একটুখানি দেখার চেষ্টা করেছিলাম। হেলমেট পরা অস্ত্রধারী কয়েকজন পাকসেনাকে আমরা দেখেছিলাম, তারা বাবুদের বাড়ির পাশের একটা চারা আমগাছের ডাল থেকে আম ছিঁড়ছিল।
২৬ শে মার্চ থেকেই আমরা পালিয়ে বাঁচার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতাম। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসের ছোট ছোট পুটলি বাঁধাই থাকতো, কে কোনটা নেবে তার ফর্দও ছিল, নাও আর দাও দৌড়। কোথায়? কোন দিকে? তার কোনও ঠিক-ঠিকানা ছিল না। আমরা দৌড় দিয়েছিলাম পুবদিকে, যেহেতু পাকসেনারা পশ্চিম দিকে নেমেছে।
আমরা পালাতে পালাতে প্রায় দুই মাইল দূরে চলে গিয়েছিলাম, আনুমানিক পঞ্চাশ-ষাট জন লোক। এর আগেও পালিয়েছি কয়েকদিন, রাতের বেলা, আমাদের বাড়ির পেছনের মাঠের মধ্যে গিয়ে কোমরসমান কুশোরের (আখের) জমিতে লুকিয়ে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
মা কিছু রান্না-বান্না করল, খাওয়া-দাওয়ার পালা শেষ হতে-না-হতেই শুরু হলো ঝড়। আমরা বাড়ির দরোজা-জানালা বন্ধ করে আল্লা-আল্লা করতে লাগলাম। আব্বা বললেন, কালবৈশাখী শুরু হয়ে গেলো। চৈত্রের শেষ আজ, কাল পয়লা বৈশাখ, বাংলা নববর্ষ।
আমাদের গ্রামটা ছিল বেশ রক্ষণশীল। বিদআতী কাজ-কর্মের বিরুদ্ধে লোকজন ছিল একজোট। ফলে এ গ্রামে নববর্ষ পালিত হতো না, এর সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। তবে হালখাতা হতো। এবার তারও কোনও আয়োজন দেখছি না। জিলাপি লাড্ডু রসগোল্লা এবার আর খাওয়া হচ্ছে না। খাওয়া-দাওয়ার প্রতি কারো মনোযোগও নেই আর। সবাই জান-মাল নিয়ে উদ্বিগ্ন, দেশ নিয়ে চিন্তিত।
১৯৭১ সাল এটা। রাজশাহী ১১ই এপ্রিল পর্যন্ত বলতে গেলে স্বাধীনই ছিল। পুলিশ, ইপিআর এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনতা ঘেরাও করে রেখেছিল রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট। যে কোনো মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করবে পাকবাহিনী, নয়তো পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে কিংবা কামান দেগে ওদের শেষ করে দেওয়া হবে। এরকম কথা-বার্তাই শুনছিলাম আমরা কয়দিন থেকে। ওদের রক্ষা করতে দুটি পাকিস্তানী বিমান প্রায় প্রত্যেকদিনই রাজশাহীতে কয়েকবার করে বোমাবর্ষণ করে চলেছিল। ওদের বোমাবর্ষণে আমাদের গ্রামের ওদুদ ভাই এরই মধ্যে মারা গেছে। হাইস্কুলে পড়ত সে, তাগড়া জোয়ান হয়ে উঠছিল কেবল। এ নিয়ে আমাদের গ্রামে শহীদের সংখ্যা দাঁড়ালো দু’জন। এর আগে পঁচিশে মার্চ কালরাত্রিতে মারা গেছেন আমার মায়ের ফুফাতো ভাই, আমাদের রাজ্জাক মামা। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবনে প্রহরার দায়িত্বে ছিলেন। নির্দেশ মতো প্রশাসন ভবনের গেট না খোলার অপরাধে তাকে গুলি করে হত্যা করেছিল পাকসেনারা।
ঢাকা থেকে, যমুনা পেরিয়ে, পাকসেনাদের একটি বাহিনী নগরবাড়ি হয়ে রাজশাহী দখল করতে এগিয়ে এলো। তাদের আধুনিক ভারি অস্ত্রের মুখে কোনও প্রতিরোধই টিকলো না। ১২ই এপ্রিল রাজশাহীর পতন হলো। ঝলমলিয়ার হাটে বেপরোয়া গুলি চালিয়ে বহু নিরপরাধ হাটুরেকে হতাহত করল পাকসেনারা। জ্বালিয়ে দিলো অনেক দোকান-পাট। বিড়ালদহ এবং বেলপুকুরিয়া রেলগেটে স্বল্পস্থায়ী, কিন্তু ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হলো। উভয়পক্ষেরই অনেক হতাহত হয়েছিল সে দুটি যুদ্ধে। আমাদের গ্রামে এসে আশ্রয় নিলেন অনেক যোদ্ধা। বেশিরভাগই পাশের পদ্মা পেরিয়ে চলে গেলেন ভারতের উদ্দেশে। গোটা গ্রামের মানুষ আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো। সে রাতটা যে কীভাবে কেটেছিলো আমাদের! পাকসেনারা আসতে পারে এই ভয়ে আমরা মাঠের মধ্যে, জঙ্গলে, রাত কাটিয়েছি।
তারপর ১৩ই এপ্রিলের ঘটনা, পাক আর্মিদের আমাদের গ্রামে আগমন। আব্বা বলছিলেন, তেমন কিছু করেনি বটে, কিন্তু লক্ষ্মণ ভাল নয়। আমরা বোধ হয় আর বাড়িতে থাকতে পারব না। কিন্তু পালিয়ে যাবো কোথায়?
রাজশাহী মহানগরীর উপকণ্ঠে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে, আমাদের শ্যামপুর গ্রাম। তার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে পদ্মা নদী। এই গ্রামের লোকেরা রাজশাহীর রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। মওলানা ভাসানী, শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দীর মতো নেতাদের পদার্পণ ঘটেছে এই গ্রামে। আমার মামা আব্দুস সোবহান তখন আওয়ামী লীগের একজন বড় নেতা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ। আর কামারুজ্জামান তো তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠজন। শ্বশুরকুলের দিক থেকে তিনি মামার আত্মীয়ও বটে। অন্যদিক থেকে, তৎকালীন মুসলিম লীগের (আইউবপন্থী) কেন্দ্রীয় নেতা অ্যাডভোকেট আয়েনউদ্দীনও এই গ্রামেরই মানুষ। তাঁর দৌলতে মোনায়েম খান, শরীফউদ্দীন পীরজাদার মতো লোকেরাও এই গ্রামে এসেছেন। আমার আব্বার যুক্তি হলো, এই গ্রাম পাক আর্মির চোখ এড়াতে পারবে না। আব্বা খুব রাজনীতিসচেতন মানুষ ছিলেন, তাঁর রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে গ্রামের লোকেরা খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তিনি বললেন, ভায়ের (মানে আমার একমাত্র মামার) বাড়িতে থাকা ঠিক হবে না। আমাদেরও যে কী হবে আল্লাই জানেন। আব্বার মন্তব্য শুনে মা ওই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যেই কাঁদতে লাগল।
প্রায় ঘণ্টা দেড়েক মুষলধারে বৃষ্টি হলো। বৃষ্টির প্রকোপ কমলে আব্বা পরিস্থিতি দেখতে বের হলেন। অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। বৃষ্টি পড়ছে তখনো ফিরফির করে। উঠোনে পানি থইথই করছে। আমাদের বাড়িটা ছিল মাটির প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। একটা নালা আছে বাড়ির পানি বেরুনোর। সে নালা দিয়ে পানি বেরিয়ে কুল পাচ্ছে না। আব্বা নালাটা বেশ পরিষ্কার করে দিলেন। খানিকটা পরে দরোজায় ধাক্কা পড়লো। আমার ছোট নানী, মানে আমার মায়ের ছোট চাচী, তার সঙ্গে তার মেজো ছেলে, মাইনুল মামা। তারা আমাদের নিয়ে যেতে এসেছেন। এখানে একা-একা থাকা নিরাপদ নয়। আমাদের বাড়িটা ছিল মাঠের ধারে, পাড়ার সব শেষের বাড়ি। পাড়ায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে অনেক সময়ই আমরা জানতে পারতাম না। পুঁটলি নিয়ে ফিরফিরে বৃষ্টি মাথায় আমরা গিয়ে উঠলাম ছোট নানার বাড়ি। দেখলাম সেখানে মামাও উপস্থিত। আব্বা, মা, মামা, ছোট নানা আর নানী ফিসফিস করে গল্প করতে লাগলেন। ঝড়-বৃষ্টির পর প্রকৃতি ভারি শীতল এবং আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। সারাদিনের ক্লান্তি আর আতঙ্কে বিধ্বস্ত আমরা ছোটরা দ্রুত ঘুমিয়ে পড়লাম গাদাগাদি করে।
আমাদের যখন জাগানো হলো তখনও ফজরের আজান হয়নি। জানলাম, আমাদের ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ভারতে যাওয়া ছাড়া মামাকে বাঁচানোর উপায় নেই। কিন্তু আমরা কেন? ভারতে গিয়ে কী হবে কে জানে! মামা ও নানার যুক্তি, আব্বা গেলে অন্তত একটা আশ্রয় মিলবে, কারণ ওখানে আব্বার দুই ভাই আছেন। মা আপত্তি করেছিল। আব্বার সরকারি চাকরিটাই আমাদের জীবিকার একমাত্র উপায়। ভারতে চলে গেলে চাকরিটা আর থাকবে না। আব্বা পিডব্লিউডির সাবএসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আব্বার কী হয়েছিল কে জানে! তিনি বলছিলেন, কখনো কখনো জীবনে এমন সময় আসে যখন কাউকে না কাউকে কিছু একটা স্যাক্রিফাইস করতেই হয়। দেশ ও জাতির এই দুর্দিনে সে স্যাক্রিফাইস না হয় আমরা করলাম। বলাবাহুল্য, আব্বার চাকরি চলে গিয়েছিল। স্বাধীনতার পর অবশ্য আব্বা সে চাকরি ফিরে পেয়েছিলেন, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছিল। তাঁর স্যাক্রিফাইসের মর্যাদা তিনি পাননি সারাজীবন।
মামা তাঁর পরিবারের কাউকে সঙ্গে নিলেন না। ছোট নানা তাঁর মেজো ছেলে মাইনুল মামাকে দিলেন আমাদের সঙ্গে, অন্তত পরিবারের একজন নিরাপদে থাকুক এই তাঁর প্রত্যাশা। গোটা পরিবার বলতে আমরাই, আমার আব্বা-মা, আর আমরা পাঁচ ভাইবোন (আমার সবচেয়ে ছোট দুই ভাইবোনের তখনো জন্ম হয়নি)। ভাইবোনদের মধ্যে আমিই সবার বড়, তখন আমার বয়স কেবল দশ পেরিয়েছে। আর ছোট বোন পলির বয়স এক বছরের কিছু বেশি।
কাউকে কিছু না জানতে দিয়ে চুপিচুপি বেরিয়ে পড়লাম আমরা। নদীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে, আমার যতদূর মনে পড়ছে, নান্নু মামা (ছোট নানার বড় ছেলে, তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা) সঙ্গে ছিলেন।
সেদিন বাংলা নববর্ষের দিন, অর্থাৎ ১৩৭৮ সালের পয়লা বৈশাখ, ইংরেজি ১৯৭১ সালের ১৪ই এপ্রিল। ভোরের বাতাসে ভেজা শীতল আবেশ। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। আমরা খুব রাজনীতি-তাড়িত মানুষ ছিলাম। সেই দশ বছর বয়সে বড়োদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমরা ছোটরাও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সারা রাত জেগে মিছিল করে বেড়িয়েছি। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের পর বড়োদের সঙ্গে ডামি রাইফেল কাঁধে ট্রেনিং নিয়েছি। আর প্রায় প্রত্যেকদিনই মিছিল করেছি। ২৩ শে মার্চ গ্রাম থেকে মিছিল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে রাজশাহীর প্রাণকেন্দ্র সাহেববাজারে গিয়েছি। মিছিলে গুলি হয়েছে দুপুরের কিছু আগে, আমরা দলছুট হয়ে মূল সড়ক ছেড়ে নানান পাড়া-মহল্লা ঘুরে বাড়ি ফিরেছিলাম শেষ বিকেলে। আমি বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের পুরো ভাষণ মুখস্থ করে ফেলেছিলাম। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠ অবিকল নকল করে সেই ভাষণ শোনাতে হতো আমাকে। বাড়িতে ইত্তেফাক নিতেন আব্বা। ফলে রাজনীতির অতীত ছাড়াও একেবারে হাল খবরও জানা থাকতো আমার। সবচেয়ে বড় কথা প্রায় প্রত্যেকদিন রাতে আমার মামা আসতেন আমাদের বাড়ি, আব্বার সঙ্গে সারাদিনের রাজনৈতিক কর্মকা- নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। আমি মনোযোগ দিয়ে শুনতাম তাঁদের সেই আলোচনা। এভাবে ওইটুকু বয়সেই আমি আমাদের গ্রামের লোকদের কাছে ‘রাজনীতিবিশেষজ্ঞ’ হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু নিজেদের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে হবে এটা কখনো ভাবিনি। যেখানে যাবো সেখানে জীবন যে ভয়ানক রকম অনিশ্চিত সেটা বড়দের আলাপ-আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি। বিস্ময়, আতঙ্ক আর অসহায়তার এক বোবা বোধ নিয়ে আমরা পাঁক-কাদা খুঁচে পথ ভেঙ্গে চলেছি।
আমাদের পাড়ার সোজা দক্ষিণে মোল্লাপাড়া, তার দক্ষিণে পদ্মা, আমাদের বাড়ি পার হয়ে সোজা গেলে বড়জোর দশ মিনিটের রাস্তা। কিন্তু আমাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল উল্টো দিকে, পুব-দক্ষিণমুখো। মোল্লাপাড়ায় একটা বালুরঘাট আছে, কিন্তু সেখানে খেয়া নৌকা পাওয়া মুশকিল। মামার ইচ্ছে নগরপাড়া পেরিয়ে সাহাপুরঘাটে ওঠা। সেখানে খেয়ানৌকা পাওয়া যায় সবসময়। মামার ভক্ত এক মাঝি আছে ঘাটের পাশেই, তাঁর ইচ্ছা তাকে নিয়েই তিনি নদী পেরোবেন। রাতের বৃষ্টিতে রোদপোড়া দোআঁশ মাটি এলিয়ে গোবর একেবারে। হাঁটা যায় না। আইলগুলোও ধসে-দেবে যাচ্ছে। সাহাপুর প্রায় মাইল দুয়েকের পথ। খেয়াঘাটে পৌঁছার আগেই ভোর হয়ে গেলো।
খেয়াঘাটে একটা নৌকাও নেই, এমনকি আশপাশে কোনও মানুষ-জনেরও দেখা মিলল না। হতাশ হয়ে বসে পড়লাম আমরা। আশপাশের বাড়িগুলো খুঁজতে গিয়ে আরও অবাক হওয়ার পালা। সব ফাঁকা। বোঝা গেলো আমাদের মতো ওরাও সব পালিয়েছে। গত দুদিন চারঘাট আর সারদায় গণহত্যা চালিয়েছে পাকবাহিনী। এই তো নদীর ধার দিয়ে গেলে তিন-চারটা গ্রামের পরেই। হয়তো সেই হত্যাকা-ের কথা শুনে আগে-ভাগেই পালিয়েছে এই গ্রামের মানুষরা।
অগত্যা চরপাড়ায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন মামা। আবার পেছনে ঘুরে মোল্লাপাড়ার বালুরঘাট পেরিয়ে পশ্চিমে যেতে হবে। নদীর ধার দিয়ে হাঁটতে লাগলাম আমরা। বৃষ্টি¯œাত সূর্য ততক্ষণে রোদ ছড়াতে শুরু করেছে। চরপাড়ার কাছে এবার এপাশে কিছুটা চর পড়েছে। সেই চর মাড়িয়ে নদী। ভাগ্য ভালো একটা নৌকা পাওয়া গেলো।
পদ্মা পেরিয়ে ভারতের সীমান্তে পৌঁছে আমাদের তো চোখ ছানাবড়া। এত্ত লোক! সাহাপুরের সেই মাঝির সঙ্গেও দেখা হয়ে গেলো। এরা এখনো সীমান্ত এলাকায় রয়ে গেছে। বাড়িতে যদি ফেরা যায়! ওখানে অনেক খবর পাওয়া গেলো। ভারত সরকার শরণার্থীদের আশ্রয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আওয়ামী লীগের ছোট-বড় বহু নেতা ইতোমধ্যে ভারতে চলে গেছেন। মামা আর আব্বা অনেকখানি আশ্বস্ত হলেন। শুনে কবুতরের মতো দুর্বল আমাদের বুকও হালকা হলো খানিকটা।
আমরা আপাতত যাবো মুর্শিদাবাদের ডোমকুল থানার একটি গ্রামে। সেটা আমার পিতার জন্মস্থান। এখনো সেখানে আমার দুই পিতৃব্য ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন। আব্বার নিজের পৈতৃক জমি-জমাও আছে সেখানে, আমার চাচারা ভোগ-দখল করেন। আব্বা আশা, এই বিপদের দিনে সেখানে গিয়ে আমরা তাঁদের কাছে আপাতত আশ্রয় পাবো।
কাতলামারিতে বাসে চেপে দুপুর নাগাদ আমরা ইসলামপুরে নামলাম। এখানে বাস বদল করতে হবে। বাসের দেরি ছিল, আর আমরা সবাই ছিলাম ভয়ানক ক্ষুধার্ত। সেই ভোর থেকে বেলা প্রায় দশটা নাগাদ হাঁটতে হয়েছে আমাদের। একটা চা-মিষ্টির দোকানে গিয়ে বসলাম আমরা। কিন্তু দোকানী বেঁকে বসল। ‘জয়বাংলা’র লোক শুনে বলল, পাকিস্তানের টাকা সে নেবে না। আমাদের কাছে তো পাকিস্তানের টাকা ছাড়া অন্য টাকা নেই। একে ক্ষুধা, তার ওপর চিড়া-দুধ-রসগোল্লার লোভনীয় খাবার, আমরা হাত-মুখ ধুয়ে জিভ চটকাচ্ছি। আব্বা খুব বোঝানোর চেষ্টা করলেন। বললেন, বাস কন্ডাক্টর পাকিস্তানী টাকাই নিয়েছে। কিন্তু দোকানীর মন গলল না। আমরা মন-মরা হয়ে উঠে পড়লাম। এমন দুরবস্থা আর অপমানকর পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কখনো পড়িনি। আমাদের বাড়িতে সব সময় বাইরের দু-চার জন লোকের পাত পড়ে, তাতেই অভ্যস্ত আমরা। নিজেদের ভিখিরি মনে হলো এখন। মায়ের চোখ বেয়ে অশ্রু গড়াতে লাগলো। আব্বা আর মামার মুখ লজ্জায়-অপমানে কালো হয়ে উঠেছে।
আমরা মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসছি এমন সময় একজন ধুতি-পরা মধ্যবয়সী মানুষ আমাদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। তিনি এই হোটেলেই চা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, বসুন আপনারা, বসো বাবাধনেরা, তোমরা বসো। তারপর দোকানীকে উদ্দেশ করে বললেন, খাবার দাও ওদের। আমি পয়সা দেবো।
আমরা তবু বেরিয়ে আসতে চাইলাম। এরকম করুণার পাত্র আমাদের কখনো হতে হয়নি। ভদ্রলোক বললেন, আমি জানি, আপনারা ভদ্রঘরের মানুষ, আপনাদের খারাপ লাগছে। কিন্তু এখন আপনারা যদি আমাকে এ সুযোগটুকু না দেন তাহলে আমি খুব কষ্ট পাবো।
ভদ্রলোকের জোড়হাত, আন্তরিক আহ্বান, আর আমাদের ছোটদের দিকে তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত মামা রাজি হলেন। বললেন, ঠিক আছে, ওরা খাক।
আমরা বসলাম আবার। সেই ভদ্রলোক আমাদের বরযাত্রী খাওয়ানোর মতো নিজে তদারকি করে খাওয়ালেন। তাঁর আতিথেয়তায় আব্বা-মামাও না করতে পারলেন না। Ñদিদি কি আমাকে দাদা ভাবতে পারছেন না? এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে পেরে মা-ও খেলেন একটা মিষ্টি।
বাসে উঠে ভাড়া দিতে গিয়ে আবার সেই টাকা নিয়ে বিপত্তি। পাকিস্তানী টাকা নেবে না কন্ডাক্টর। সে ‘জয়বাংলা’র গোষ্ঠী উদ্ধার করতেও ছাড়ল না। আমার পাশে একজন দাড়িওয়ালা লম্বা পাঞ্জাবি-পরা, মৌলবি-ধরনের ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি বারবার আমার আব্বার দিকে তাকাচ্ছিলেন। Ñভাড়া দিতে হবে দাদা, পয়সা বের করুন, বলে কন্ডাক্টর যখন অন্যদের ভাড়া আদায় করতে এগিয়ে গেলো, তখন মৌলবি ভদ্রলোক আব্বাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনেরা পাকিস্তান থেইকে আসছেন? যাবেন কুথায়?
আব্বা হতাশমুখে মাথাটা একটু নেড়ে বললেন, কাটাকোবরা নামবো।
Ñসেখান থেইকে কুথায় যাবেন?
Ñশ্রীকৃষ্ণপুর।
ভদ্রলোক এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন, তাঁর চোখ দুটি যেন বা একটুখানি চঞ্চল হয়ে উঠলো। Ñছিকিষ্টপুর কার বাড়ি?
হতাশায় ক্ষোভে কিছুটা বিরক্ত আব্বা। বললেন, আপনি কি চিনবেন?
Ñছিকিষ্টপুরের সব্বাইকে চিনি আমি। কার বাড়ি যাবেন বুলেন তো?
Ñআব্দুল লতিফ মোল্লা, আব্দুল করিম মোল্লাÑ চিনেন ইনাদের? তাদের বাড়ি যাবো।
ভদ্রলোকের মুখটা এবার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি আব্বার গায়ে গিয়ে পড়েন এইরকম অবস্থা প্রায়। বললেন, আপনে কি এলাহী মোল্লা?
আমাদের সবার বাকরুদ্ধ অবস্থা। লোকটা আমার আব্বার নাম জানলো কী করে?
Ñআমি আবুল কালাম, চাচা, আমি বিলপাড়ার সোলেমান মৌলবির ছেলে আবুল কালাম। আব্বার দুই হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আবেগে চেপে ধরলেন তিনি। তাঁর চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো।
কী উচ্ছ্বসিত দুজনে! শুনলাম, আব্বা শৈশবে সোলেমান মৌলবির কাছে কিছুদিন কুরআন শিক্ষা করেছিলেন। তখন বয়সে কিছু ছোট হলেও আবুল কালামও পড়তেন তাঁর সাথে। আব্বা মক্তব পাশ করে কৈশোরেই বাড়ি ছেড়েছিলেন হুগলির উদ্দেশে, আরো লেখাপড়া শিখবেন বলে। হুগলি থেকে ১৯৫২ সালে রাজশাহী। জন্মভূমি গ্রামের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল খুব কম। পাকিস্তানে চলে আসার পর যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৫৪ সালের পর এই প্রথম তাঁর ভারত ভ্রমণ। আবুল কালামের গালভর্তি বুকসমান সাদা-কালো দাড়ি ছাপিয়ে তিনি অবশ্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত চিনতে পারলেন।
কন্ডাক্টরকে ডেকে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন আবুল কালাম। মায়ের কাছে এসে বারবার বলতে লাগলেন, এতদিন পর শ্বশুরবাড়ি বেড়াতে এলেন গো মা? আপনের শ্বশুরবাড়িতে আমরা কত গিয়েছি, খেইছি, তার ইয়ত্তা নাই মাগো। আপনে মোল্লাবাড়ির ছোটবউ গো মা, আপনের ইট্টুুখানি খেদমত করার সুযোগ দেন।
কাটাকোবরা থেকে শ্রীকৃষ্ণপুর কমপক্ষে দুমাইল রাস্তা। হাঁটা ছাড়া গতি নেই শুনে আমাদের কান্নার জোগাড়। আবুল কালাম ভাই আমাদের একটা ছাপড়া হোটেলে বসিয়ে ‘যে যা খাবে দাও, আমি আসছি’ বলে ‘কিছু করা যায় কিনা’ দেখতে বেরুলেন। আমাদের লজ্জা অনেকখানি কেটেছে ততক্ষণে, তাছাড়া আব্বা বললেন, যা খরচ হচ্ছে ওকে শোধ করে দেব, অসুবিধা নাই, তোরা খা। সুতরাং আমরা ঝাল-মিষ্টি মিলিয়ে যার-যা ভাল লাগলো নিলাম। চা খেয়ে শরীরটা বেশ ফুরফুরে মনে হতে লাগলো।
আবুল কালাম মৌলবি বটে, কিন্তু কাজের মানুষ। তিনি একটা গরুরগাড়ি ভাড়া করে আনলেন। মা আর আমরা বাচ্চারা গাড়িতে উঠলাম। বাকিরা হেঁটে চললেন।
আমরা যখন মোল্লাবাড়ি পৌঁছলাম তখন পড়ন্ত বিকেল। আমাদের গ্রামে কাদা-পানি দেখে গিয়েছিলাম, কিন্তু এদিকে বৃষ্টি হয়নি। রোদে পোড়া-পোড়া ভাব প্রকৃতির। আবুল কালামের চেঁচামেচিতে গ্রামে ঢোকার পর থেকেই লোকজন গাড়ির পেছনে সার ধরলো। আব্বা আর মামা মোসাফাহ করতে করতে বেচাইন।
আব্দুল লতিফ মোল্লা, আমার মেজো আব্বা, বেশ কয়েকবার আমাদের বাড়ি গিয়েছেন। ল আব্বা আব্দুল করিম মোল্লা একবার গিয়েছেন। তাঁরা ছাড়া আর সব মানুষই আমার অচেনা। কিন্তু বসতে না বসতেই আমাকে আপন করে নিলো আমার তিন চাচাতো ভাই মহিউদ্দিন, মানসুর আর মোজাফ্ফর। দুই জমজ চাচাতো বোন শামসু বুবু আর মেহেরুন বুবু রুটি এনে ধরলেন সামনে। আমাদের তো চোখ ছানাবড়া। এত্ত বড় রুটিও হয় দুনিয়াতে! আমরা এমনিতে রুটি খেতে অভ্যস্ত নই। তার ওপর এইরকম মাথালের মতো বড় হাতে-বেলা মোটা মোটা রুটি। সঙ্গে কাঁঠালের ঘাটি, আর খেজুরের ঝোলা গুড়। ভয়ে ভয়ে মুখে দিলাম। ভাল, বেশ ভাল। চমৎকার। রুটি খেতে এতো ভাল লাগে তা-ও জানা ছিল না আমাদের।
১৩৭৮ সালের পয়লা বৈশাখ দিনটি ছিল এমনই, কষ্ট ও আনন্দের মিশেলে স্মৃতিময়। তারপর প্রায় নয় মাস রিলিফের পচা-বাসি খাবার খেয়েছি, কেঁদেছি, আবার স্বাধীন বাংলা বেতারের খবর-কথিকা শুনে উদ্দীপ্ত হয়েছি। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসের ৬ কি ৭ তারিখ আমরা দেশে ফিরেছিলাম, স্বাধীনতার পর। আমার যতদূর মনে পড়ে আমি বাংলা নববর্ষ উদযাপন শুরু করেছি ১৯৮০ সাল থেকে। যখনই নববর্ষ আসে তখনই আমার স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে মুক্তিযুদ্ধকালীন সেই নববর্ষের দিনটি। আমি ভীষণ কষ্ট পাই, যখন দেখি ইসলামপুরের সেই ধুতি-পরা ভদ্রলোক কিংবা বিলপাড়ার সোলেমান মৌলবির ছেলে আবুল কালামের সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে না। তাঁদের ঋণ আমরা কীভাবে শোধ করবো?
পুনশ্চ: কাকতালীয় ব্যাপার এই যে, আজ ১৪২৩ সালের পয়লা বৈশাখ, যখন এই লেখাটি পাঠকের চোখের সামনে, তখন আমি ভারত ভ্রমণে চলেছি। ৪৫ বছর আগে, ১৩৭৮ সালের এই দিনে গিয়েছিলাম শরণার্থী হয়ে, আর আজ চলেছি স্বাধীন বাংলাদেশের গর্বিত নাগরিক হিসেবে। আমার নববর্ষ মানে তাই চুপিচুপি হৃদয়ের মাঝে দেশ ও মানবিক চেতনাকে বারবার অনুভব, উপলব্ধি ও স্পর্শ করা, কষ্ট ও আনন্দের মিশেলে জীবনকে উদযাপন করা। সেই ধুতি-পরা ভদ্রলোক আর আবুল কালামের স্মৃতি ছাড়া আমার নববর্ষ নিরর্থক।